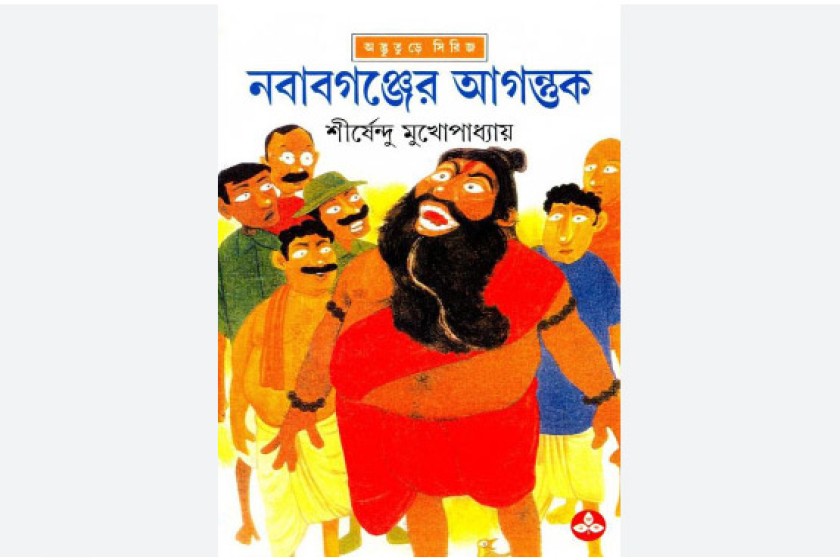
নবাবগঞ্জের আগন্তুক - শীর্ষেন্দুর অদ্ভুতুড়ে সিরিজের পঁচিশতম আখ্যান
- 17 May, 2025
- লেখক: মনীষা নস্কর
একটা জায়গা কাছেই আছে, কিন্তু চোখের সামনে নেই। চাইলেও কেউ হুট করে সেখানে চলে যেতে পারে না। কিন্তু সে জায়গা আছে। লীলা মজুমদার, ল্যুইস ক্যারল-রা এমন সব আশ্চর্য জায়গার কথা বলেছিলেন বটে। তবে সেসব ছিল নেহাতই ফ্যান্টাসি। শীর্ষেন্দুও বারকতক তাঁর অদ্ভুতুড়ে সিরিজে এমন জায়গার কথা বলেছেন। কিন্তু তফাত শুধু একটা জায়গায়, সেগুলো ফ্যান্টাসি না, তা সায়েন্স ফ্যান্টাসি।
২৫ নম্বর অদ্ভুতুড়েতে গ্রামের নাম নবাবগঞ্জ। নবাবগঞ্জের কাছেই আছে নয়নগড়। সে নয়নগড় কিন্তু নবাবগঞ্জের লোকেরা চোখে দেখতে পায় না, কারণ সে জায়গা আছে ভিন্ন কম্পাঙ্কে। একটা সূচের মতো যন্ত্র হাতে নিয়ে তবেই যাওয়া যেতে পারে নবাবগঞ্জ থেকে নয়নগড়ে।
নবাবগঞ্জ সাদাসিধে চোর-ছ্যাঁচোড়ে ভর্তি হাসিখুশি আর পাঁচটা অদ্ভুতুড়ে গ্রামের মতোই। ইদানীং গ্রামে নতুন নতুন লোক আসছে। নবাবগঞ্জের প্রথম আগন্তুক জ্ঞানপাগলা। জ্ঞান হল নয়নগড়ের যুবরাজ। নয়নগড়ের দখল নিতে চায় মাজুম আর তার সমর্থকরা। মাজুমরা দিনের আলোয় অন্ধ, রাত বাড়লেই তাদের শক্তি বাড়ে। নয়নগড়ের বুড়ো রাজা চান না মাজুমদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। তাই মাজুম সূচের সাহায্যে যুবরাজ জ্ঞানকে নির্বাসনে পাঠিয়েছে ভিন্ন কম্পাঙ্কের নবাবগঞ্জ গ্রামে। কিন্তু এখানে সূচটি গেছে খোয়া। মাজুম, জ্ঞান, তাদের দুজনের দুটো দল সবাই আটকা পড়েছে নবাবগঞ্জে।
গল্প শুরু হয় গবাক্ষবাবুর সাথে এক চোরের মোলাকাত দিয়ে। এই চোর যে সে চোর নয়, বেশ অ্যাস্থেটিক সেন্স সম্পন্ন চোর। জন্মসূত্রে পাওয়া নাম ‘পঞ্চা’ তার বড়ই না-পসন্দ ছিল, কোর্টে গিয়ে এফিডেফিট করে সে ‘প্রিয়ংবদ’ হয়ে এসেছে। তবু তার খেদের অন্ত নেই—
"গাঁয়ের লোকের উচ্চাটনের কথা আর বলবেন না মশাই। উশচ্চাটন একেবারে যাচ্ছেতাই। আগে পঞ্চা-পঞ্চা করত, এখন পেড়াপেড়ি করায় বদু বদু বলে ডাকে। প্রিয়ংবদ উশচ্চাটনই করতে পারে না।"
স্রেফ গেঁয়ো চোরদের অদ্ভুতুড়ে কান্ডকারখানা নিয়েই শীর্ষেন্দু লিখে ফেলেছেন একরাশ কিশোরপাঠ্য গল্প। অদ্ভুতুড়ে সিরিজেও মাঝেমাঝে তেমন চোরেরা উঁকি মেরে যায়। অদ্ভুতুড়ে গল্পগুলোয় গ্রামের লোকজন চোর, ভূত, বোকা পুলিশ নিয়ে বেশ সন্তুষ্ট থাকে। ভাবখানা এমন, গাঁয়ে দু’চারখানা চোর ডজনখানেক ভূতপ্রেত না থাকলে কি আর সেটা গ্রাম হল নাকি? গবাক্ষবাবুর ঘরে পঞ্চাচোর ঢুকেছে, গবাক্ষবাবু দিব্যি গপ্পো জুড়ে দিয়েছেন চোরের সঙ্গে।
"জিনিস! জিনিসটাই বা কী এমন রেখেছি যে চোর ঢুকবে! তোদের কি ধারণা ঘরে দামি-দামি জিনিস রেখে চোরদের নেমন্তন্নের চিঠি পাঠিয়ে বসে আছি। আমি তেমন বান্দা নই।"
পঞ্চা খুক করে একটু হেসে বলল, "তা আর বলতে! ঘরের যা ছিরি করে রেখেছেন তাতে ঢুকতে লজ্জাই হয়। তক্তাপোশের তো একখানা পায়াই নেই, ইটের ঠেকনো দিয়ে রেখেছেন। রান্নাঘরে কয়েকখানা মেটে হাঁড়িকুড়ি আর কলাই করা থালাবাটি। না মশাই, চোরেরও মান-সম্মান আছে।
পঞ্চার এই কথায় গবাক্ষবাবুর একটু প্রেস্টিজে লাগল। তিনি অতিশয় গম্ভীর গলায় বললেন, "তা হলে কি তুই বলতে চাস আমি ছ্যাঁচড়া লোক?"ণ
"বললে ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যাবে। তবে সত্যি কথা বলতে হলে বলতেই হবে যে ছ্যাঁচড়া শব্দটা যেন আপনার জন্যই জন্মেছে। অনেক বাড়িতে ঢুকেছি মশাই, কারও বাড়িতে এমন দুর্দশা দেখিনি। চোরদের জন্য কি আপনার একটু মায়াও হয় না!”
গবাক্ষবাবু বেশ অপমান বোধ করছেন, কিন্তু প্রতিবাদ করারও উপায় নেই। পঞ্চা সত্যি কথাই বলছে। তাই গবাক্ষবাবু গলাটা একটু নামিয়ে বললেন, "ভাল করে খুঁজলে কি আর টাকাটা সিকিটা পেতি না?"
"আজ্ঞে সে-কথা ঠিক। খুঁজলে আপনার ঘরে টাকাটা সিকিটা কপালে যে জোটে না তা নয়। বাঁদিকে পায়ের কাছে তোশকের তলায় একখানা সিকি আছে, বালিশের তলায় একটা আধুলি, আলনায় যে ছেঁড়া জামাখানা ঝুলছে তার বাঁ পকেটে একখানা কাঁচা টাকাও আছে বটে, তবে সেটা অচল। আজ বাজারে আলুওলা টাকাটা নিতে চায়নি বলে আপনার খুব মেজাজ চড়ে ছিল।"
"টাকাটা মোটেই অচল নয়। চালালে দিব্যি চলে যাবে।"
"তা যাবে। সাঁঝবাজারে যে-লোকটা ঘানিঘরের পাশে বেগুন বেচতে বসে তার দু' চোখে ছানি। তাকে গছাতে পারেন। নইলে ঈশেনপুরের নন্দী মহাজনের হাবাগোবা বাজার সরকার মহেশবাবুকে। নইলে জকপুর বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের অঙ্কের মাস্টার পাগলা কালীবাবুকে। ভারী আনমনা লোক। অঙ্কের পণ্ডিত হলে কী হবে, বাজার করতে গিয়ে সাত টাকা কিলোর সাড়ে তিনশো গ্রাম জিনিসের দাম কষতে গলদঘর্ম হতে হয়।”
অদ্ভুতুড়ে সিরিজের এই এক আশ্চর্য ব্যাপার— কথোপকথনগুলো বেশ লম্বা একটানা হয়ে চললেও মোটেই গল্পের গতিটি তাতে ব্যাহত হয় না। কত যে টুকরো টুকরো কমিক মোমেন্ট ওই কথাগুলোর মধ্যে বসে থাকে, তার ইয়ত্তা নেই।
“চোরেদের আজকাল যা আস্পর্ধা হয়েছে তা আর কহতব্য নয়। চুরি করতে ঢুকেছিস, কোথায় মিনমিন করবি, ঘাড় হেঁট করে থাকবি, ধরা পড়ে চোখের জল ফেলবি, হাতে পায়ে ধরবি, তা নয় উলটে গলা তুলে ঝগড়া করছিস!"
"ঝগড়া। কস্মিনকালেও কারও সঙ্গে ঝগড়া করিনি মশাই, তবে হ্যাঁ, দরকার হলে উচিত কথা বলতেও ছাড়ি না। আর চোর বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করছেন কেন, চোর কি খেটে খায় না! আপনাদের চেয়ে তাদের খাটুনি বরং অনেক বেশি। আপনারা যখন নাকে তেল দিয়ে রাতে ঘুমোন তখন এই আমাদের রাত জেগে মেহনত করতে হয়। তার ওপর কাজের ঝুঁকিটাই কি কম? ধরা পড়লে গেরস্তের কিল, পুলিশের গুঁতো হজম করতে হয়, বরাত খারাপ হলে কড়া হাকিমের হাতে পড়ে হাজতবাসও আছে। চোর বলে কি মানুষ নই আমরা?"
গবাক্ষবাবু আসলে কুড়িয়ে পেয়েছেন নয়নগড়ে যাবার সেই সূচখানা। সূচ প্রথমে কুড়িয়ে পায় দেড়েল কালী। সূচ থেকে আশ্চর্য আলো বেরোয় দেখে সেটা কোনও দামী জিনিসটিনিস হবে ভেবে সে ওটা বেচতে যায় গ্রামের একজন উচ্চশিক্ষিত বড়লোক সজনীবাবুর কাছে। তিনি পাঁচশোর বেশি দেবেন না শুনে দেড়েল কালী অন্য খদ্দেরদের দেখায় জিনিসটা। শেষে কিছু লোক তাকে মেরেধরে জিনিসটা কেড়ে নেয়। পরে তাদের মধ্যেও লড়াই বাধে। সূচ আবার খোয়া যায়। রাস্তায় কুড়িয়ে পান গবাক্ষবাবু।
এইবার সজনীবাবুও টের পেয়েছেন সূচটা যেমন তেমন সূচ নয়। তিনিও তাঁর চেনা চোরদের কাজে লাগিয়েছেন সূচের সন্ধানে। মাজুম, জ্ঞানও হাত গুটিয়ে বসে নেই। তারাও গ্রামের চোরদের পালা করে এর ওর বাড়িতে পাঠাচ্ছে। সব মিলিয়ে ভারী হুলুস্থূল ব্যাপার চলছে।
পঞ্চা চোরের সাথে গবাক্ষবাবুর লম্বা আলাপচারিতায় গ্রামের সমসাময়িক বেশ কিছু ঘটনার আভাস পেয়ে যায় পাঠক। এই যেমন, সজনীবাবুর বাড়িখানা দুর্গের চেয়ে কম কিছু নয়। পাইক বরকন্দাজ কুকুর মিলে পাহারা দিচ্ছে সে বাড়ি। লোকাল তান্ত্রিক শ্যামাপদ তাঁর ইনফর্মার। আগের পড়া অদ্ভুতুড়েগুলোয় যখনই এমনধারা সাবধানী বড়লোকদের আগমন ঘটেছে, গল্পের শেষে দেখা গেছে তারাই আসলে কালপ্রিট। ২২নম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘হরিপুরের হরেক কান্ড’র সুজনবাবু এমনই এক উচ্চশিক্ষিত বড়লোক, যিনি পরের গুপ্তধন গাপ করতে চেয়েছিলেন। তিনিও এই গল্পের সজনীবাবুর মতো চোর পুষতেন। আবার, সুজন আর সজনী— নামদুটোতেও কেমন মিল!
সজনীবাবুর বাড়িতে কোনও চোর ঢুকতে পারে না।
ও-বাড়িতে চুরি করার প্রেস্টিজই আলাদা। নিখিল নবাবগঞ্জ দলিত তস্কর সমাজে ঢেঁড়া দিয়েছে, ও-বাড়িতে যে চুরি করতে পারবে তাকে সোনার মেডেল দেওয়া হবে।
"অ্যাঁ। দলিত কী যেন বললি।"
"নিখিল নবাবগঞ্জ দলিত তস্কর সমাজ।”
"দলিত! দলিত মানে কী?"
"তা কে জানে মশাই। তবে কথাটা নাকি আজকাল খুব চালু। আমাদের ফটিক লেখাপড়া জানা লোক, ময়নাগড় বাসবনলিনী বিদ্যাপীঠে ক্লাস টেন অবধি নাকি পড়েছিল। সে-ই কথাটা জোগাড় করেছে।"
একবার লক্ষ্মীকান্ত চোর কোনওমতে সজনীবাবুর বেডরুমে ঢুকে পড়েছিল। তারপর—
গবাক্ষবাবু সোৎসাহে বললেন, "কচুয়া ধোলাই খেল বুঝি? সজনীবাবুর পাইক বরকন্দাজ গায়ে গতরে খুব জোয়ান। তাদের রদ্দা খেলে আর দেখতে হচ্ছে না।"
"দুর মশাই! কোথায় রদ্দা! চোরেরা রদ্দার পরোয়া থোড়াই করে। আমাদের হাড় হল পাকা হাড়। কিলিয়ে আপনার হাতে ব্যথা হয়ে যাবে। আমাদের কিছুই হবে না।"
"তা হলে আর লক্ষ্মীকান্তর দুর্দশাটা কী হল? পুলিশের হাতে সোপর্দ হল নাকি?”
"তা হলেও অনেক ভাল ছিল। কিছুদিন ঘানি ঘুরিয়ে ছুটি হয়ে যেত। তা নয় মশাই। তার চেয়ে অনেক খারাপ। সজনীবাবু লক্ষ্মীকান্তকে ক্ষমা করে দিলেন।"
"বাঃ, সে তো মহৎ কাজ!"
"সবটা শুনুন, তারপর ফুট কাটবেন। ক্ষমা করে তারপর তাকে এক বাটি দুধ চিঁড়ে খাইয়ে বসালেন। তারপর সারারাত ধরে উপদেশ দিলেন। উপদেশ শুনতে শুনতে লক্ষ্মীকান্ত বেচারা হেদিয়ে পড়ল। ভোরবেলা পর্যন্ত উপদেশ গেলার পর সে চিঁ চিঁ করতে লাগল।"
গবাক্ষবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "আহা বেচারা! সত্যিই উপদেশের চেয়ে খারাপ কিছু হয় না রে!"
এখন লক্ষ্মীকান্ত সজনীবাবুর টাকায় মুদির দোকান দিয়েছে। তবে গল্প এগোলে জানা যায়, মুদির দোকানটা আসলে মুখোশমাত্র, লক্ষ্মীকান্ত এখন সজনীবাবুর হয়ে ভিনগাঁয়ে চুরির চাকরি নিয়েছে।
তবে পঞ্চাচোর এসেছে মাজুমের দলের হয়ে। সে অবশ্য মাজুমকে চেনে তল্লাটে নতুন আসা তারা তান্ত্রিক নামে। সূচ খুঁজতে এসে সে গবাক্ষবাবুকে বুঝিয়ে দিয়ে গেল ও সূচ যে সে সূচ নয়।
পরদিন সকালে অবশ্য গল্প এগোয় আর পাঁচটা দিনের মতোই, আগের রাতের রহস্যের কোনও চিহ্ন থাকে না দিনের আলোয়। সজনীবাবু প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন। সামনে পড়েছেন স্কুলের বাংলা শিক্ষক নরহরিবাবু। এই স্কুলটি আসলে সজনীবাবুর বাবার নামে স্থাপিত স্কুল, যার হর্তাকর্তা সজনীবাবুই। তাঁকে দেখেই নরহরিবাবু বেশ তৈলাক্ত গুডমর্নিং জানালেন, ‘পেন্নাম হই সজনীবাবু, প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়েছেন বুঝি!’ নরহরিবাবু তখন মুড়ি আর নারকেলকোরা দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ব্রেকফাস্ট সারছিলেন। সজনীবাবু এমনিতে গম্ভীর রাশভারী মানুষ। তবে সেদিন যে তাঁর কী হল, দুষ্টুমি করে ভালোমানুষের মতো নরহরিবাবুকে বললেন, ‘’আচ্ছা, কাল থেকে একটা শব্দের মানে খুঁজে পাচ্ছি না। আপনি কি বলতে পারেন ‘কল্যবর্ত’ কথাটার মানে কী?’’ নরিহরিবাবু স্পিকটি নট। ব্যস্। সেই যে শুরু হল, ‘কল্যবর্ত’ শব্দটা একখানা ঝড়ই তুলে দিল গোটা গাঁয়ে।
নরহরিবাবুর গিন্নি অবশ্য খুব ভালোমানুষ, তিনি বলেছেন, ‘"এ তো আরবি ফার্সি শব্দ বলে মনে হচ্ছে। তা অত ভেঙে পড়ার কী আছে! ডিকশনারিতে অমন শক্ত শক্ত শব্দ অনেক থাকে। সবাই কি আর সব কিছুর মানে জেনে বসে আছে? তুমি মুড়ি খাও তো।"
কিন্তু বাকিরা তো এমন দরাজ দিল নয়।
পাশের বাড়িতেই থাকেন গবাক্ষবাবু, তাঁর ভাই অলিন্দবাবু। সজনীবাবুর প্রশ্নটা গবাক্ষবাবু শুনতে পেয়েছেন, কারণ তাঁর দাঁতন থেমে গিয়েছিল। অলিন্দবাবুও শুনেছেন, কারণ বৈঠকি ছেড়ে তিনি রেলিঙের ওপর দিয়ে ঝুঁকে নরহরিবাবুর দুর্দশা দেখছিলেন। জানলার কাছে এগিয়ে গিয়ে নরহরি শুনতে পেলেন, অলিন্দবাবু উত্তেজিতভাবে বলছেন, "এঃ, এই ইস্কুলে আর ছেলেটাকে পড়ানো যাবে না দেখছি। বাংলার মাস্টার যখন এমন সোজা শব্দটার অর্থ বলতে পারল না তখন ইস্কুলের অবস্থা তো বুঝতেই পারছ!"
কিন্তু মজার কথা হল, তাঁরাও ‘কল্যবর্ত’ শব্দের অর্থ জানেন না। শুধু তাই নয়, নিজেদের অজ্ঞতাটা চাপা দেওয়ার জন্য তাঁদের কসরতও চোখে পড়ার মতো!
"তা আর বলতে। শব্দটা কী যেন! ওই সময়ে একটা কাক এমন কা করে ডেকে উঠল যে, শুনতে পাইনি।"
"শোনোনি? আরে কল্যবর্ত, কল্যবর্ত।"
"অ। তা এ তো বেশ সোজা জিনিস। আমারই ভারী চেনা-চেনা ঠেকছে। মানেটা পেটে আসছে, মুখে আসছে না।"
"আরে কল্যবর্ত হচ্ছে এক ধরনের মর্তমান কলা। অ্যাই বড়-বড় সাইজের হয়। আমার শ্বশুরবাড়ির দিকে তো কল্যবর্তের ঝাড়।"
নরহরিবাবু দিশেহারা হয়ে সামনে বসে থাকা জ্ঞানপাগলাকে ডাকেন। দুটো টাকা ঘুষ দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, ‘কল্যবর্ত’র অর্থ। সে ঠোঁট উলটে বলে দিল, ‘সেটা আর শক্ত কী? সকালের জলখাবারকেই কল্যবর্ত বলে।’
এত সহজ অর্থ নরহরি আশা করেননি। তিনি ভাবলেন জ্ঞানপাগলা ভুলভাল বকে গেল।
ওদিকে গ্রামে ঢিঢি পড়ে গেছে। আলুওলা শ্রীদাম পর্যন্ত খিল্লি করছে নরহরিবাবুকে নিয়ে। বিপিন উকিল হেঃ হেঃ করে আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন কল্যবর্ত মানে— “কল্য মানে কাল, মানে আগামী কালই ধরুন। আর বর্ত মানে বেঁচেবর্তে থাকা। সোজা মানেটা দাঁড়াল, যা বাজার পড়েছে, দিনকালের যা অবস্থা, তাতে আগামী কাল অবধি বর্তে থাকলেই বাঁচি। বুঝলেন?" ব্যায়ামবীর যোগেনবাবু বললেন— “ভুল শুনেছেন। ওটা হবে কলাপাত্র। মানেও খুব সোজা, কলার পাতা।”
নরহরিবাবু ধরেই নিয়েছেন, এইবার তাঁর চাকরিটি যাবে। বাংলার মাস্টার কল্যবর্ত মানে জানে না, তার চাকরি আর থাকে?
শ্যামা তান্ত্রিকের সঙ্গে সজনীবাবুর খাতির, গ্রামের সবাই জানে। নরহরিবাবু শ্যামা তান্ত্রিকের কাছে হত্যে দিতে গেলেন। তান্ত্রিকও কম পণ্ডিত না, সে কল্যবর্তের মানে করল— ‘মহাকালের ঘূর্ণিঝড়’! পাঁচটাকা প্রণামী দিয়ে নরহরিবাবু স্কুলে গেলেন।
স্কুলেও ঢিঢি পড়েছে। অভিভাবকেরা সবাই ক্ষুব্ধ। হেডমাস্টার তেজেনবাবু সেন্সিবল মানুষ।
তেজেনবাবু গম্ভীর মুখে বললেন, "পৃথিবীর সেরা পণ্ডিতরাও সব শব্দের অর্থ জানেন না। যাই হোক, অভিভাবকরা কেউ কি শব্দটার অর্থ জানেন?"
অভিভাবকরা একটু মুখ চাওয়াচাওয়ি করে নিলেন। নৃপেন বৈরাগী বললেন, "এর মানে হচ্ছে ইয়ে আর কি। ওই যে-যাকে বলে-"
আর এক অভিভাবক সুধীর বৈষ্ণব বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো-খুব সোজা মানে, ওটা হচ্ছে গিয়ে-"
তৃতীয় অভিভাবক হরিপ্রিয় দাস বললেন, "আরে কলিকালের শেষ যখন হয় তখনই হয় কল্যবর্ত।"
তেজেনবাবু গুরুগম্ভীর গলায় বললেন, "আপনারা বসুন, দক্ষিণাবাবুকে লাইব্রেরি থেকে বাংলা অভিধান আনতে পাঠিয়েছি। তিনি এলেন বলে।"
লাইব্রেরি খুলে দেখা গেল, জ্ঞানপাগলাই সঠিক উত্তর দিয়েছিল! কল্যবর্ত-র অর্থ প্রাতরাশ।
সজনীবাবুর বাড়ির সান্ধ্য আড্ডায় ফের কথা উঠল কল্যবর্ত নিয়ে। যারা যারা ভুলভাল অর্থ বলেছিল সবাই সজনীবাবুর তোষামোদকারী গোছের লোক। এদের মুখেন মারিতং জগৎ। কথায় কথায় সজনীবাবু জেনে ফেললেন জ্ঞানপাগলা একমাত্র লোক, যে শব্দটার মানে ঠিক বলেছিল। সজনীবাবু আরও একখানা শব্দবাণ ছুঁড়লেন!
নৃপেনবাবু হঠাৎ খেঁচিয়ে উঠে বললেন, "এঃ, জ্ঞানপাগলা বড় পণ্ডিত এসেছেন কিনা। কল্যবর্ত মানে তো আমরাও জানতুম। কী বলো সুধীর, কী বলো হরিপ্রিয়?”
"হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিকই তো।”
"হেডমাস্টার তেজেনবাবু যখন আমাদের জব্দ করার জন্য উলটে আমাদেরই কল্যবর্ত মানে জিজ্ঞেস করল তখন আমরা তো বুক ফুলিয়েই বলে দিলুম যে, কল্যবর্ত মানে সকালের জলখাবার। শুনে তেজেনবাবু চুপসে গেলেন।"
সজনীবাবু ভারী অবাক হয়ে বললেন, "তাই নাকি? তা হলে তো বলতে হয় আপনারা বেশ জ্ঞানী লোক।”
নৃপেনবাবু লজ্জার ভাব করে বললেন, "না, না, এ আর এমন কী!"
সজনীবাবু মৃদু-মৃদু হেসে বললেন, "আমি আরও একটা শব্দ নিয়ে বড় ধন্ধে পড়েছি। তা আপনারা জ্ঞানী মানুষ, বলতে পারেন এসকলাশি শব্দটার সঠিক অর্থ কী হবে?"
আর তক্ষুণি—
“নৃপেনবাবু হঠাৎ শশব্যস্তে উঠে পড়ে বললেন, "এই রে, নাতিটার সকাল থেকে জ্বরভাব, দোকান থেকে ওষুধ নিয়ে যেতে হবে। এক্কেবারে মনে ছিল না।"
সুধীরবাবুও তড়াক করে উঠে পড়ে বললেন, "গেল বোধ হয় আমার ছাতাটা। ভুল করে ছাতাটা দিনু মুদির দোকানে ফেলে এসেছি।”
উঠি-উঠি ভাব করে হরিবাবু বললেন, "সকাল থেকে মাথাটা ঘুরছে। শশধর ডাক্তারকে একবার প্রেশারটা না দেখালেই নয়।"
তিনজনেই উঠে পড়েছেন দেখে সজনীবাবু মৃদু হেসে বললেন "আরে তাড়া কীসের? শব্দটার অর্থ আজ না বললেও চলবে। বসুন, বসুন, চা আর পাঁপড়ভাজা আসছে।”
তিনজনেই ফের বসে পড়লেন।”
এই পার্টিকুলার জাতটা আমাদের আশেপাশেই থাকে সর্বক্ষণ। চায়ের দোকানে, মুদির দোকানে, রেশনের লাইনে, ক্লাবঘরে, ফেসবুকে এমন কিছু লোক থাকবেই, যারা প্রত্যেকে কোহলির চেয়ে বেশি ভালো ক্রিকেট বোঝে, মেসির চেয়ে অনেকগুণে ভালো ফুটবল বোঝে, মোদী-মমতার চেয়ে ভালো পলিটিক্স বোঝে, এমনকি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বেশি ভালো করে রবীন্দ্রনাথকে বোঝে! অদ্ভুতুড়ে সিরিজে এত বেশি সারকাজমের ঝাঁঝ আগে ছিল না। সঠিক হিসেব কষে বলা মুশকিল, তবে দেখা যাচ্ছে ২০০০ সালের পরে লেখা অদ্ভুতুড়েগুলো সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে আরও বেশি স্মার্ট হয়ে উঠছে। কিশোরপাঠ্য হাস্যকৌতুকের পাশাপাশি বেশ পরিণতমনস্ক সারকাস্টিক কথোপকথনও মজার মোড়কে লেখক পরিবেশন করছেন।
সান্ধ্যআড্ডার সেই তিন পণ্ডিত জ্ঞানপাগলাকে দশটা টাকা দিয়ে জেনে নেন, ‘এসকলাশি’ হল ইংরেজি ‘স্কলারশিপ’ শব্দের অপভ্রংশ। ওদিকে সজনীবাবুও টের পেয়েছেন জ্ঞানপাগলা মোটেই সাধারণ পাগল ছাগল নয়। তিনি শ্যামা তান্ত্রিককে পঞ্চাশ টাকা দিয়ে জ্ঞানপাগলার খোঁজ নিতে বললেন।
শ্যামাতান্ত্রিকও কল্যবর্তর মানে ভুল বলেছিল। নতুন আসা তারা তান্ত্রিকের ওপর সে মহা খাপ্পা। সেই বড় তান্ত্রিক, সেটা লোককে জানাতে তো হবে! তাই তারার নাম শুনলেই সে হুঙ্কার ছেড়ে বলে, ‘কাঁচ্চা খেয়ে নেবো! চিব্বিয়ে খেয়ে নেবো!’ ঠিক এ জায়গাতেই মনে পড়ে যায় ১৬ নম্বর অদ্ভুতুড়ে ‘ছায়াময়’এর কালী কাপালিককে। সে ব্যাটাও ছিল শ্যামা তান্ত্রিকের মতোই ভেকধারী। কালী কাপালিকের মতো শ্যামাতান্ত্রিকও গল্পে কমিক রিলিফ আনার কমতি রাখেনি।
“বজ্র গম্ভীর স্বরে দু'বার 'কালী, কালী' বলে শ্যামা রাস্তায় নেমে পড়ল। বৃষ্টির তোড় একটু বেড়েছে, বাতাসের জোরও। রাস্তাঘাট যেমন নির্জন তেমনই অন্ধকার।
দ্বিতীয় চেলা একটা টর্চ জ্বেলে বলল, "একটু দেখে চলবেন বাবা। রাস্তায় জল জমে গেছে।"
শ্যামা সবেগে জল ঠেলে হাঁটতে হাঁটতে বলল, "ওরে, টর্চের আলোতে কি আমি পথ দেখি? আমি দেখি ধ্যানের চোখে, তৃতীয় নয়নে। সামনে মা হাঁটছেন, দেখতে পাচ্ছিস না? ওই দ্যাখ শ্যামা মা কেমন মল বাজাতে বাজাতে চলেছেন। দেখতে পাচ্ছিস?"
"আমাদের পাপী চোখ বাবা, এই চোখে কি দেখা যায়?"
"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ।”
অট্টহাসি শেষ হওয়ার আগেই হঠাৎ দশাসই চেহারা নিয়ে গদাম করে উপুড় হয়ে পড়ে গেল শ্যামা। তারপরই আর্ত চিৎকার, "বাবা রে!"
এই ধরনের দৃশ্যগুলো এমন করে শীর্ষেন্দু লেখেন, পড়লে খুব সহজেই ভিস্যুয়ালাইজ করে নেওয়া যায়। এখনও কেন যে গল্পটা নিয়ে সিনেমা বানানো হল না, কে জানে!
এইবার গল্প এগোয় দ্রুতগতিতে ক্লাইম্যাক্সের দিকে। গবাক্ষবাবু সূচটা নিয়ে খুটখাট করতে করতে হঠাৎ জ্বালিয়ে ফেলেন আশ্চর্য আলোটা। আলো দেখে মাজুম হাজির। আর সেইসময়ে সজনীবাবুর পোষা চোর লক্ষ্মীকান্তও ছিল ঘরের মধ্যে। সে গিয়ে খবর দেয় সজনীবাবুকে। আরও জানায়, জ্ঞানপাগলা রীতিমতো কমব্যাট এক্সপার্ট। লক্ষ্মীকান্ত তাকে লাঠির বাড়ি মারতে গিয়েছিল গবাক্ষবাবুর ঘরে চুরি করতে সুবিধে হবে বলে। জ্ঞানপাগলা ঘুষি বসিয়ে তার মুখ ফাটিয়ে দিয়েছে।
লক্ষ্মীকান্তকে বিদেয় করে সজনীবাবু নিজেই চললেন গবাক্ষবাবুর বাড়ির দিকে। পথে দেখা হল অচেনা মুলুকের অচেনা চোরদের সঙ্গে। গবাক্ষবাবুর বাড়ি গিয়ে দেখা গেল, মাজুম এসে গবাক্ষবাবুকে তুলে নিয়ে গেছে, মেরে আধমরা করে ফেলে রেখে গেছে লোভী লক্ষ্মীকান্তকে যে কিনা সূচের লোভে ফের এসেছিল।
মাজুমের চোখে আলো সয় না। গবাক্ষবাবু ভুল করে টর্চের আলো তার মুখে ফেলায় মাজুম কিছুক্ষণের জন্য রাতকানা হয়ে গেছে। সে তাই গবাক্ষবাবুকে ধরে এনেছে যাতে গবাক্ষবাবু মাজুমকে পথ দেখিয়ে জটেশ্বরের জঙ্গলে নিয়ে যেতে পারেন।
ওদিকে জ্ঞানপাগলার সাথে কথা বলে সজনীবাবু বুঝতে পেরেছেন পরিস্থিতি কতখানি ঘোরালো। তিনি এখন জ্ঞানকে সাহায্য করছেন। জঙ্গলে এসে হাজির হয়েছে প্রায় গোটা গ্রাম। বেশ একখানা হুড়ুদ্দুম ফাইট হল। তারপর? সব ভালো যার শেষ ভালো। যুবরাজ জ্ঞান মাজুম আর তার দলকে নবাবগঞ্জে নির্বাসনে রেখে সূচ নিয়ে চলে গেল নয়নগড়। আর মাজুমরা শত্রুতা ভুলে শ্যামা তান্ত্রিকের চেলা হয়ে গেল।
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১ - মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২ - গোঁসাইবাগানের ভূত - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩ - হেতমগড়ের গুপ্তধন - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৪- নৃসিংহ রহস্য - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৫ - বক্সার রতন - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৬ - ভূতুড়ে ঘড়ি - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৭ - গৌরের কবচ - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৮ - হীরের আংটি - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৯ - পাগলা সাহেবের কবর - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১০ - হারানো কাকাতুয়া - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১১ - ঝিলের ধারে বাড়ি - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১২ - পটাশগড়ের জঙ্গলে - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৩ - গোলমাল - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৪ - বনি - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৫ - চক্রপুরের চক্করে - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৬ - ছায়াময় - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৭ - সোনার মেডেল - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৮ - নবীগঞ্জের দৈত্য - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১৯ - কুঞ্জপুকুরের কাণ্ড - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২০ - অদ্ভুতুড়ে - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২১ - পাতালঘর -আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২২ - হরিপুরের হরেক কাণ্ড -আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৩ - দুধসায়রের দ্বীপ - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৪ - বিপিনবাবুর বিপদ - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২৫ - নবাবগঞ্জের আগন্তুক - আলোচনার লিংক
