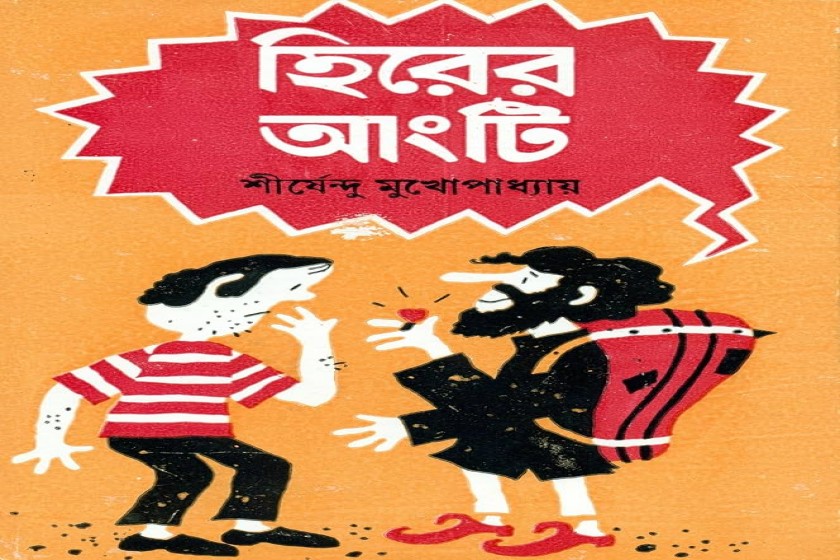
হীরের আংটি : শীর্ষেন্দুর অদ্ভুতুড়ে সিরিজের অষ্টম আখ্যান
- 28 December, 2024
- লেখক: মনীষা নস্কর
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ১ - মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ২ - গোঁসাইবাগানের ভূত - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৩ - হেতমগড়ের গুপ্তধন - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৪- নৃসিংহ রহস্য - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৫ - বক্সার রতন - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৬ - ভূতুড়ে ঘড়ি - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৭ - গৌরের কবচ - আলোচনার লিংক
অদ্ভুতুড়ে সিরিজ ৮ - হীরের আংটি - আলোচনার লিংক
মাঝে মাঝে ফাঁকা সময় পেলে ভাবতে বেশ ভাল্লাগে, এই একটা ইয়াব্বড় ট্রলিব্যাগ কুড়িয়ে পেলাম, খুলে দেখি থরে থরে সাজানো কড়কড়ে দু’হাজার টাকার বান্ডিল। কিংবা কোনও ভুলোমনের ডাকাত ব্যাঙ্ক লুটে ফেরার পথে টাকাভর্তি ব্যাগটা ফেলে রেখে গেল ফুটপাথে, আর পড়বি তো পড়, আমারই চোখে পড়ে গেল। তখন কী করব? সবার আগে তো ফ্লাইটের টিকিটটা কাটবো, তারপর সোজা উড়তে থাকবো। ইজিপ্টের মমি দেখে আসবো। স্কটল্যান্ডের অ্যানিক কাসলের পাথরগুলোয় হাত বুলিয়ে আসবো। জাপানে গিয়ে সুশি খেয়ে আসবো। আন্টার্কটিকায় ক্রুজ পার্টি করবো পেঙ্গুইনদের সাথে। সাউথ কোরিয়াতে স্নোফল দেখতে যাবো। গ্রিসে গিয়ে সান্তোরিনিতে বসে ওয়াইন খাবো। ডাবলিনে হ্যালোউইন ফেস্টিভ্যাল দেখে আসবো। নরওয়ে গিয়ে আলোভর্তি আকাশ দেখবো। অস্ট্রেলিয়ার পিংক লেকে পা ডোবাবো। ল্যুভর থেকে শুরু করে বিশ্বের সবকটা তাবড় তাবড় মিউজিয়াম ঘুরে আসবো। আর.. আর.. উঁহুঁ, দেখার শেষ নেই। আলটপকা কিছু পয়সাকড়ি হাতে এলে জমিয়ে রাখা স্বপ্নগুলোর পাশে টিকমার্ক দেওয়ার জন্য হাত নিশপিশ করে। কেউ কিনতে চায় শখের গাড়িটি, কেউ বা কেনে বিলাসবহুল বাংলোবাড়ি। কিন্তু একজন চায় সে বারোটা গামছা কিনবে। রোজ ইলিশ মাছ আর কাটোয়ার ডাঁটা খাবে। তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি খাবে। এইটুকুই তার শখ, স্বপ্ন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা। সে হল ষষ্ঠীচোর!
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়ের অদ্ভুতুড়ে সিরিজে এযাবৎ অনেক অদ্ভুত কিসিমের লোকের দেখা মিলেছে। কিন্তু ষষ্ঠীচোরের মতো মানুষ এল এই প্রথমবার। অদ্ভুতুড়ে সিরিজের আটনম্বর গল্প ‘হিরের আংটি’, উপন্যাসিকা না বলে একে বড়গল্প বলাই সঙ্গত। মোটে সত্তরপাতা এর আয়তন। ১৯৮৬-র জুনে এইটি প্রকাশিত হচ্ছে। এর ঠিক আগের গল্প ‘গৌরের কবচ’ এসেছে একই বছরের জানুয়ারিতে। প্রকাশকালের সময়ের ব্যবধান অল্প। লেখাদুটোও কি অল্প সময়ের ব্যবধানে লেখা? গৌরের কবচ অত্যন্ত এলোমেলো, খাপছাড়া। অদ্ভুতুড়ে সিরিজের সিগনেচার টোনটাই সেখানে বেপাত্তা। কমিক রিলিফ নেই। গল্পের হিরোটি হাবাগোবা, টুকটাক হিরোত্ব দেখালেও শ্রদ্ধার বদলে বিরক্তিই আসে। বরং সেখানে ভিলেনটি ছিল জবরদস্ত। সে দুষ্টু লোক হলেও হিরোর চেয়ে হাজারগুণ বেশি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। মেঠো গ্রামবাংলার ব্যাকড্রপ থাকলেও ক্লাইম্যাক্সে বড় বেশি হলিউডি মারমার কাটকাট গোছের চড়াসুরের ভাইব। তুলনায় পরের গল্প ‘হিরের আংটি’ অনেক বেশি নরমসরম। আগের গল্পে কবচ নিয়ে হুজ্জুতি। এ গল্পে আংটি নিয়ে। দুটো গল্পে মিল অনেক। রাঘবের মতোই এ গল্পেও একজন এসেছে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে। তবে ‘হিরের আংটি’ এইজন্যই আলাদা বলব, এ গল্পে অদ্ভুতুড়ে সিরিজের চেনা ছকটা ফিরে এসেছে। হাসি-ঠাট্টা-মজার প্রলেপটা না থাকলে বড় অস্বস্তি হয়, ‘গৌরের কবচ’ পড়তে গিয়েই তা হাড়ে হাড়ে বোঝা গেছে।
‘হিরের আংটি’ গল্প শুরু হচ্ছে ষষ্ঠীচোরকে দিয়ে, শেষও হচ্ছে তাকে দিয়েই। সে এক ভারী মজার চরিত্র, তার কথায় পরে আসছি। আগে গল্পটুকু ছোট্ট করে বলে নেওয়া যাক। হাবুলের দাদু দূরদেশে এক রাজাগোছের লোকের অধীনে কাজকর্ম করতেন। সে লোকের মন্দিরে গুপ্তধন খুঁজে পান, অজস্র মণিমুক্তোর সঙ্গে ছিল দুটো একইরকম দেখতে হীরের আংটি। রাজাটি খুব বিশ্বাস করতেন হাবুলের দাদুকে। গুপ্তধনের বখরা নিয়ে শরিকে শরিকে খুনোখুনি হতে শুরু হয়। রাজা তাঁর নাতিকে নিয়ে পালিয়ে যান। পালানোর আগে গুপ্তধন গোপনে হাবুলের দাদুকে দিয়ে দেন রাজামশাই, চুক্তিবদ্ধ করিয়ে নেন আগামী পঁচিশ বছরের মধ্যে যদি রাজার নাতি গিয়ে পৌঁছয় হাবুলের দাদুর কাছে, তবে গুপ্তধন তাকেই ফেরত দিতে হবে। সব ঠিক আছে কিনা দেখার জন্য বৈশাখী অমাবস্যার রাতে রাজার দুই লেঠেল শ্বেত আর লোহিত আসতে থাকবে বছর বছর। গুপ্তধন নিয়ে হাবুলের দাদু দেশে ফিরেছেন, সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তবে গুপ্তধন আগলে রেখেছেন রাজার নাতির জন্যই। কপালজোরে পাওয়া পয়সাকড়ি নিয়ে এতটুকু বাবুয়ানি তিনি নিজে তো করেনইনি, বাড়ির কোনও সদস্যকেও বুঝতে দেননি গুপ্তধনের অস্তিত্ব। ‘গোঁসাইবাগানের ভূত’ মনে আছে তো? বুরুনের বাবা-দাদু বুরুনকে শাসনের ছলে স্বাবলম্বী হতে শিখিয়েছিলেন। এ গল্পেও হাবুলের দাদু হাবুলকে অনবরত বলেন নিজের কাজ নিজে করতে। জুতো বুরুশ থেকে জল নিয়ে খাওয়া, সবটুকুই ছোট্ট হাবুল শিখে ফেলেছে। ছোটদের লেখায় বড়রা একটু উপদেশ টুপদেশ দেবেন, সেটা খুবই স্বাভাবিক। তবে শীর্ষেন্দু ছোটদের পালসটা ভালো বোঝেন। অ্যায়সা কায়দা করে হাবুলের অভ্যেসগুলোর কথা বলে দিলেন, আমিই জলের জন্য হাঁক পাড়তে গিয়ে কোনওমতে সামলে নিয়ে নিজেই জলটা নিয়ে এলাম।
‘‘বাড়িতে এতগুলো কাজের লোক থাকলেও হাবুলকে নিজের সব কাজ নিজেকেই করে নিতে হয়। দাদুর সেইরকমই আদেশ আছে। সে নিজের জামাকাপড় নিজে কাচে, নিজের জুতো নিজেই বুরুশ করে, নিজের ঘরখানাও তাকেই ঝাড়পোঁছ করতে হয়, নিজের এঁটো থালাও মাজতে হয়। দাদু বলেন, “দেখ হাবুল, এ-দেশটা গরিব বলে আমরা কাজের লোক রাখতে পারি। কিন্তু দেশটা যদি উন্নত হত, তা হলে কম পয়সায় কাজের লোক রাখা সম্ভব হত না। সব কাজ নিজেকেই করতে হত। একদিন যখন দেশটার ভোল পাল্টাবে, তখন তো কাজের লোকের অভাবে তোরা অথই জলে পড়বি। তার চেয়ে অভ্যাস রাখা ভাল। আর নিজের কাজ নিজে করলে আত্মবিশ্বাস বেড়ে যায়।” আমি নিশ্চিত, ১৯৮৬-র জুনে এ গল্প যারা পড়েছিল, অন্তত একহপ্তার জন্য তাদের মায়েদের মুখে হাসি ফুটেছিল!
গল্পে ফেরা যাক। হাবুলের দাদুর কাছে এসে হাজির হয়েছে রাজার নাতি, গন্ধর্ব। তাকে দেখে হাবুলের ভারী পছন্দ হয়ে গেছে। সাতটা অদ্ভুতুড়ে পড়ার পর খানিকটা যেন অভ্যেসই হয়ে গেছে এইটি ধরে নেওয়া যে, ছোট বাচ্চাটির যে চরিত্রটিকে মনে ধরবে, সেইটিই ভালোমানুষ। কিন্তু ‘হিরের আংটি’তে আবার ছকভাঙা এক্সপেরিমেন্ট। গন্ধর্ব আসলে চোর। গন্ধর্ব শ্বেতের ছেলে। আসল রাজার নাতি মরে গেছে সেই ছোটবেলাতেই। নকল গন্ধর্ব এসেছে গুপ্তধন নিয়ে যেতে। হয়তো নিয়েও যেত। কিন্তু বাদ সাধলো ষষ্ঠীচোর। গন্ধর্বকে প্রথমবার দেখেই সে তার পিছনে লেগে রইল তার আঙুল থেকে হিরের আংটি হাতানোর জন্য। ওই আংটি বেচে সে টাকা পাবে, তাই দিয়ে বুনে নেবে তার স্বপ্নগুলো— “হিরেটা যদি খাঁটি হয়, তাহলে ষষ্ঠী বন্দুক কিনে ফেলছেই। তারপর দুমদাম দু'দশটা করে লাশ পড়তে থাকবে তার হাতে। হাজার-হাজার লাখ-লাখ টাকা লুটেপুটে নিয়ে আসবে চারদিক থেকে। গণেশ কাংকারিয়ার গদি সাফ করবে, বৈজু লালোয়ানির বাড়ির ঠাকুরঘর থেকে লুকোনো সোনা বের করবে, যতীন সামন্তর বন্ধকি কারবারে জমা হওয়া জিনিসপত্র সোনারুপো গোরুর গাড়িতে চাপিয়ে তুলে নিয়ে আসবে। শহরের দুটো ব্যাংকে ডাকাতি করলে মোটা টাকাই এসে যাবে হাতে। কয়েক লাখ টাকা হলে ষষ্ঠী তখন জুতো মসমসিয়ে নতুন লুঙ্গি পরে বিড়ি ফুঁকতে ফুঁকতে বাজার থেকে রোজ ইলিশ মাছ আর কাটোয়ার ডাঁটা কিনে আনবে। ও দুটো খেতে সে খুব ভালবাসে। আর তেলেভাজা দিয়ে মুড়ি, রোজ খাবে। ভাবতে ভাবতে জিবে জল এসে গেল তার। উত্তেজনায় গাছের গুঁড়িতে একটা কিলও দিয়ে বসল।”
কিন্তু ষষ্ঠীচোরের ভাগ্যটা মোটেই তেমন সাথ দিচ্ছে না। গন্ধর্বকে জপিয়ে সে তাকে নিয়ে এল বটে কালী স্যাকরার আস্তানায়। কিন্তু গন্ধর্ব যে চুরিবিদ্যেয় ষষ্ঠীচোরের গুরুদেব, তা তো ষষ্ঠী জানে না। কড়কড়ে চারশোটাকা পকেটে পুরে হাতসাফাই করে আসল আংটি সরিয়ে জাল আংটি গছিয়ে চলে গেল গন্ধর্ব। ব্যাপার যখন বুঝল ষষ্ঠী, সে রাগের মাথায় পাঁচশো টাকা কবুল করে ভাড়া নিল টিকেগুণ্ডাকে। প্ল্যানমাফিক নিশুতি রাতে গন্ধর্বকে ঘুমপাড়ানি ওষুধ স্প্রে করে আংটি হাতিয়ে তারা চলল কালী স্যাকরার কাছে। গন্ধর্ব কিন্তু জাত চোর। ঘুমের ওষুধে তার কচু হবে! সে আগেই কালী স্যাকরাকে ঠেঙিয়ে চাট্টি সোনাদানা লুটে এনেছে। টিকেগুন্ডা এতক্ষণে বুঝে গেছে এ পাঁচশোটাকার কাজ নয়, লাখটাকার আংটির গুরুতর কেস। ষষ্ঠীকে দুটো রদ্দা দিয়ে নিজেই ভাগ নিয়ে নিল দশহাজার টাকা, ষষ্ঠী পেল পাঁচশো। আংটি রইল কালীস্যাকরার জিম্মায়। আর গন্ধর্বও হাজির হল সময়মতো। কালীস্যাকরা দ্বিতীয় দফা ঠ্যাঙানি খেল, আংটি তো গেলই সঙ্গে হাপিশ হল গোপন সিন্দুকের পয়সাকড়িও। ওদিকে টিকেগুন্ডা আর ষষ্ঠীচোরের জন্যও বরাদ্দ ছিল একপ্রস্থ মার। গন্ধর্ব তাদের পিটিয়ে টাকাগুলো নিয়ে কেটে পড়ল।
জ্ঞান ফেরার পর ষষ্ঠীচোরের রিঅ্যাকশন দেখলে হাসি চাপা দায়! ‘‘কিছুক্ষণ ঝিম মেরে বসে থেকে আবার চোখ খুলে সে দেখল, টিকে এখনও গন্ধমাদনের মতো পড়ে আছে সামনে। দেখে ফিক করে একটু হেসে ফেলল ষষ্ঠী। তার মোটে পাঁচশো, টিকের গেছে দশ হাজার।
উচিত শিক্ষা হয়েছে। ভগবান যা করেন, মঙ্গলের জন্যই করেন।
কপালের ফের না হলে টিকের যাওয়ার কথা পাঁচশো, আর ষষ্ঠীর দশ হাজার।
দশ হাজার তার ট্যাঁক থেকে গেলে ষষ্ঠী শোকে আর উঠে দাঁড়াতে পারত না।
পাঁচশোর শোক অনেক কম। ষষ্ঠী তাই গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল, গন্ধমাদনটার দিকে তাকিয়ে আবার ফিকফিক করে হাসল সে। পাগলবেশী ডাকাতটা টিকে-কে একটা ল্যাং আর একটা বিরাশি সিক্কার রদ্দা কষিয়েছে। সেই তুলনায় ষষ্ঠীর ভাগে পড়েছে মাত্র একটা গাঁট্টা, ভগবানই চিরকাল গরিবকে দেখেন।”
এইবার গল্প শেষ করতে শীর্ষেন্দু লাগালেন তাড়াহুড়ো। হঠাৎই এসে পড়ল শ্বেত লোহিত। হাবুলদের বাড়ির কুকুরের নাম ছিল টমি, হয়ে গেল জিমি। দুম করে সবাই বুঝে ফেলল গন্ধর্ব নকল রাজকুমার। সে নাকি কোন ফাঁকে হীরের আংটির জোড়াটা যেটা হাবুলের দাদুর কাছে ছিল, সেটাও ঝেড়ে দিয়েছে। কবে, কীভাবে তা লেখকও জানেন না। আংটি গায়েব দেখে হাবুলের দাদুকে খুন করতে যাচ্ছে শ্বেত। হাবুলের কাকা বীরু ধরে আনলেন গন্ধর্ব আর লোহিতকে। তারপর দাদু বেশ সবাইকে ক্ষমাটমা করে দিলেন। ষষ্ঠীচোর দারোয়ানের চাকরি পেল। শেষ দশ বারো পাতা কেন যে এত তাড়াহুড়ো করে লিখতে হয়েছিল কে জানে! দিব্যি এগোচ্ছিল গল্প। কিন্তু না, শেষটায় গিয়ে সব কেমন ঘ্যাঁট পাকিয়ে গেল।
স্টোরিলাইন শুরুতে বাসমতী পোলাও হয়ে শেষপাতে খিচুড়ি হলেও স্বাদেগন্ধে অতুলনীয়। কমিক রিলিফটুকু আগাগোড়া মজুত। ষষ্ঠীচোর না থাকলে এ গল্প পাতে দেওয়ার মতো হত না। তবে এ গল্পে সিনেমা বানানোর মালমশলার কমতি নেই, তা বুঝেছিলেন পরিচালক ঋতুপর্ণ ঘোষ। ১৯৯২তে মুক্তি পায় ‘হিরের আংটি’ ছবিটি। পরিচালক হিসেবে এইটিই তাঁর প্রথম ছবি। এই এক ছবিতেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ঋতুপর্ণ ঘোষ নামটি সিনেমার ইতিহাসে থেকে যাওয়ার জন্যই এসেছে। সিনেমার প্রয়োজনেই বেশকিছু অদলবদল হয়েছে কাহিনিতে, এবং তা একেবারেই যথাযথ। ষষ্ঠীচোরের ভূমিকায় সুনীল মুখার্জির অভিনয় অত্যন্ত সাবলীল। প্রায় শুরুর দিকেই দেখা যায়, হ্যারিকেনের আধো আলো-আঁধারিতে সে গালে হাত দিয়ে বসে স্বপ্ন দেখছে, একদিন তার নিজের ডাকাতদল হবে! কাগজে গোটা গোটা অক্ষরে খরচাপাতির হিসেব কষছে। কাগজের মাথায় কাঁচাহাতে আঁকা একটা খাঁড়া, নীচে ত্যাড়াব্যাঁকা অক্ষরে লেখা— ‘শ্রী শ্রী কালিমাতা সহায় ডাকাত দল খুলিবার খরচ’। ভুলভাল বানানে সে লিস্ট বানাচ্ছে কটা ঘোড়া আনবে, কতগুলো বন্দুক রাখবে! শীর্ষেন্দুর গল্পটি ছিল যেন দুর্গাপুজোর মাটির কাঠামো। তাকে রংচং করে, শাড়ি-গয়নায় সাজিয়ে তোলার কাজটাই করেছেন ঋতুপর্ণ ঘোষ। গল্পে হাবুলের মায়ের দেখা প্রায় মেলেইনি। সিনেমায় মহিলাচরিত্রগুলির ওপর আলাদাভাবে ফোকাস করা হয়েছে। হাবুলের সাথে আরেকজন খুদে চরিত্রের সংযোজন করেছেন পরিচালক, সে হল তিন্নি। গল্পে কাকা বীরুর হঠাৎই আবির্ভাব হয়েছে, সে কীরকম মানুষ, তার বন্ধুবান্ধব কারা, এসবের কোনও হদিশ গল্পে ছিল না। অথচ বীরু চরিত্রটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একজন চরিত্রর মনের কাছাকাছি পাঠককে পৌঁছতে হলে তাকে চেনার জন্য কিছু তো সূত্র চাই। ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবিতে কাকা বীরু সক্কাল সক্কাল ছাদে ব্যায়াম করেন। স্নান না করে বাড়ির বাইরে পা রাখেন না। ভাইপোর ওয়র্ক এডুকেশনের কাজে হেল্প করেন। আর আছে দুর্গাপুজো! বাড়ির দালানে প্রতিমায় রং চলছে। ফর্দমতো বাজার করতে ছুটছেন বীরু। মনে করিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ‘সব মিলিয়ে আনবেন, গেলবারের মতো চাঁদমালাটা ফেলে আসবেন না।’ গল্পে বীরুর যতটুকু পরিচয় পাওয়া গেছে, তা খুবই সামান্য। অতটুকু ইনফরমেশনে কোনও চরিত্রই দাঁড়াতে পারে না। গল্পে যেখানে যতটুকু খামতি ছিল, সবটুকুই যত্ন করে পলিশ করেছেন ঋতুপর্ণ। এ গল্প পড়ার পাশাপাশি ‘হিরের আংটি’ ছবিটি দেখলে গল্পের চরিত্রগুলো পাঠকের কাছে আরও বেশি জীবন্ত হয়ে উঠবে, তা বলাই বাহুল্য।
