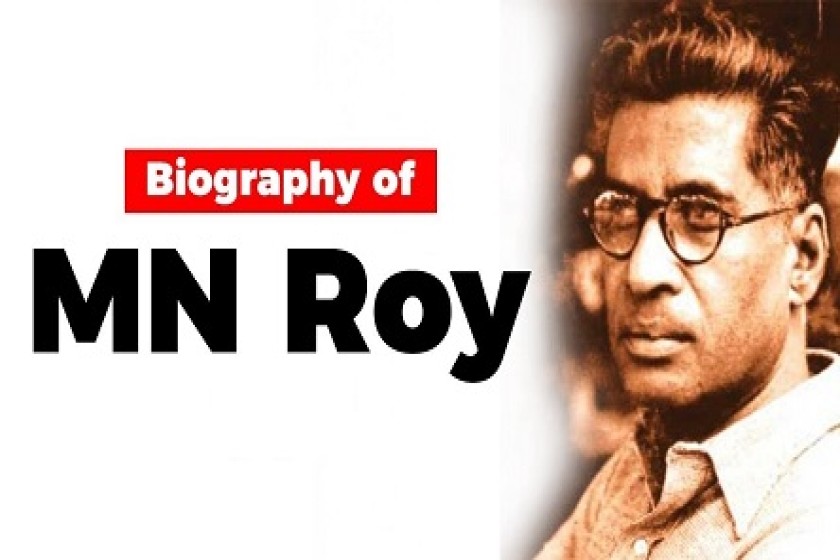
এম এন রায় : বর্ণময় জীবন ও রাজনীতি
- 07 November, 2025
- লেখক: সৌভিক ঘোষাল
মানবেন্দ্রনাথ রায় : (১৮৮৭ – ১৯৫৪)
১
মানবেন্দ্রনাথ রায়ের আসল নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, কিন্তু তিনি এম এন রায় নামেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ হয়ে আছেন। তাঁর বর্ণময় জীবনে এসেছে নানা নাটকীয় উত্থান পতন, চিন্তা প্রক্রিয়াতেও ঘটেছে নানা নাটকীয় বাঁকবদল। সম্মান ও মর্যাদায় তিনি যেমন ভূষিত হয়েছেন, তেমনি বিতর্কও তাঁকে তাড়া করে ফিরেছে অবিরত। তাঁকে নিয়ে কিছু চর্চা নানাসময়ে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও ভারতীয় রাজনীতির মূল ধারাগুলি অনেকদিন ধরেই তাকে খানিকটা একপাশে সরিয়ে রেখেছে। কংগ্রেস বা কমিউনিস্ট কোনও শিবিরই তাঁকে সম্পূর্ণভাবে নিজের লোক বলে মনে করতে পারে নি, যদিও তিনি জীবনের দুই পর্বে এই দুই শিবিরের নেতা হিসেবেই কাজ করেছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক তত্ত্ব প্রায়শই তীক্ষ্ণ চিন্তা ও বুদ্ধির ঝলকে দেদীপ্যমান, এডওয়ার্ড সাঈদ থেকে শুরু করে উত্তর ঔপনিবেশিক তত্ত্ববিশ্বের প্রধান চিন্তাবিদেরা অনেকেই তাঁর দ্বারা প্রভাবিত, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাত্ত্বিক রাজনীতির পরিসরে তিনি এখন আর সেভাবে চর্চিত নন। একুশ শতকের সমাজতন্ত্র নির্মাণের প্রশ্নটি যখন সামনে আসে, তখন অনেকেই মেনে নেন যে বিশ শতকী সমাজতন্ত্র নির্মাণের ভুলভ্রান্তি ও সীমাবদ্ধতাগুলি পেরিয়েই সেদিকে এগোতে হবে। এপথে এগনোর অনেক ইতিবাচক উপাদান এম এন রায়ের নানা লেখায় আছে, কারণ তিনি খুব কাছ থেকে রাশিয়া ও চিনের বিপ্লবী আন্দোলনের নানা দিককে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু একুশ শতকী সমাজতন্ত্র নির্মাণের তাত্ত্বিক ব্যবহারিক রাজনৈতিক পরিসরেও তিনি সেভাবে চর্চিত নন। সাম্প্রতিক সময়ে ভারত এবং বিশ্বের নানা জায়গায় ফ্যাসিবাদ যে নতুনভাবে মাথাচাড়া দিচ্ছে, তার কিছু আগাম ইঙ্গিৎ অনেককাল আগেই তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু সে সব নিয়েও চর্চা খুব দুর্বল জায়গায় আছে। এম এন রায়ের জীবন, কাজ ও তত্ত্বচিন্তাকে মনোযোগের সঙ্গে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করলে কিন্তু আমরা বুঝতে পারি রাজনৈতিক চালচিত্রের একদা নায়ক হিসেবে তিনি শুধু ইতিহাসচর্চার বিষয় নন, সমকালীন এবং অতি অবশ্যই ভবিষ্যৎ রাজনীতিভাবনার ক্ষেত্রে তাঁর কাছ থেকে আমাদের অনেক কিছু পাবার আছে। এই সম্ভাবনার দিকগুলিকে খোলার জায়গা থেকেই আমাদের নতুন করে এম এন রায় চর্চা শুরু করা দরকার।
বাঙালি তরুণ নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যকে আমেরিকায় গিয়ে মানবেন্দ্রনাথ রায় হতে হয়েছিল রাজনৈতিক কারণেই। প্রথম জীবনে তরুণ নরেন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনের দিনকালে বাংলার আরো অনেক যুবকের মতোই জড়িয়ে পড়েছিলেন সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে। ব্যরিস্টার প্রমথনাথ মিত্র প্রবর্তিত যুগান্তর সমিতি তখন বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মকাণ্ডের কেন্দ্র। সে সময়ের বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নেতা ছিলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওরফে বাঘা যতীন। বিপ্লবী কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য টাকা ও অস্ত্র জোগাড় তখন ছিল বিপ্লবীদের প্রধান প্রয়োজন। অর্থের জন্য নির্ভর করা হত স্বদেশী ডাকাতির ওপর। এই সমস্ত গোপন অভিযানে নরেন্দ্রনাথ তাঁর কৌশলী দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন। টাকা লুঠ করে তিনি দলের হাতে তুলে দিয়ে এমনভাবে মিলিয়ে যেতেন যে ইংরেজ পুলিশ শত চেষ্টাতেও তার কোনও খোঁজ পায় নি। একবার নরেন্দ্রনাথ ধরা পড়েছিলেন, পুলিশ লক আপে তার ওপর অত্যাচারও হয়েছিল, কিন্তু কোনও তথ্য তার মুখ দিয়ে বের করা যায় নি। সরকার তাকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়।
প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ বিরোধী জার্মানদের কাছ থেকে অস্ত্র সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের যে প্রস্তুতি শুরু হয়, সেখানেও নরেন্দ্রনাথ সক্রিয় হয়ে ওঠেন। একইদিনে একই সময়ে গোটা দেশের বিভিন্ন ক্যান্টনমেন্টে ব্রিটিশ বিরোধী যুদ্ধ শুরুর যে পরিকল্পনা রাসবিহারী বসুর নেতৃত্বে তৈরি করা হয়েছিল, তা শেষ মুহূর্তে একজনের বিশ্বাসঘাতকতায় বানচাল হয়ে যায়। রাসবিহারীকে দেশ ছেড়ে জাপানে পালিয়ে যেতে হয়। বাঘাযতীন অস্ত্র সংগ্রহ করে নতুন করে লড়াই শুরুর পরিকল্পনা নেন। জার্মানদের সঙ্গে যোগাযোগ করে অস্ত্র আনার জন্য পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার নানা জায়গায় নরেন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়ান। একবার জাপানে গিয়ে রাসবিহারী বসুর সঙ্গেও দেখা করেন। সে সময় চিনের জাতীয়তাবাদী নেতা সান ইয়াৎ সেন চিন থেকে পালিয়ে জাপানে আত্মগোপন করে ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও নরেন্দ্রনাথ দেখা করেন। সান ইয়াৎ সেনের অনুরোধে গোপনে চিনে গিয়ে তিনি সেখানকার জার্মান দূতাবাসের সঙ্গেও যোগাযোগ করে সাহায্য সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছিলেন।
জার্মানদের চেষ্টায় পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া থেকে গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র ভর্তি বেশ কিছু জাহাজ বিপ্লবীদের সাহায্যের জন্য ভারতের দিকে রওনা দিয়েছিল। কিন্তু শেষপর্যন্ত সমস্ত উদ্যোগগুলিই ব্রিটিশ পুলিশ ও গোয়েন্দা দপ্তরের কাছে ধরা পড়ে যায়। বাঘাযতীনকে বুড়িবালামের ধারে অসম যুদ্ধে ইংরেজরা হত্যা করে। নরেন্দ্রনাথের খোঁজে সর্বত্র তল্লাশী শুরু হয়। নরেন্দ্রনাথ পালিয়ে যান আমেরিকায়। সেখানে বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখোপাধ্যায়ের ভাই ধনগোপাল মুখার্জী তাঁকে আশ্রয় দেন। ধনগোপালের পরামর্শেই পরিচয় বদল করে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য পরিণত হলেন মানবেন্দ্রনাথ রায় নামে। নতুন নামে ভর্তি হলেন আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ে। সে সময়ে লালা লাজপৎ রাই আমেরিকায় ছিলেন। এম এন রায়ের সঙ্গে তাঁর আলাপ পরিচয় হল। আমেরিকায় থাকাকালীন সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ ও কার্ল মার্ক্সের লেখালিখির সঙ্গে মানবেন্দ্রনাথের পরিচয় হয়। তিনি সে সব গভীর মনোযোগে অধ্যয়ন করা শুরু করেন ও এই বিষয়ে প্রাজ্ঞ হয়ে ওঠেন। তবে মার্ক্সীয় দর্শন শুধু জ্ঞানতাত্ত্বিক দিক থেকেই এম এন রায়কে ঋদ্ধ করে নি, চিন্তাভাবনার জগৎটাকেও একেবারে পালটে দিল। শুধু রাজনৈতিক ক্ষমতা বদল বা ক্ষমতা দখল নয়, শ্রেণি দৃষ্টিকোণ থেকে ক্ষমতার প্রকৃত পরিবর্তনই যে মুক্তির আসল উপায় সেটা এম এন রায় ুপলব্ধি করেন ও নিছক জাতীয়তাবাদী থেকে রূপান্তরিত হন সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীতে।
বিশ্বযুদ্ধের সেই দিনকালে আমেরিকার সঙ্গে ব্রিটিশের সম্পর্ক ভালো ছিল। আমেরিকার বুকে শুরু হওয়া গদর আন্দোলন নিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আগে থেকেই দুশ্চিন্তা ছিল। তাঁদের নিশানায় নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে এম এন রায়ের নামও ছিল। একবার আমেরিকান কর্তৃপক্ষের হাতে তিনি গ্রেপ্তারও হলেন। আমেরিকায় নাম বদলে থাকাটাও নিরাপদ হবে না বুঝতে পেরে তিনি গোপনে আমেরিকা থেকে চলে গেলেন মেক্সিকোতে।
মেক্সিকোতে গিয়ে সমাজতন্ত্রে নবদীক্ষিত এম এন রায় কাজ শুরু করলেন নতুন করে। তখন তিনি একজন আন্তর্জাতিকতাবাদী। ফলে যে দেশের যেখানেই থাকুন না সেটাই তাঁর শ্রেণিসংগ্রামী রাজনীতির কর্মক্ষেত্র। মেক্সিকোতে থাকাকালীন বিভিন্ন র্যাডিক্যাল গোষ্ঠীকে নিয়ে গঠিত মেক্সিকোর সোশালিস্ট পার্টির মধ্যে তিনি কাজ শুরু করলেন ও অচিরেই এর প্রধান নেতায় রূপান্তরিত হলেন। এই সময় রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সংগঠত হয়েছিল লেনিনের নেতৃত্বে। মার্কিন সরকার কমিউনিস্ট বিরোধী হলেও রাশিয়াতে ব্যবসা করার জন্য যোগাযোগ করে মন্ত্রী পরিষদের সঙ্গে। মন্ত্রী পরিষদের প্রধান লেনিন তাঁর বিশ্বস্ত কমরেড বরোদিনকে অনেক টাকা পয়সা সহ মার্কিন দেশে আলাপ আলোচনার জন্য পাঠান। বরদিন এসেছিলেন গোপনে তাই তিনি সন্দেহভাজন হয়ে ওঠেন। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য তিনি টাকা পয়সার ব্যাগটা একজন অচেনা মানুষকে দিয়ে দেন ও তিনি ব্যাগটা নিয়ে পালিয়ে যান। বিদেশে কপর্দকশূন্য বরোদিন আমেরিকার মিশন অসম্পূর্ণ রেখে চলে আসেন পাশের দেশ মেক্সিকোতে কারণ সেখানে তখন কারাঞ্জার নেতৃত্বে সমাজবাদী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বরদিন মেক্সিকোতে এসে সোশালিস্ট পার্টির একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি বরোদিনকে নিয়ে আসেন তাঁদের নেতা এম এন রায়ের কাছে। এম এন রায় ও বরোদিনের সাক্ষাৎ ইতিহাসের এক নতুন মুহূর্তের জন্ম দেয়, যা শুধু এম এন রায়ের ব্যক্তিজীবন নয়, ভারতের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ ও কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের কার্যকলাপেও পরবর্তীকালে গভীর প্রভাব বিস্তার করে।
বরোদিনকে এম এন রায় শুধু টাকা পয়সা আতিথ্য দিয়ে সাহায্যই করলেন না, দুজনে হয়ে উঠলেন পরম বন্ধু। বরোদিন খুব কাছ থেকে দেখলেন একজন ভারতীয় অল্পবয়সী যুবক কীভাবে স্প্যানিশ ভাষায় অসাধারণ দক্ষতা অর্জন করেছেন এবং সেই ভাষাতেই সেখানকার শ্রমিকদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচারকার্য চালাচ্ছেন, হাজার হাজার শ্রমিককে উদ্বুদ্ধ করছেন। কারাঞ্জার সমাজবাদী সরকার এবং সেই সরকারের প্রধান কারাঞ্জার ওপর এম এন রায়ের ব্যক্তিগত প্রভাব কত বেশি তা দেখেও বরোদিন আশ্চর্য হলেন। কীভাবে সেই সরকারের জন্য শ্রমিক বান্ধব নীতিমালার খসড়া তৈরি করে দিচ্ছেন রায়, তাও বরোদিন দেখলেন। মেক্সিকোর সোশালিস্ট পার্টি মূলত রায়ের ইচ্ছে ও তাত্ত্বিক যুক্তির জোরেই রূপান্তরিত হল রাশিয়ার বাইরে মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টিতে। রাশিয়ার পরে এটাই ছিল সারা বিশ্বের দ্বিতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। এম এন রায়ের কার্যকলাপে মুগ্ধ বরোদিন লেনিনকে চিঠি লিখে এইসব প্রসঙ্গ সবিস্তারে জানান। লেনিনও এম এন রায় সম্পর্কে বিশেষ আগ্রহ অনুভব করেন। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় অধিবেশনের আগে লেনিন চিঠি লিখে এম এন রায়কে সেই অধিবেশনে যোগ দেবার আমন্ত্রণ জানান। নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনার জন্য এম এন রায় যেন বেশ কিছুটা আগেই রাশিয়া পৌঁছন, লেনিন সেই ইচ্ছাও প্রকাশ করেন। মানবেন্দ্রনাথ রায় লেনিনের আমন্ত্রণে সোৎসাহে সাড়া দেন ও জার্মানীতে কিছুদিন কাটিয়ে রাশিয়া পৌঁছন। শুরু হয় তাঁর জীবনের নতুন অধ্যায় যা ভারতে কমিউনিজমের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্কিত।
২
সোভিয়েত রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে প্রায় এক দশক এম এন রায় ঘনিষ্টভাবে কাজ করেন। কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে তিনি মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে যোগ দিতে এসেছিলেন। সেই অধিবেশন থেকেই তিনি কমিন্টার্নের নেতা হিসেবে নির্বাচিত হন ও পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে কমিন্টার্নের প্রতিনিধিই হিসেবে কাজ করেন। ভারতের কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রচার, জাতীয় কংগ্রেসের র্যাডিক্যাল অংশকে সমাজতন্ত্র ও পূর্ণ স্বাধীনতার মতাদর্শে প্রভাবিত করার চেষ্টা ছিল এই সময়ে তাঁর প্রধান কর্মকাণ্ড। এছাড়াও সেন্ট্রাল এশিয়ার সোভিয়েত নেতৃত্বাধীন বিভিন্ন দেশে তিনি কাজ করেন। জার্মানীতে এবং চিনেও কমিন্টার্নের পক্ষ থেকে তিনি আন্দোলন সংগঠন মতাদর্শ বিকাশের দায়িত্বভার নিয়ে গিয়েছিলেন। এই সমস্ত কাজ করার সময় তিনি অনেক পড়াশুনো করেন, ভাষা শেখেন, তাত্ত্বিক কাঠামো তৈরি করে তাকে প্রয়োগে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। সেন্ট্রাল এশিয়ার দেশগুলি সহ অনেক জায়গাতে সেগুলো যথেষ্ট সাফল্য পায়, আবার তাঁর ও বরোদিনের নেতৃত্বাধীন কমিন্টার্নের টিম চিনে প্রবল বিপর্যয়ের মুখোমুখি পড়ে। তাঁরা প্রবল সমালোচিত হন ও রাতের অন্ধকারে চিন থেকে একপ্রকার গোপনে পালিয়ে আসতে বাধ্য হন। চিনের বিপর্যয় কমিন্টার্নের নেতার পদ থেকে এম এন রায়ের অপসারণের কারণ হয় এবং তিনি ক্রমশ সর্বোচ্চ ক্ষমতাধর হয়ে ওঠা সোভিয়েত নেতা স্তালিনের সঙ্গে বিবাদে জড়িয়ে পড়েন। শেষমেষ তাঁকে খানিকটা গোপনে রাশিয়াও ছাড়তে হয়, ফিরে আসতে হয় ভারতে। ভারতে ফিরে তিনি আর কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে পারেন নি। খানিকটা বাধ্য হয়েই তিনি ভারতের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। ১৯৩০ এর দশক জুড়ে কংগ্রেসের মধ্যে কাজ করার পর শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদ ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রামকে দেখার প্রশ্নে কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে তাঁর বিরোধ দেখা যায়। তিনি কংগ্রেস থেকে সরে আসেন ও র্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের মতাদর্শকে সামনে রেখে নিজের রাজনৈতিক দল ও লেখালিখির কাজ চালিয়ে যান মূলত শৈলশহর দেরাদুনকে কেন্দ্র করে। ১৯৫৬ সালে অসুস্থ অবস্থায় দেরাদুনেই তাঁর মৃত্যু হয়। এম এন রায়ের কমিউনিস্ট পর্ব, জাতীয় কংগ্রেস পর্ব ও র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট পর্বের মতাদর্শকে আলাদা আলাদাভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা দরকার, তবে বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর কমিউনিস্ট পর্বটিই আমাদের মূল আলোচ্য।
কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে যোগ দেবার জন্য লেনিনের আহ্বানে এম এন রায় কংগ্রেসের বেশ কিছুটা আগেই রাশিয়াতে চলে এসেছিলেন। এখানে আসার পর লেনিন তাঁকে নিজের লেখা কলোনিয়াল থিসিসটি পড়তে দেন ও তাঁর মতামত চান। কমিউনিস্টরা ঔপনিবেশিক দেশগুলির মুক্তিসংগ্রাম বিষয়ে তখন রাজনৈতিক লাইন তৈরি করার চেষ্টা করছিলেন। সেই উপলক্ষ্যেই লেনিন এই থিসিসটি লিখেছিলেন। এম এন রায় লেনিনের থিসিসটি পড়ার পর সে বিষয়ে কিছু মতপার্থক্যের কথা খোলাখুলি জানান। লেনিন সর্বোচ্চ নেতা হলেও বিতর্ক ও ভিন্নমতকে প্রশ্রয় দিতেন। তিনি এম এন রায়কে একটি পৃথক কলোনিয়াল থিসিস লেখার দায়িত্ব দেন। এম এন রায় সেটি লিখে লেনিনকে দেন। লেনিন আবার রায়ের থিসিসের অনেক দিক মানতে পারেন নি। তবে তিনি এই বিতর্ককে আড়াল না করে দুটি দলিলকেই কমিন্টার্নের অধিবেশনে নিয়ে আসেন ও এই নিয়ে খোলামেলা বিতর্ক আহ্বান করেন। বিতর্কে দুটি দলিলই খানিক সংশোধনের পর গৃহীত হয়। লেনিনের সঙ্গে তাত্ত্বিক বিতর্কের সাহস ও জোর এম এন রায়কে কমিউনিস্ট নেতা হিসেবে কমিন্টার্নে বিশেষ মর্যাদায় অভিষিক্ত করে। তিনি এর নেতা হিসেবে পরিগণিত হন এবং এর স্মল ব্যুরোতেও নির্বাচিত হন।
লেনিন এবং এম এন রায়ের কলোনিয়াল থিসিসের মূল পার্থক্য কী ছিল? এই পার্থক্য ছিল ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বুর্জোয়া শ্রেণির ভূমিকা নিয়ে। লেনিন মনে করেছিলেন জাতীয় বুর্জোয়াদের সাহায্য সহযোগিতা নিয়েই ঔপনিবেশিক দেশগুলিতে উপনিবেশ বিরোধী সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়া দরকার। অন্যদিকে এম এন রায়ের মত ছিল বুর্জোয়া শ্রেণি শ্রমিক কৃষক আন্দোলনের স্বার্থ বিরোধী শক্তি। শ্রমিক ও কৃষকদের ওপর ভর করেই ঔপনিবেশিক দেশের মুক্তিসংগ্রামকে পরিচালনা করতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে সমস্ত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবী কমিন্টার্নের তৃতীয় অধিবেশনে জার্মানী থেকে রাশিয়ায় গেছিলেন, সেই বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বা ভূপেন্দ্রনাথ দত্তও লেনিনের মতোই জাতীয় বুর্জোয়াদের বাইরে রেখে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব বলে ভাবতে পারেন নি।
এই বিতর্কের ছ বছর পর আরেকটি বড় বিতর্কের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এম এন রায়কে। সেটি প্রথম বিতর্কের মতো কেবল তাত্ত্বিক বিতর্ক ছিল না, ছিল রণনীতি ও রণকৌশলগত প্রশ্ন এবং এই বিতর্ককে কেন্দ্র করে চিনে এম এন রায়ের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট ইন্টার্ন্যাশানালকে বিরাট বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে হয়েছিল। সেই সময় চিনে কমিউনিস্ট ইন্টার্ন্যাশালের পক্ষ থেকে এম এন রায় ও বরোদিনের নেতৃত্বাধীন একটি দলকে পাঠানো হয়েছিল। চিনের কমিউনিস্টরা তখন জমি দখলের বৈপ্লবিক লাইন নিয়ে এগোবেন কীনা তাই নিয়ে বিতর্ক ছিল। ডেলিগেশন রওনা হবার আগে রাশিয়ায় কমিন্টার্ন নেতৃত্বের সভায় এম এন রায় দৃঢ় মত রাখেন কৃষিবিপ্লবের ওপর ভিত্তি করে চিন বিপ্লব সমাধা করার ওপর। কুয়োমিনটাং তখন ছিল বড় জমিদার, সমর নায়ক আর পুঁজিপতিদের দখলে। রায় বলেন বড় জোত দখল করে জমির পুনর্বন্টনের প্রোগ্রাম নিতে হবে কমিউনিস্ট পার্টিকে। গরীব কৃষকের হাতে জমি গেলে তাঁদের আস্থা অর্জন করতে পারবে কমিউনিস্টরা, পার্টি ও আন্দোলন ক্রমশ শক্তিশালী হবে, বিপ্লবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হবে। স্তালিন সহ অনেকের এই নিয়ে সংশয় ছিল। কারণ তাঁরা মনে করেছিলেন চিনে কমিউনিস্টরা তখনো দুর্বল। সমর নায়কেরা বেশীরভাগই বড় বড় জোতের মালিক। র্যাডিক্যাল ভূমি সংস্কার শুরু করলেই তাঁরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চলে যাবেন। আর সমর নায়কেরা কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চলে গেলে সেই আক্রমণ কমিউনিস্টরা মোকাবিলা করতে পারবেন না। তবে রায়ের থিসিস ধরে সাবধানে চিনা কমিউনিস্ট পার্টি এগোবে এবং নিয়ন্ত্রিতভাবে কাজ করবে, এরকম বোঝাপড়া নিয়েই রায় ও বরোদিনের নেতৃত্বাধীন কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের ডেলিগেশনটি রাশিয়া থেকে চিনে আসে। রুশ ডেলিগেশনের তরফে র্যাডিক্যাল ভূমিসংস্কার কর্মসূচী পেশ করার পর দেখা যায় চিনের কমিউনিস্টদেরও র্যাডিক্যাল ভূমিসংস্কার নীতি নিয়ে এগনোতে যথেষ্ট আপত্তি আছে। চিনা কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন নেতা চিউ চিউ পি, চেন তু সি প্রমুখরা কমিন্টার্ন ডেলিগেশনের নীতি প্রয়োগের বিরুদ্ধেই মত প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু এম এন রায়ের নেতৃত্বাধীন কমিন্টার্ন ডেলিগেশন র্যাডিক্যাল জমি দখল ও পুনর্বন্টনের কর্মসূচী নিয়ে এগনোর ওপরেই জোর দেয়। এর ফল হয় মারাত্মক। কুয়োমিনটাং ও তার সমর নায়কেরা কমিউনিস্টদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। শয়ে শয়ে কমিউনিস্টকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়। এম এন রায়, বরোদিন সহ কমিন্টার্নের নেতাদের রাতের অন্ধকারে গোপনে চিন থেকে পালিয়ে আসতে হয়। কমিন্টার্নের বৈঠকে বরোদিন জানান তিনিও এই র্যাডিক্যাল পথে এগনোর পক্ষপাতী ছিলেন না, কিন্তু রায় একে সমর্থন করেছিলেন। সেই সময় রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে এমনিতেই চলছিল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। লেনিনের মৃত্যুর পর সাধারণ সম্পাদক স্তালিন কোনও বিরুদ্ধ মতকে আমল দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। ট্রটস্কি, কামেনেভ, জিনোভিয়েভকে সে সময় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে ভিন্ন মত ও স্তালিনের নেতৃত্বের সমালোচনার কারণে তাড়িয়ে দেওয়া হয়। চিনে কমিন্টার্নের নীতি নিয়ে স্তালিনের সঙ্গে এম এন রায়ের আগেই বিরোধ হয়েছিল। সেই সময় স্তালিনের সঙ্গে জোট ছিল বুখারিনের, যে বুখারিন রাশিয়ার ভেতরে নেপ ও ধনী কৃষক এমনকী কুলাকদেরও খানিকটা ছাড় দেবার পক্ষপাতী ছিলেন। বুখারিন, স্তালিন এম এন রায়ের র্যাডিক্যাল ভূমিসংস্কার কর্মসূচী মানতে পারেন নি। জিনোভিয়েভের অপসারণের পর বুখারিন তখন কমিন্টার্নের প্রধান আর রুশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব স্তালিনের হাতে। স্তালিন বুখারিন জোট চিনের বিপর্যয়ের যাবতীয় দায় এম এন রায়ের ওপর চাপিয়ে দিয়ে তাঁকে বহিষ্কার করেন। সেই সময়ে রাশিয়ায় বিরোধী মতাবলম্বীদের যেভাবে গ্রেপ্তার ও নিকেশ করা হচ্ছিল, তাথেকে শঙ্কিত হয়ে অসুস্থ এম এন রায় একটি অ্যাম্বুলেন্সে চেপে গোপনে রাশিয়া ত্যাগ করেন ও জার্মানীতে চলে আসেন। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গেই থাকা দুই ভারতীয় বিপ্লবী অবনী মুখার্জী ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় পরবর্তীকালে গ্রেট পার্জের সময় বন্দী ও খুন হয়ে গিয়েছিলেন রাশিয়ার মাটিতে। সেই কথা মাথায় রাখলে মনে হয় সেসময় গোপনে রাশিয়া না ছাড়লে এম এন রায়েরও পরবর্তীকালে মর্মান্তিক পরিণতি হওয়া অসম্ভব ছিল না। চিনের ঘটনাবলী ও সেই বিতর্কের সামগ্রিক মূল্যায়ন আমাদের বর্তমান পর্যালোচনার বাইরের ব্যাপার। তবে এম এন রায় কেন ঐ পথে এগিয়েছিলেন তাঁর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ তিনি করার চেষ্টা করেছেন ‘মাই এক্সপিরিয়েন্স ইন চায়না’ বইতে। কমিন্টার্ন এর সমস্যাবলী নিয়ে রায়ের ভাবনাচিন্তার কথা পাওয়া যাবে তাঁর ক্রাইসিস ইন কমিন্টার্ন বইতে। লেনিনের মৃত্যুর পর স্তালিনের একনায়কত্ব ও ভিন্ন মতের নেতাদের সরিয়ে দেওয়ার যে অধ্যায়টি নিয়ে বহুবিতর্ক হয়, সেই অধ্যায়টিকে এম এন রায় কেমনভাবে দেখেছিলেন তা জানা যায় তাঁর ‘রেভেলিউশন অ্যান্ড কাউন্টার রেভেলিউশন ইন চায়না’ বইটি থেকে।
৩
এম এন রায়ের জীবন ও কাজের যে দিকটি আমাদের দিক থেকে সবচেয়ে জরুরী তা হল ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা ও বিকাশে তাঁর নিরন্তর চেষ্টা। কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পর ১৯২০ সালের অগস্টে রায় কমিন্টার্ন এর তরফে নির্দিষ্ট দায়িত্ব পেয়ে চলে যান সেন্ট্রাল এশিয়াতে এবং সেখানকার দেশগুলিতে কাজ করতে থাকেন। মুসলিমধর্মের মানুষেরা ঐ দেশগুলিতে ছিলেন সংখ্যাগুরু। কমিউনিস্টদের ভূমিসংস্কার কর্মসূচীতে আতঙ্কিত হয়ে কুলাকেরা মুসলিমদের মিথ্যা কথা বলে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে উস্কে দেবার চেষ্টা করে। রায় ধৈর্যের সঙ্গে বিষয়টির মোকাবিলা করেন ও সেখানকার মানুষজনকে সোভিয়েত কমিউনিজমের পক্ষে টেনে নেন। প্রাচ্যের মানুষের মধ্যে মার্কসবাদের বিশ্ববীক্ষাকে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি মার্ক্সীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তিনি লেনিনকে একটি চিঠি লেখেন। চিঠিটি রুশ নেতৃত্বের সভায় পড়া হলে সবাই এতে সানন্দ সম্মতি দেন। মস্কোতে খোলা হয় কমিউনিস্ট ইউনিভার্সিটি ফর দ্য টয়েলার্স অব দি ইস্ট।
১৯২০ সালে সেন্ট্রাল এশিয়ার তাসখন্দের মাটিতে এম এন রায় সহ সাতজন আলাপ আলোচনা করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি নামে এক নতুন সংগঠন তৈরি করেন। উপস্থিত সাতজন ছিলেন - এম এন রায়, অবনী মুখার্জী, তিরুমল আচার্য, রোজা ইটিংগফ, এভেলিন রায়, মহম্মদ আলী, মহম্মদ শফীক। পরবর্তী সময়ে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশানালের তরফে মূলত এম এন রায় ভারতের মাটিতে একটি কার্যকরী কমিউনিস্ট সংগঠন তৈরির চেষ্টা চালিয়ে যান। এম এন রায় সম্পাদিত ‘ভ্যানগার্ড’ পত্রিকাটি এই কাজে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও কমিউনিস্টদের ভূমিকা এই পরিস্থিতিতে কী হতে পারে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সহ এম এন রায় এইসময়ে ‘ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন’ নামে একটি বই লেখেন। এই বইতে রায় বলেন কংগ্রেসের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বুর্জোয়া শ্রেণির স্বার্থে কাজ করছে এবং তা প্রকৃত শ্রমিক-কৃষক বিপ্লবের পথে বাধাস্বরূপ। তিনি গান্ধীর অহিংস আন্দোলনের বিপরীতে একটি সশস্ত্র মার্কসবাদী বিপ্লবের পক্ষে এই বইতে যুক্তি দেন। রায়ের যুক্তি দেশের ভেতর ও বাইরের অনেক বিপ্লবী সে সময়ে মানতে পারেন নি এবং তাঁরা রায়ের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত হন।
প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা সেই সময় নানা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলেন। দ্বিতীয় কমিউনিস্ট ইন্টার্নাশ্যানালের সময় গড়ে তোলা এম এন রায়দের কমিউনিস্ট পার্টিকে ভারতের কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্নদের যথার্থ প্রতিনিধি হিসেবে মেনে নিতে পারেন নি বার্লিন ও জার্মানীর অন্যান্য স্থানে অবস্থিত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীরা। তাঁরা বার্লিন কমিটি হিসেবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় সক্রিয় ছিলেন। এই বার্লিন কমিটির মোট ১৪ জন মস্কোতে এসেছিলেন কমিন্টার্নের তৃতীয় অধিবেশনে যোগ দিতে।
১৯২১ সালে কমিন্টার্নের তৃতীয় অধিবেশনের সময় মস্কোতে উপস্থিত প্রবাসী ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে ছিল নানান ধরনের পরস্পর বিরুদ্ধ চিন্তাভাবনা। প্রধান ত্রয়ী এম এন রায়, বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত আলাদা আলাদা পদ্ধতিতে ভারতে কাজ করার কথা ভেবেছিলেন। ভারতীয় বিপ্লবের পথ ও পদ্ধতি নিয়ে যেমন তাঁদের আলাদা আলাদা মত ও দৃষ্টিকোণ ছিল। এম এন রায় শ্রমিক শ্রেণির নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে ভারতের রাজনীতিকে পরিচালনার কথা বলেছিলেন। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ও বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনকেই মুখ্য ব্যাপার ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ভাবনাচিন্তাকে পরবর্তী স্তরের ব্যাপার বলে মনে করেছিলেন। তবে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যেখানে স্বাধীনতা অর্জনের প্রশ্নটিতেই সর্বাত্মক গুরুত্ব দিয়েছিলেন সেখানে ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত এই কাজের পাশাপাশি শ্রমিক ও কৃষকদের বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তাঁদের মধ্যে আলাদা করে সংগঠন তৈরি ও মতাদর্শ প্রচারের কথা ভেবেছিলেন। কমিন্টার্নের নেতাদের কাছে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জমা দেওয়া থিসিসটি সঙ্গত কারণেই একটি ন্যাশানালিস্ট থিসিস হিসেবে পরিগণিত হয়েছিল। রায়, চট্টোপাধ্যায়, দত্ত এই ত্রয়ী ছাড়াও অবনী মুখার্জী, নলিনী গুপ্ত প্রমুখরা পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে এইসময়ে নানা বিষোদগার চালিয়ে যান। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণগত ভিন্নতা ছাড়াও টাকাপয়সা, সাংগঠনিক কর্তৃত্ব ইত্যাদি প্রশ্নে অসংখ্য ছোট বড় সমস্যা এঁদের ঐক্যকে বিনষ্ট করে এবং এই ঐক্যের অভাবে প্রবাসীদের কমিউনিস্ট উদ্যোগ সাংগঠনিকভাবে এক জায়গায় আসতে পারে নি। এম এন রায় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের নেতা হিসেবে মস্কোকে কেন্দ্র করে কাজ করতে থাকেন। বীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ফিরে আসেন বার্লিনে ও হিটলারের উত্থানের আগে পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন, যুক্ত হয়েছিলেন জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে। ভূপেন্দ্রনাথ মস্কোতে থেকে কাজ করার প্রস্তাব পেয়েছিলেন, কিন্তু রাজি হন নি। মস্কো থেকে তিনি আবার জার্মানীতে ফেরেন, গবেষণার কাজ শেষ করেন ও পি এইচ ডি ডিগ্রি নিয়ে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।
রুশ বিপ্লবের পর বিশ শতকের বিশের দশকে ভারতের কয়েকটি প্রান্তে কয়েকজন সংগঠক নেতাকে ধরে কয়েকটি কমিউনিস্ট কেন্দ্র গড়ে ওঠে। ১৯২০ সালে মানবেন্দ্রনাথ রায় সহ কয়েকজনের উদ্যোগে তাসখন্দের মাটিতে যে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তা এই সমস্ত উদ্যোগগুলির মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে ভূমিকা নেবার চেষ্টা করত। এম এন রায়ই মুখ্য ভূমিকায় ছিলেন। কমিউনিস্ট মতাদর্শ ছড়ানোর কাজে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল মানবেন্দ্রনাথ রায় সম্পাদিত ও বিদেশ থেকে প্রকাশিত ‘দ্য ভ্যানগার্ড অব ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স’। পরে এটি ‘অ্যাডভান্স গার্ড’ নামেও প্রকাশিত হত। দেশের মাটিতেও প্রতিটি কেন্দ্র থেকেই এক বা একাধিক পত্রিকা বেরোত এবং সেগুলিও কমিউনিস্ট মতাদর্শকে ছড়িয়ে দেবার কাজ করত। মুম্বাই কেন্দ্রটির নেতৃত্বে ছিলেন শ্রীপত অমৃত ডাঙ্গে এবং তাঁর সহযোগী ছিলেন এস ভি ঘাটে, কে এন যোগলেকর, আর এস নিম্বকর, টি ভি পারভাতে। মুম্বাই থেকে তাঁদের উদ্যোগে বেরোত ‘দ্য সোশালিস্ট’ নামের পত্রিকাটি। কলকাতা কেন্দ্রটির নেতৃত্বে ছিলেন মুজফফর আহমেদ। তাঁর সহযোগীদের মধ্যে ছিলেন আব্দুল হালিম, আব্দুর রেজ্জাক খাঁ প্রমুখরা। কলকাতা থেকে বেরোনো ‘লাঙল’, ‘আত্মশক্তি’, ‘ধূমকেতু’, ‘দেশের বাণী’, ‘অমৃতবাজার’ ইত্যাদি পত্রিকা ছিল সমাজতান্ত্রিক চিন্তাভাবনা দ্বারা প্রভাবিত। লাহোর কেন্দ্রটির নেতৃত্বে ছিলেন গোলাম হোসেন। সেখান থেকে বেরোত ‘ইনকিলাব’ পত্রিকা। এর সম্পাদনা করতেন গোলাম হোসেন ও সামসউদ্দিন। একে ঘিরে সেখানে গড়ে ওঠে ইনকিলাবি গোষ্ঠী। চেন্নাই কেন্দ্রটির নেতৃত্বে ছিলেন সিংঘরাভেলু চেট্টিয়ার। তিনিই ভারতে প্রথম মে দিবস পালন করেছিলেন। শ্রমিক আন্দোলন ছাড়াও সামাজিক আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ট সম্পর্ক ছিল এবং পেরিয়ারের সঙ্গে তিনি জাতপাত বিভেদের বিরুদ্ধে কাজ করেছিলেন। চেন্নাই থেকে প্রকাশিত হত ‘নবযুগ’, পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন ভি কৃষ্ণা রাও। সিঙ্গরাভালু চেট্টিয়ারের উদ্যোগে চেন্নাই থেকে আরও একটি পত্রিকা বেরোত। জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্যও সিংঘরাভেলু চেট্টিয়ার কাজ করতেন। উত্তরপ্রদেশে হসরৎ মোহানি, গণেশ শঙ্কর বিদ্যার্থী প্রমুখরাও জাতীয়তাবাদ ও কমিউনিস্ট আন্দোলনের যুগ্ম প্রভাবের মধ্যে থেকে কাজ করছিলেন। বিভিন্ন প্রান্তের এই গোষ্ঠীগুলি নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপণ করে একটি একক সংগঠন গড়ে তোলার প্রয়াস চালাচ্ছিল। ১৯২৫ সালে কানপুরে এক সম্মেলনে তাঁরা মিলিত হন এবং গড়ে তোলেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি। এম এন রায় প্রথম থেকেই এই সংগঠনের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সেইসময় কমিউনিস্টদের মধ্যে খোলা কাজের প্রতিবন্ধকতা থাকায় তাঁরা অনেকে জাতীয় কংগ্রেস বা অন্যান্য দলের মধ্যে থেকে কাজ করতেন। কোলকাতায় তৈরি হয়েছিল ওয়ার্কাস অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি। এম এন রায় একে নানাভাবে সাহায্য সহযোগিতা করতেন। পরে দেশের অন্যান্য অঞ্চলেও এর শাখা খোলা হয় একে এক সর্বভারতীয় চরিত্র দেওয়া হয়। কিন্তু কমিন্টার্নের ১৯২৮ সালের সম্মেলন এক সংকীর্ণতাবাদী লাইন নিলে ভারতের কমিউনিস্টরা ওয়ার্কাস অ্যান্ড পিজেন্ট পার্টি থেকে বেরিয়ে আসেন। সে সময় এম এন রায় কমিন্টার্ন এবং রাশিয়া থেকে বিতাড়িত হয়েছেন। তিনি কমিন্টার্নের এই নয়া নীতি মানতে পারেন নি।
১৯৩০ সালে রাশিয়া থেকে জার্মানী হয়ে ভারতে ফেরেন এম এন রায়। এক দশক তিনি জাতীয় কংগ্রেসের ভেতরে কাজ করেন। কিন্তু জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর কাজ কখনোই মসৃণ হয় নি। রায় জাতীয় কংগ্রেসকে বুর্জোয়া প্রভাবের বাইরে নিয়ে আসার চেষ্টা করতেন ও কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী অংশের বিরুদ্ধে জহরলাল নেহরুর মতো বামপন্থী কংগ্রেসীদের এই মতের দ্বারা প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও তিনি এই মর্মে আলাপ আলোচনা চালিয়েছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত কংগ্রেসের শ্রেণিচরিত্র এইসব চেষ্টার মধ্যে দিয়ে বদলানো সম্ভব না হওয়ায় রায় হতাশ হন। তিনি নিজের মত সামনে আনার জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচনেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন তবে খুব বেশি সমর্থন পান নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরুর পর, বিশেষ করে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে জার্মান ফ্যাসিস্টদের যুদ্ধ ঘোষণার পর কংগ্রেস যেভাবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড় আন্দোলন শুরু করে তা তিনি মানতে পারেন নি। তিনি মনে করেছিলেন বিশ্বযুদ্ধ ও ফ্যাসিবাদের আগ্রাসনের পরিস্থিতিতে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামটাই মূল ব্যাপার। দেড় দশক আগে কমিউনিস্টদের থেকে তিনি সাংগঠনিকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, তবে এই জটিল সময়ে তাঁর অবস্থান ছিল সি পি আই এর মতোই। তবে এই পর্বে কমিউনিস্ট পার্টির কাছাকাছি রাজনৈতিক অবস্থান নিয়ে তিনি বিচ্ছিন্ন হলেন জাতীয় কংগ্রেস থেকে। অবশ্য কমিউনিস্টদের সঙ্গে তাঁর রাজনৈতিক সাংগঠনিক সম্পর্ক আর পুনঃস্থাপিত হয় নি। তিনি র্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট নামের এক নতুন সংগঠন তৈরি করলেন ও নয়া মানবতাবাদের রাজনৈতিক দর্শন প্রচারকাজে মগ্ন হলেন। দেরাদুন হয়ে দাঁড়াল তাঁর কর্মকাণ্ডের মূল ভরকেন্দ্র। এখানেই স্বাধীনতার এক দশক পরে ১৯৫৬ সালে অসুস্থ অবস্থায় তিনি প্রয়াত হন।
