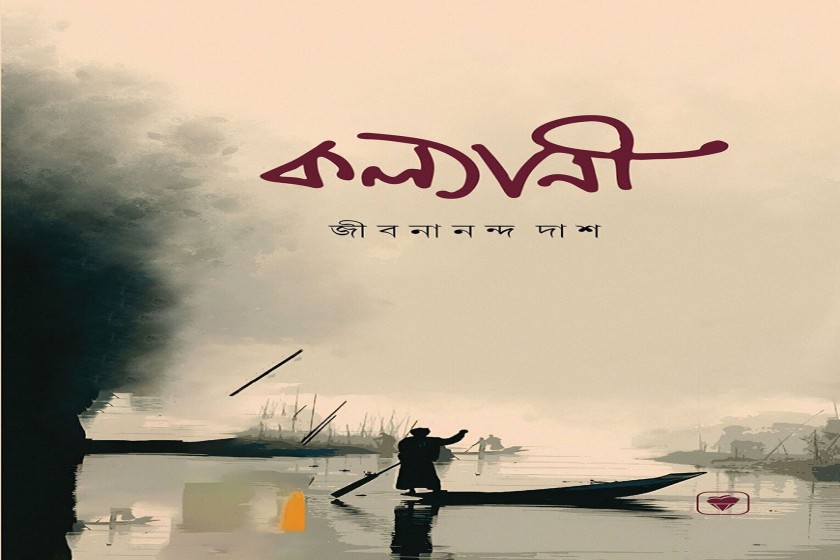
জীবনানন্দের উপন্যাস : আদিপর্বের দুটি আখ্যান 'পূর্ণিমা' ও 'কল্যাণী'
- 07 October, 2025
- লেখক: সৌভিক ঘোষাল
১
বিশ শতকী বিশ্ব উপন্যাসের অন্যতম প্রধান নক্ষত্র চেক ঔপন্যাসিক ফ্রানজ কাফকা যখন বিয়াল্লিশ বছর বয়সে মারা গেলেন, তখনো পাঠককুলের জানা ছিল না তিনি ট্রায়াল, ক্যাসেল ও আমেরিকা নামের তিনটি উপন্যাস লিখে গিয়েছেন। কাফকার মৃত্যুর পর তাঁর বন্ধু ম্যাক্স ব্রড এগুলি প্রকাশ করলে বিশ্বসাহিত্যে বিপুল আলোড়ন ওঠে। লেখালিখির জগতে কাফকার এইসব উপন্যাস ও মেটামরফোসিস এর মতো গল্পের প্রভাবে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। বিস্ময়ের কথা এই যে কাফকা নিজে চান নি, তাঁর এই উপন্যাসগুলি প্রকাশের আলো দেখুক। বন্ধু ব্রডকে তিনি নির্দেশ দিয়েছিলেন তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেবার। ভাগ্যিস সেই কাজটি যক্ষা আক্রান্ত, স্যানাটোরিয়ামের বিচ্ছিন্নতায় বিষণ্ণ রোগাক্রান্ত হতাশ কাফকা নিজে করেন নি আর ব্রডও তাঁর প্রাণের বন্ধুর নির্দেশিকা অগ্রাহ্য করে লেখাগুলি প্রকাশ করেছিলেন।
কাফকার অপ্রকাশিত উপন্যাস প্রকাশের মতোই বাঙালি পাঠককে বিস্মিত ও আলোড়িত করেছিল জীবনানন্দের একের পর এক উপন্যাসের আশ্চর্য আত্মপ্রকাশ। ১৯৫৪ সালে পঞ্চান্ন বছর বয়সে কবি জীবনানন্দের আকস্মিক ও দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুর সময়কালে তাঁর ঔপন্যাসিক পরিচয়টি বাঙালি পাঠকদের জানা ছিল না। এই পরিচয়ের জন্য আমাদের অপেক্ষা করতে হয়েছে আরো অনেকদিন। কবির মৃত্যুর প্রায় বিশ বছর পর কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশের উদ্যোগে ১৯৭৩ এ প্রকাশিত হয় ‘মাল্যবান’ উপন্যাসটি। এর মধ্যে দিয়েই কবি জীবনানন্দ প্রথমবারের জন্য উপন্যাসকারের পরিচয়ে পাঠকের সামনে এলেন ও চমকিত করলেন। ‘মাল্যবান’ প্রকাশের কিছুদিন পর ‘সুতীর্থ’ উপন্যাসটি ‘দেশ’ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে বেরোয় ১৯৭৫-৭৬এ। ‘প্রতিক্ষণ’ প্রকাশনা সংস্থা থেকে গত শতকের আটের দশকে জীবনানন্দ সমগ্রতে প্রথম থেকে অষ্টম খণ্ডে ধারাবাহিকভাবে বেরিয়েছিল পূর্ব প্রকাশিত ‘মাল্যবান’ সহ বেশ কয়েকটি উপন্যাস। প্রতিক্ষণ প্রকাশিত উপন্যাসগুলির মধ্যে আছে – ‘জলপাইহাটি’, ‘মাল্যবান’, ‘কারুবাসনা’, ‘জীবনপ্রণালী’, ‘বাসমতীর উপাখ্যান’, ‘প্রেতিনীর রূপকথা’, ‘বিভা’। প্রতিক্ষণ প্রকাশিত জীবনানন্দ সমগ্রের শেষ চারটি খণ্ড – নয় থেকে বারোতে কোনও উপন্যাস ছিল না। তবে এর পরে আরো কয়েকটি উপন্যাস পাণ্ডুলিপির খাতা থেকে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়েছে গবেষকদের অসীম পরিশ্রমে। এগুলির মধ্যে আছে – নিরুপম যাত্রা, মৃণাল, কল্যাণী, পূর্ণিমা। আর আছে ‘বিরাজ’ নামের এক উপন্যাস প্রচেষ্টার শুরুর কয়েকটি পাতা। আজ জীবনানন্দের যে উপন্যাস জগৎ আমাদের সামনে আছে, সেখানে রয়েছে মোট বারোটি উপন্যাস ও একটি অসমাপ্ত খসড়া। রচনাকাল অনুযায়ী তার ক্রমতালিকাটি এরকম - পূর্ণিমা (১৯৩১ নভেম্বর), কল্যাণী (১৯৩২ জুলাই), মৃণাল (১৯৩৩ ফেব্রুয়ারি), বিভা (১৯৩৩ ফেব্রুয়ারি), নিরুপম যাত্রা (১৯৩৩ মার্চ), জীবনপ্রণালী (১৯৩৩ মার্চ), কারুবাসনা (১৯৩৩ অগস্ট), প্রেতিনীর রূপকথা (১৯৩৩ অগস্ট সেপ্টেম্বর), বিরাজ (১৯৩৩ এর দ্বিতীয়ার্ধ - অসম্পূর্ণ রচনা), জলপাইহাটি (১৯৪৮ এপ্রিল - মে), সুতীর্থ (১৯৪৮ মে - জুন), মাল্যবান (১৯৪৮ জুন), বাসমতীর উপাখ্যান (১৯৪৮ এর দ্বিতীয়ার্ধ)।
রচনাকালের দিকে তাকালে বোঝা যায় ১৯৩১ ও ১৯৩২ এর সূচনাপর্বের দুটি উপন্যাসের পর ১৯৩৩ এ জীবনানন্দ ঝড়ের গতিতে লিখে গেলেন একের পর এক মোট ছটি উপন্যাস। এরপর দীর্ঘ পনেরো বছর আর উপন্যাস লিখলেন না তিনি। আবার সদ্য স্বাধীন দেশভাগ জর্জরিত ভারতে লিখতে শুরু করলেন উপন্যাস আর এক বছরের মধ্যেই লিখে ফেললেন বড়সড় চারটি আখ্যান। এরপর আরো ছ বছর বেঁচে ছিলেন তিনি। কবিতায় সৃষ্টিশীল থাকলেও উপন্যাসের দিকে আর এগোন নি।
উপন্যাসকার জীবনানন্দের পাশাপাশি গল্পকার জীবনানন্দের কথা উল্লেখ না করলে অবশ্য তাঁর কথাকার পরিচয়ের পূর্ণ স্বরূপটি উদঘাটিত হয় না। সে এক স্বতন্ত্র পর্যালোচনার বিষয়।
জীবনানন্দের উপন্যাস নিয়ে বাংলায় প্রথম বইটি লেখেন অধ্যাপক পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়। বইটির নাম ছিল ‘জীবনানন্দ : উপন্যাসের ভিন্ন স্বর’। জীবনানন্দের জন্ম শতবর্ষে ১৯৯৯ সালে এই নাতিদীর্ঘ বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। জীবনানন্দের জন্ম শতবর্ষে তাঁকে নিয়ে সাহিত্য অকাদেমির আলোচনা সভায় পঠিত প্রবন্ধের যে সংকলন শঙ্খ ঘোষের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়, সেখানেও কথাকার জীবনানন্দের উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখতে পাই। বাংলা উপন্যাসের যে সব ইতিহাস লেখা হয়েছে, তার প্রথম দিককার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলিতে – যেমন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা’ বা সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘বাংলা উপন্যাসের কালান্তর’ তখনো অবধি অপ্রকাশিত কথাকার জীবনানন্দ আলোচনায় না এলেও পরের দিকের বইগুলিতে – যেমন সত্যেন্দ্রনাথ রায়ের ‘বাংলা উপন্যাস ও তার আধুনিকতা’ জীবনানন্দ গুরুত্ব সহকারে আলোচিত হয়েছেন। জীবনানন্দকে নিয়ে পত্রপত্রিকার পাতায় অজস্র আলোচনা হয়েছে, বিশেষ করে বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনে। সেখানে কবি জীবনানন্দের পাশাপাশি আলোচিত হয়েছেন আখ্যানকার জীবনানন্দও। দুই শতাব্দীর সন্ধিক্ষণে পরিকথা পত্রিকার বিশ শতকের বাংলা উপন্যাস সংক্রান্ত বিশেষ সংখ্যাটির কথা আমরা এই প্রসঙ্গে ভাবতে পারি। সেখানে জীবনানন্দের উপন্যাস ‘সুতীর্থ’ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত। সব মিলিয়ে আমরা বলতেই পারি, জীবৎকালে কবি জীবনানন্দের কথাকার সত্তাটি যতই মেঘে ঢাকা থাকুক, আজ আর তা নেই।
২
জীবনানন্দের একটি উপন্যাস প্রচেষ্টা অসমাপ্ত থেকে গেছে। ১৯৩৩ এর দ্বিতীয়ার্ধে, সম্ভবত অগস্টে ‘বিরাজ’ নামের উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেছিলেন জীবনানন্দ। তবে তিন পাতার পর এটি আর এগোয় নি। সেখানে মহাত্মা গান্ধীর কারাবাসের কথা এসেছে চরিত্রপাত্রদের সংলাপ বিনিময়ে। এসেছে হিটলার ও নাজিদের নিয়ে রঙ্গব্যঙ্গ। “ভবিষ্যতে গৃহস্থালির কাজে কয়লার ব্যবহার অনেক বৃদ্ধি পাইবে, এই সময় কয়লা ব্যবসায়ীগণ যদি এমন পোড়া কয়লা বাহির করিতে পারেন, যাহাতে ধুঁয়া হইবে না। … যাহাতে ভস্মের পরিমাণ কম হইবে, যাহার আকার সুবিধাজনক হইবে। … ওপরে স্বস্তিকা থাকবে। - আচ্ছা স্বস্তিকা নর্ডিক? – আমি তো জানি বৈদিক।” হিটলার ও তার নাজি পার্টি তখন সদ্য জার্মানীর ক্ষমতা দখল করেছে, তাদের প্রচারাভিযান ও কার্যকলাপ বিপুল তরঙ্গ তুলেছে সারা বিশ্বে। আর্য নর্ডিক জাতির মহিমা কীর্তনে তারা জগৎ কাঁপাচ্ছে। এদেশেও নর্ডিক বৈদিক সম্পর্করেখা তৈরি করে সমীকরণ কষা হচ্ছে। এসব নিয়ে মৃদু বিদ্রুপই জীবনানন্দের উপন্যাসে দেখা যায়। তবে তিন পাতার অতি ক্ষুদ্র সূচনা অংশটি থেকে উপন্যাসকে কোনদিকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ তার কোনও আঁচ আমরা পাই না। কেন উপন্যাসটিকে প্রবল রাজনৈতিক বাতাবরণের মধ্যে রেখে শুরু করেও তিনি এটি নিয়ে আর এগোলেন না, তার কোনও উত্তর সংকেতও আমাদের কাছে নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জীবনানন্দের এরকম আর কোনও উপন্যাস খসড়ার হদিশ, যা তিনি লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু শেষ করেন নি, আমাদের কাছে নেই।
৩
দাম্পত্যের শীতলতা ও আর্থিক সঙ্কট মধ্যবিত্ত মধ্যবয়সী পুরুষকে জর্জরিত করে দিচ্ছে, এমন একটা থিম নিয়ে জীবনানন্দের বিখ্যাত উপন্যাস ‘মাল্যবান’ লেখা হয়েছিল। এই ধরনের থিম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা রয়েছে জীবনানন্দের প্রথম উপন্যাস ‘পূর্ণিমা’তে। ‘পূর্ণিমা’ মাল্যবানের তুলনায় আকারে অনেক ছোট, অপরিণত এবং শিল্পগুণেও ততটা উল্লেখযোগ্য কিছু নয়।
কিন্তু সন্তোষ চরিত্রটির জীবন ও ভাবনার মধ্যে জীবনানন্দের অন্যতম বিখ্যাত উপন্যাস ‘মাল্যবান’এর অতৃপ্তি ও আক্ষেপের বীজটি নিহিত বলে সেটি গুরুত্বপূর্ণ। ‘পূর্ণিমা’ উপন্যাসে আমরা দেখি উপন্যাসের নায়ক সন্তোষের সংসার আর্থিক সঙ্কটে দীর্ণ। সে নিজে তাই নিয়ে বিব্রত আর তা আরো বাড়ে যখন স্ত্রী পূর্ণিমা এই নিয়ে তাকে নানারকম খোঁটা দেয়। পূর্ণিমার অবিবাহিত দিদি চামেলি, ছোট বোন টুক্কু আর একলা হয়ে পড়া বয়স্ক মামাকে দেখার কেউ নেই। বিশেষ করে চামেলি স্বাধীনতা আন্দোলনে জড়িয়ে চাকরী খোয়ানোর পর পূর্ণিমার বাপের বাড়ির আর্থিক সঙ্কট মারাত্মক চেহারা নিয়েছে। এদের পাশে দাঁড়াতে পারলে সন্তোষও খুশি হত, কিন্তু আর্থিক সঙ্গতি নেই। সে আশা করে অচিরেই একটা ভালো কাজ জুটে যাবে, স্ত্রীকেও সেই আশায় ভরসা করতে বলে, কিন্তু বাস্তবে তা আর হয় না। এমন সময় হঠাৎ জানা যায় বড় শ্যালিকা চামেলির বিবাহ স্থির হয়েছে বোম্বে নিবাসী উচ্চপদে কর্মরত এক প্রবাসী বাঙালি ডাক্তারের সঙ্গে। এই সংবাদ সুখ ও স্বস্তির হতে পারত। কিন্তু দেখা যায় দিদির স্বামীভাগ্য অনেক ভালো হয়ে যাচ্ছে আর সে সুন্দরীতর হয়েও সন্তোষের দরিদ্রতর সংসারে থাকতে বাধ্য – এটা পূর্ণিমাকে ঈর্ষান্বিত করে। সে স্বামীকে ভালো চাকরী খোঁজার জন্য আরো বেশি করে উত্যক্ত করতে থাকে। সন্তোষ যখন কলকাতার মেসে থেকে কোলকাতায় বিবাহের প্রয়োজনীয় কাজ সারতে আসা শ্যালিকা চামেলির সঙ্গে দেখা করতে আসে, তখন সন্তান সম্ভবা পূর্ণিমার চিঠি আসতে থাকে। সে সব চিঠিতে পূর্ণিমা তার শারীরিক নানা সমস্যার কথা জানায় আর স্বামীকে ঘরে ফিরতে বলে। অসুস্থ স্ত্রী পূর্ণিমার পাশে চলে না গিয়ে সন্তোষ বড় শ্যালিকার বিবাহ নিয়ে মেতে থাকে। শুধু তাই নয় গোপনে আশা করতে থাকে সন্তান প্রসবের ধাক্কা স্ত্রী পূর্ণিমা নিতে পারবে না এবং তার মৃত্যু হবে। শেষ পর্যন্ত বাস্তবেও তাই হয়। দাম্পত্য সঙ্কটের তীব্রতায় স্বামী মনে মনে স্ত্রীর মৃত্যু কামনা করছে, এই মারাত্মক ছবি বাংলা উপন্যাসে ব্যতিক্রমী। তিরিশের দশকে রচনাকালের সমসময়ে এই লেখা প্রকাশিত হলে শিল্পগুণে দুর্বল হলেও হয়ত এই থিমের কারণেই তা প্রবল আলোড়ন ফেলত। সম্ভাবনা ছিল আখ্যানকারের ব্যক্তিগত জীবনের ওপর অনুসন্ধানের সার্চলাইট এসে পড়ার, যা এসব উপন্যাস, বিশেষ করে মাল্যবান প্রকাশের পর সত্যিই এসে পড়েছিল।
‘মাল্যবান’ জীবনানন্দের বিখ্যাত উপন্যাসগুলোর অন্যতম। এখানে দাম্পত্য সঙ্কটের ছবিটি আরো গভীর। উৎপলার কাছে প্রেমের বদলে শীতলতা, হিংস্রতা পেয়ে পেয়ে মাল্যবানের জীবন যৌবন কীভাবে বিধ্বস্ত হল, আখ্যান তা বিস্তারে ও গহনে গিয়ে দেখিয়েছে। আমরা জীবনানন্দের দ্বিতীয় পর্বের এই বিখ্যাত উপন্যাসটি নিয়ে অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করব।
৪
ফিরে আসা যাক জীবনানন্দের প্রথম পর্বের উপন্যাসের আলোচনায়। ‘পূর্ণিমা’র পর জীবনানন্দ দ্বিতীয় যে উপন্যাসটি লেখেন সেটি হল ‘কল্যাণী’। এর আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই উল্লেখ করা দরকার জীবনানন্দের উপন্যাসে দাম্পত্য সঙ্কট কিন্তু শুধুই পুরুষের চোখ দিয়ে দেখা হয় নি। নারীর প্রেম ও বিবাহের সঙ্কট তার নিজের মনোজগতে কী ঝড় তুলেছিল, ‘কল্যাণী’ উপন্যাসে তাকে কেন্দ্রে রেখেছিলেন আখ্যানকার জীবনানন্দ।
‘কল্যাণী’ উপন্যাসটির মধ্যে আধুনিক চরিত্র চিত্রায়ণ আছে, আছে শিক্ষিতা নারীর আত্মমর্যাদাবোধ, স্বাধীন বিচারবুদ্ধির সঙ্গে প্রথাগত পারিবারিক ভাবনাচিন্তার দ্বন্দ্ব। কল্যাণী এই উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র। উপন্যাসের সময়কালের প্রথম পর্বে সে কলকাতায় হোস্টেলে থেকে কলেজে পড়ে। মেয়েদের কলেজ, তবে দু চারজন পুরুষ অধ্যাপক আছেন। এছাড়া কল্যাণীর জীবনে আনাত্মীয় পুরুষ বলতে দাদার মেসের বন্ধুবান্ধবেরা। তাদেরই একজন – অবিনাশের সঙ্গে কল্যাণীর গোপনে মন দেওয়া নেওয়া হয়। সে আবার কল্যাণীদের গ্রামের জমিদারবাড়ির কাছেই থাকে।
কল্যাণী জমিদার তনয়া, তবে ততদিনে সেই জমিদারি গভীর সঙ্কটে। আয় প্রায় নেই, তবে ব্যয় নানাবিধ। ফলে সম্পত্তি কতদিন টিঁকবে তাই নিয়ে ব্যাপক প্রশ্নচিহ্ন। কল্যাণীকে তাই দ্রুতই চন্দ্রমোহন নামের এক বড়লোক পাত্রের হাতে তুলে দিতে তার বাবা, মা, দাদা সকলে সচেষ্ট। তাকে বাড়িতে অতিথি হিসেবে নিয়ে আসেন কল্যাণীর বাবা। অন্যদের থেকে ব্যাপক সমাদর পেলেও কল্যাণী চন্দ্রমোহনকে একেবারেই পছন্দ করে উঠতে পারে না। তার সমস্ত প্রশংসাবাক্যকে কেবলই সাজানো জাল বলে মনে করে। বিয়ের জন্য চাপ যখন প্রবল, তখন কল্যাণী শেষ চেষ্টা হিসেবে যায় প্রেমিক অবিনাশের কাছে। কিন্তু অবিনাশ কল্যাণীকে বিয়ে করতে প্রস্তুত নয়, সীমাহীন দারিদ্রই তার কারণ। কল্যাণীর ভাইও স্পষ্টই বোনকে জানিয়ে দেন অচিরেই তাদের জমিদারি চলে যেতে পারে, বাড়িটিও হয়ত চলে যাবে বিদেশ ফেরৎ দাদা আর তার বিদেশিনি বউয়ের কব্জায়। সে নিজেও বিয়ে করবে কিছুদিনের মধ্যে আর ভাইয়ের বউরা কেউই কল্যাণীকে তাদের সংসারে স্থান দেবে না। পতনোন্মুখ জমিদারীর দীনতার আখ্যান সামনে আসার আগেই বিয়ে করে ফেলা কল্যাণীর পক্ষে তাই সবচেয়ে বুদ্ধিমত্তার কাজ হবে। এইসব পরামর্শ আর প্রতিবন্ধকতাকে সামনে দেখে কল্যাণী শেষপর্যন্ত চন্দ্রমোহনের আকুতিতে সাড়া দিয়ে তাকে বিয়ে করে। বিয়ের পরেই সামনে আসে আসল রহস্য। সাত আট কোটি টাকার ব্যবসার যে গল্প চন্দ্রমোহন ফেঁদেছিল বিয়ের আগে, জানা যায় সে সবই কন্যাপক্ষকে বিভ্রান্ত করার সুনিপুণ চাল। জমিদার বাড়ির মেয়েকে বিয়ে করার জন্য বানিয়ে তোলা মিথ্যা কাগজপত্র। আদতে তার কাছে সাত আট কোটি নয়, আছে মাত্র সাত আট হাজার টাকা। সে কাজকর্মও কিছু করে না। ব্যাঙ্কে রাখা টাকার সুদে কোনও রকমে দিন চালায়। কল্যাণীর বাড়ির লোক এইসব গোপন মিথ্যা জেনে যাবার পর চন্দ্রমোহনের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কল্যাণী একাকী স্বামীগৃহে প্রতি বছর সন্তান সম্ভবা হতে থাকে। যে মেয়ে অনেক স্বপ্ন দেখেছিল, তার বাকী জীবনটা এক বিরাট মিথ্যাকে নিয়ে এরপর কাটাতে হবে এক প্রবঞ্জককে স্বামী হিসেবে মেনে নিয়ে আর অন্যান্য সব আত্মীয় পরিজন থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন থেকে।
মেয়েকে পাত্রস্থ করা নিয়ে কন্যার পিতামাতার চিন্তার কথা তো নানা দেশের সাহিত্যেরই এক বহুচর্চিত থিম। শাক্ত পদাবলী থেকে শরৎচন্দ্রের গল্প উপন্যাস – এর উদাহরণ অজস্র। কিন্তু জীবনানন্দের ‘কল্যাণী’ এর চেয়ে আলাদা। কারণ এখানে আখ্যানের কেন্দ্রে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা নেই, রয়েছে যাঁর বিবাহকে কেন্দ্র করে বাড়ির সকলের উদ্বেগ ও উদ্যোগ, সে নিজে বিষয়টিকে কীভাবে দেখছে।
কলেজ পড়ুয়া মেসের মেয়েদের জীবন জীবনানন্দের কল্যাণী উপন্যাসে যেভাবে উঠে এল, স্বাধীনতা পূর্ববর্তী বাংলা উপন্যাসে তার দ্বিতীয় কোনও নজির কি আছে? মেয়েদের আলাপচারিতার মধ্যে দিয়ে তাদের মনোজগতের এক খোলামেলা রূপ এই উপন্যাসে নিয়ে আসেন জীবনানন্দ। সব শিক্ষিত মেয়েই যে পুরনো সংস্কার বাদ দিয়ে নতুন চোখে জীবন ও জগৎকে দেখতে পারছে তা কিন্তু নয়। মিনুর সঙ্গে কল্যাণীর কথোপকথনটি লক্ষ করা যাক। কল্যাণীর দাদা তার বোনকে থিয়েটার দেখাতে নিয়ে যায়, এটা মিনু ভালোভাবে নেয় নি। ছোড়দার থিয়েটারের প্রতি ঝোঁক আছে, এটা মিনুকে বলতে গিয়েও কল্যাণী কথাটা গিলে ফেলে। “থিয়েটারের দিকে ঝোঁক? কেমন শোনায়? কল্যাণী লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল।”
কল্যাণী আর মিনুর বন্ধুত্বে শুধু কথা নেই, অল্প শরীরী বিনিময়ও আছে। মিনু কল্যাণীর মুখের অনুপম রূপসৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকে আর তারপর তাদের মধ্যে যে বিনিময় হয় তা এরকম –
কল্যাণীর নিঃশ্বাসের থেকেও যেন মিষ্টি ঘ্রাণ আসছে।
মিনু বললে – কি খেয়েছিস সে?
কখন?
মুখের থেকে তোর কিসের গন্ধ আসে?
জানি না তো।
জানিস না। সব সময়েই আমি পাই।
কল্যাণী বলে – কিসের গন্ধ রে মিনু?
মিনু কোনও জবাব দিল না, সৌন্দর্যের রসের থেকেই এ যেন এক ঘ্রাণ, পদ্মের রক্তমাংসের থেকে যেমন গভীর বিলাসের গন্ধ আসে তেমন, পদ্ম কি কিছু খায়?
একটা চুমো খাই কল্যাণী?
চুমো সে খেল –
এমন পরিতৃপ্তি মিনু কোনও দিনও পায় নি যেন।
একে সমকাম বা লেসবিয়ান সম্পর্কের পূর্ণ রূপ বলা যবে না ঠিকই, কিন্তু সেকালের এক উপন্যাসে কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা পরস্পরকে নিভৃতে চুম্বন করছে আর শরীরী তৃপ্তি পাচ্ছে, এ নিঃসন্দেহে এক ব্যতিক্রমী উপস্থাপণ।
এই উপন্যাসে মেয়েদের মেসের আড্ডার এক চমৎকার খণ্ডচিত্র পাই উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদটিতে। সেখানে দেখি রাতের বেলা কল্যাণীর টেবিলের পাশে পাঁচ ছয় জন মেয়ে এসে জড় হয়েছে। তারপর শুরু হয় তাদের রাতের আড্ডা। তখন ভাদ্র মাস, বাইরে প্রবল বৃষ্টি। আড্ডায় আছে কল্যাণী, মিনু, কমিশনারের মেয়ে চিতু, মীরা, সুপ্রভা, আবসী। আবসীর মুখে কোনও সংলাপ নেই, বাকী সকলেই কিন্তু নানা বিষয়ে নানা কথা বলে ও নিজেদের মতামত খোলাখুলি জানায়।
চিতু চরিত্রটির উপস্থাপণ রয়েছে খানিকটা বিদ্রুপের ভঙ্গীতে। পরাধীন আমলের সেই সময়ে চিতু ইংরাজদের অক্ষম নকলনবিশ। সে কাঁটা চামচ আর ছুরি দিয়ে খায়, ইংরাজী গান গায়। বাংলা মাসের নামগুলোও সে জানে না। ঋতু বৈচিত্র্য সম্পর্কেও তার প্রাথমিক ধারনা নেই, তাই বোকার মতো সে বলে ভাদ্র মাসেই কেন বৃষ্টি হবে। ইংরাজী সিজনের মতো বাংলাতেও যে নানা ঋতু আছে তা শুনে সে মন্তব্য করে এ নিশ্চয় ইংরেজদের নকল করে শেখা। স্বাভাবিকভাবেই চরিত্রটি বাকীদের হাস্যকৌতুকের নিশানা হয়।
অল্প কয়েকজন সে সময় শিক্ষয়িত্রীর পেশায় আসছেন, কিন্তু মিনুর মতো কেউ কেউ মনে করে মেয়েরা ততটা যোগ্য শিক্ষাদাতা নন। তাদের সে নানাভাবে হেয় করে। অন্যদিকে এই আলোচনায় চিতুকে দেখা যায় সে মেমসাহব শিক্ষয়িত্রীদের পড়ানোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। অবশ্য এও বোঝা যায় সাহিত্য সম্পর্কে তার কোনও বিশ্লেষণী দৃষ্টিকোণ নেই, সে বিষয়ক কিছু শুকনো তথ্য আছে মাত্র। সাহিত্যের সবচেয়ে বড় গুণ হিসেবে তাই সে অক্লেশে উচ্চারণ বা প্রনানসিয়েশনকে চিহ্নিত করতে পারে। বাঙালি প্রফেসররা তার মতে ভালো লেকচার দিতে অক্ষম, কারণ তারা বিলিতি কায়দার উচ্চারণ জানে না।
মিনু একজন নবীন অধ্যাপক – মিস্টার গাঙ্গুলির পড়ানোর প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কল্যাণী যখন মিনুকে সেই অধ্যাপককে বিয়ে করার কথা ভাবতে বলে, সুপ্রভা বলে মিস্টার গাঙ্গুলি নিশ্চয় মিনুকে নয়, কল্যাণীকেই পাত্রী হিসেবে পছন্দ করবেন, কারণ সেই সবচেয়ে সুন্দরী।
এই প্রসঙ্গেই বেরিয়ে আসে কল্যাণী চরিত্রের অহং ও পারিপারিক পরিচয়ের গুমর। “টিচার বিয়ে করব আমি? আমার আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই।”
মীরা অবশ্য খুশি মনে যে কোনও একজন প্রফেসরকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। বাকীরা যখন বিয়ের জন্য কোন যোগ্যতার কেমন পাত্র পছন্দ তাই নিয়ে আলাপ জমায় তখন সুপ্রভা ঘোষণা করে সে বিয়ে করবে না। দেখতে সুন্দর, স্মার্ট, পড়াশুনোয় সকলের চেয়ে এগিয়ে থাকা সুপ্রভা ঘোষাল জানিয়ে দেয় তার ব্যতিক্রমী ভাবনা। সে কলেজের পরীক্ষায় পাশ করে চলে যেতে চায় তার মেজদিদি আর জামাইবাবুর কাছে নৈনিতালে।
উপন্যাসের শেষে একটি প্রবঞ্চনাময় বিবাহের সূত্র ধরে কল্যাণীর জীবনে ট্রাজেডি নেমে আসতে দেখি আমরা। কল্যাণীর ট্রাজেডি শুধু তার ব্যক্তিগত ট্রাজেডি নয়, সেকালের নব্যশিক্ষিত আত্মসচেতন নারীদের এক সাধারণ ট্রাজেডি। তারা শিক্ষার আলোতে দীপ্ত হল কিন্তু কাজের জগতে তখনো তাদের প্রবেশ ঘটল না সেভাবে। কলেজের মেসের ছাত্রীদের আলাপ আলোচনাতে নব্যশিক্ষিতা মেয়েদের দল নিজেরাই এই আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছিল, কিন্তু এর সমাধানসূত্র তাদের জানা ছিল না। অন্যান্য সকলেই যখন বিবাহের জন্য স্বামীর পেডিগ্রি কেমন হওয়া উচিত তাই নিয়ে আলাপ আলোচনা ও তর্ক করে তখন সুপ্রভা ঘোষাল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে দীপ্তিময়ী ছাত্রী জানায় সে বিয়ে করতে চায় না, হয়ত সাহিত্য আর আর্ট নিয়েই থাকতে চায়। কিন্তু জীবন চালানোর রুজি রোজগারের জন্য সেও কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের কথা ভাবে নি, ভেবেছে পাহাড়ে দিদি জামাইবাবুর আশ্রয়ে মনোরম পরিবেশে থেকে যাবে বাকী জীবন। “সুপ্রভা বললে – পাশ করব। পাশ করে চাকরী ফাকরী নেব না আর। মেজদির ওখানে গিয়ে কাটাব – নইনীতালে – পাইন বনের বাতাসের মধ্যে।” কল্যাণীও তেমন কিছুই করার কথা ভাবে। মিনু কিন্তু সুপ্রভার এই পরনির্ভর জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত মেনে নিতে চায় নি। -
“মিনু বলে – ওতে মনুষ্যত্ব থাকে না।
কল্যাণী বললে – কেন?
মিনু বললে – হয় স্বামীর সঙ্গে থাকতে হয় – না হয় নিজে করে খেতে হয়”।
নব্য শিক্ষিতা মেয়েদের চেতনায় যে বদল এলো, জীবন জীবিকা তার থেকে পড়ে রইলো খানিকটা দূরেই। কারণ মেয়েদের কাজের বাজার তখনো তৈরি হয় নি। নিজের ভাগ্যনিয়ন্ত্রা নিজেই হবে, এই আকাঙ্ক্ষা আর অর্থনৈতিক বাস্তবতার মধ্যে ফলে থেকে গেল এক অনতিক্রম্য ব্যবধান। এই ব্যবধান নতুন সময়ের নতুন যন্ত্রণা। এই যন্ত্রণাবোধের সঙ্কটকে ধারণ করেছে বলেই কল্যাণী হয়ে উঠেছে আধুনিক যুগযন্ত্রণার উপন্যাস। এই উপন্যাস তিরিশের দশকে প্রকাশিত হলে তা সমকালীন বাংলা কথাসাহিত্যে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে দিতে পারত। যিনি এর পরের বছরেই অমিত উৎসাহ আর উদ্দীপণায় একটানা ছটি উপন্যাস লিখে ফেলবেন, কল্যাণীর মতো এমন একটি রচনা নির্মাণের পরও কেন তিনি তা প্রকাশের কথা ভাবলেন না, তা নিয়ে আক্ষেপ তৈরি হয় আমাদের।
