
নকশালবাড়ি আন্দোলন ও বাংলা সিনেমা : সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন ও ঋত্বিক ঘটক
- 24 July, 2021
- লেখক: মৌসুমী বন্দ্যোপাধ্যায়
এই প্রবন্ধের শুরুতেই স্বীকার করে নেওয়া দরকার যে, মাধ্যমগত কারণেই সাহিত্যের চেয়ে সিনেমার ভাষা আলাদা, উপরন্তু সেই ভাষা দিয়ে ভোক্তা বা দর্শকের সঙ্গে সংযোগের সেতু নির্মাণ করতে গেলে নির্দিষ্ট ভাষাগোষ্ঠীর ভিতর সাক্ষরতা একটি শর্তরূপে দাঁড়ায় না, এমনকি, সাবটাইটল ছাড়াও সেই দৃশ্যমাধ্যমে অন্য ভাষাভাষী দর্শকের দরবারে পৌঁছানো যায়। সুতরাং সাহিত্যের পাঠক এবং সিনেমার দর্শকের মধ্যে পার্থক্য থেকে যাচ্ছে এবং এই হিসাবে সিনেমার আরো বেশিসংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছানোর কথা। আমাদের আলোচ্য সত্তর দশকের সিনেমায় উঠে আসা বাস্তবতা তথা নকশাল আন্দোলন, এই অধ্যায়ে আমরা দেখাতে চাইব সেই সময়কে পরিচালকরা কতোখানি তাঁদের ছবিতে জায়গা দিয়েছেন বা দিতে চেয়েছেন এবং সেই বাস্তবতার চলচ্চিত্রায়ণে তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন ছিল। আমরা এক্ষেত্রে এছে নিয়েছি বাংলা চলচ্চিত্রের তিন প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্বকে- সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক এবং মৃণাল সেন।
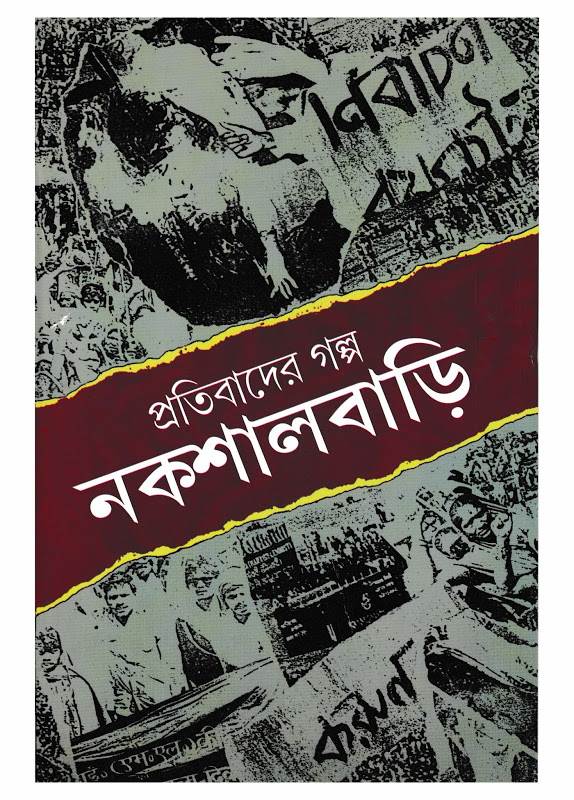
আমাদের মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে একটি বিষয় মাথায় রাখা প্রয়োজন যে, নকশাল আন্দোলন নিয়ে যাঁরা উপন্যাস, ছোটোগল্প, স্মৃতিকথা বা কবিতা লিখেছেন, তাঁদের অনেকেই নকশাল রাজনীতির প্রত্যক্ষ কর্মী ছিলেন। চলচ্চিত্র-পরিচালকদের কেউ কেউ বামপন্থী আদর্শে বিশ্বাসী হলেও তাঁরা কেউই নকশালকর্মী ছিলেন না। তার সম্ভাব্য কারণটি অর্থনৈতিক। সিনেমা বানাতে তখনকার যুগে বেশ ভালো পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হত, মধ্যবিত্ত বা নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে আসা নকশাল কর্মীদের পক্ষে কাগজে কলমে লেখা যতো সহজ ছিল, বলা বাহুল্য, সিনেমা বানানো ততো নয়। দ্বিতীয় কারণটি আরো বাস্তব। সিনেমাকে আমদরবারে পৌঁছাতে গেলে অর্থাৎ ‘রিলিজ’ হতে গেলে সেন্সর বোর্ড বা সংস্কৃতিমন্ত্রকের ছাড়পত্র লাগে, রাজনৈতিক কর্মীদের যেখানে প্রাণ বাঁচাতে পালিয়ে বেড়াতে হয়, সেখানে এই প্রাতিষ্ঠানিক ছাড়পত্র পাওয়া দূরস্থান। জনসংযোগ যেখানে উদ্দেশ্য, সেখানে ফিল্ম বানিয়ে প্রিন্ট লুকিয়ে রাখা অবান্তর, বরং জেলে বসে লেখা কবিতা বা ইস্তাহার চোরাপথে কর্মীদের কাছে পৌঁছানো সহজতর। ফলে পরিচালকদের পক্ষে নকশাল হওয়াটা কোনোক্রমেই সম্ভব নয়।

আমাদের উক্ত আলোচনার সূত্র ধরে আরো একটি বিষয় উঠে আসে। সিনেমা তার মাধ্যমগত আকর্ষণে একদিকে যেমন বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে, ছাপা কালো অক্ষরের তুলনায় অভিনেতাদের হাঁটাচলা, স্বরক্ষেপণ, সঙ্গীত ও ছবিব্যবহারের আবেদন যেমন বেশি, সেই সঙ্গে এটাও মানতে হয় যে, সিনেমাকে দর্শকের সামনে পৌঁছাতে ন্যূনতম পরিকাঠামোটুকুর দরকার ছিল। অতীতকাল ব্যবহার করা হচ্ছে এই অর্থে যে, ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের যুগ শুরু হবার আগে পর্যন্ত অন্তত সিনেমাকে নাগরিক বিনোদনই বলা হত, ‘নাগরিক’ শব্দটি এখানে আঞ্চলিক অর্থে প্রযুক্ত, সাংস্কৃতিক অর্থে নয়। এই বিষয়টিকে মাথায় রাখলে বোঝা যাবে, দৃশ্য-শ্রাব্য মাধ্যম হয়েও কেন সিনেমা নাটক বা যাত্রাপালার মতো গ্রামেগঞ্জের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে পারছে না। অর্থাৎ এই দিক থেকে বিচার করলে সিনেমার দর্শকের একটি আলাদা শ্রেণি তৈরি হয়ে যাচ্ছে এবং সেই শ্রেণির ভিতরেও শ্রেণি থাকবে সত্যজিৎ, মৃণাল বা ঋত্বিকের ছবি দেখার জন্য।

উক্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে সত্তরের দশকের চলচ্চিত্রকে যদি পর্যালোচনা করি, তাহলে দেখব, তার বিষয় হিসাবে নকশাল আন্দোলনের স্থান পাওয়ার সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। যেহেতু পরিচালকেরা কেউই এই আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না, ফলে এই আন্দোলনের আদর্শের প্রতি প্রবল আবেগ তাঁদের সিনেমায় প্রদর্শিত হবে-এটা অপ্রত্যাশিত। কিন্তু সচেতন পরিচালক সমসময়কে এড়িয়ে যেতে পারেন না, ইতিহাসবোধ ও সমাজচেতনার কারণেই তাঁকে উক্ত আন্দোলনের ছিটেফোঁটা সিনেমায় দেখাতে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, সিনেমা অনেক সময়েই কোনো লেখকের গল্প বা উপন্যাস থেকে তৈরি হয়। সেই ক্ষেত্রে কাহিনি থেকে চিত্রনাট্যের রূপান্তরে পরিচালক কিছু কিছু বর্জন বা সংযোজন করে থাকেন। আমরা সেই রূপান্তরগুলি থেকে পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির কিছু হদিশ পেতে পারি।

গত শতকের সত্তর দশকের বাংলা চলচ্চিত্রে নকশাল আন্দোলনের প্রভাব সঙ্গত কারণেই সামান্য, কারণটি আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বরং এই সময়কার বাংলা সিনেমায় গল্প-উপন্যাসের মতোই নরনারীর প্রেমকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই রোমান্টিকতার প্রদর্শন মধ্যবিত্ততার সংকটেরই উলটো পিঠ। এই সংকটের চেহারাটা কেমন ছিল, সে সম্পর্কে পরিচালক মৃণাল সেন জানাচ্ছেন-
“একটি ছোট্ট গল্প বলতে হয়, এ-শহরটাকে নিয়ে যে কাহিনি শুনেছিলাম আমার প্রিয় বন্ধু গুলজারের কাছে। সেই মুম্বইয়ের গুলজার। ছবির নির্মাতা, কবি, লেখক গুলজার। কলকাতার দক্ষিণে বেশ কিছুটা সময় গুলজার বসবাস করেছিলেন। একদিন বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন, তাঁর হাতে ছিল একটা থলে। এক প্রতিবেশী, অবশ্যই বাঙালি, গুলজারকে সকালবেলা দাঁত মাজতে মাজতে বললেন, ‘মাছ কিনতে যাচ্ছেন মশাই? ওই দিক দিয়ে চলে যান।’ এই দিকে তখন গোলাগুলি চলছিল। হাসতে হাসতে আমাকে গুলজার কাব্য করে বলেছিলেন, ‘এই হল কলকাতা। একটা যুদ্ধক্ষেত্র অথচ সব শান্ত স্বাভাবিক।’ ’’১(পৃ-৭, তৃতীয় ভুবন)
সময় থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখার আশ্চর্য ক্ষমতা কলকাতা অর্জন করেছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্মলগ্ন থেকেই, অর্থাৎ উনিশ শতকের নগরায়ণ থেকেই। আমরা দেখি, উনিশ শতকের খণ্ডিত আলোকায়ন ও আধুনিকতার কালে ইংরাজিশিক্ষিত নব্য বাঙালি তার স্বাভাবিক বিবর্তনের পথে আসা সাংস্কৃতিকতার ধারাকে অস্বীকার করে পাশ্চাত্যের অনুকরণে শহরকেন্দ্রিক সভ্যতার হুজুগে মেতে ঊঠেছিল, অথচ তার শিকড় থেকে পুরনো সামন্ততান্ত্রিক ধ্যানধারণা তখনো মুছে যায় নি। অর্থনীতির দিক থেকে পুঁজিবাদ ও সামন্ততান্ত্রিকতার আবহাওয়ায় বাঙালি এক কৃত্রিম সংস্কৃতির শরিক হয়, অথচ গ্রামিণ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির অবক্ষয়ের কালে, কৃষক-তন্তুবায়ের দুর্দশায় পত্রপত্রিকায় তর্কবিতর্কের ঝড় তোলা ছাড়া মধ্যবিত্তের অবদান যৎকিঞ্চিৎ। বৃটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় কলকাতামুখী বাঙালির সংস্কৃতি যে মধ্যবিত্ততার জন্ম দিয়েছিল, তাতে বৃহত্তর বঙ্গসংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্য ছিল তার স্বভাবজাত। ফলে প্রথম থেকেই বাঙালির মধ্যবিত্ততা আত্মকেন্দ্রিক এবং সেই আত্মকেন্দ্রিকতা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও ব্যক্তিস্বাধীনতার পাশ্চাত্য বুলি দ্বারা মহিমামণ্ডিত। আবার সেই উনিশ শতক থেকেই যাবতীয় সমাজ সংস্কার আন্দোলন, রাজনৈতিক আন্দোলনের নেতৃত্ব মধ্যবিত্ত সমাজ থেকেই উঠে এসেছে। সত্তরের আন্দোলনেও মধ্যবিত্ত তরুণদের অবদান অনস্বীকার্য। প্রকৃতপক্ষে, সূচনা থেকেই মধ্যবিত্তের সঙ্গে স্ববিরোধ শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে, যদিও আমাদের মনে রাখতে হবে, সেই উনিশ শতক থেকেই মধ্যবিত্ত সমাজের সকলে নয়, বরং কোনো কোনো বিবেকবান মানুষ সমাজসংস্কারের কাজে অংশগ্রহণ করেছিলেন, কেউ শ্রেণিস্বার্থ বজায় রেখে, কেউ বা তা অতিক্রম করে।
‘মধ্যবিত্ত’ শব্দটি অর্থনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়েও পরবর্তী কালে অর্থনীতির অতিরিক্ত এক মানসিকতাকে বোঝাতে শুরু করে। অর্থনৈতিক শ্রেণি হিসাবে কেউ নিম্নবিত্ত হয়েও মানসিকতায় মধ্যবিত্ত হতে পারেন। দাঙ্গা ও দেশভাগের কালে বাধ্য হয়ে যে সকল শরণার্থী ও পার বাংলা থেকে এপার বাংলায় এসে অস্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন, এপার বাংলায় আর্থসামাজিক অবস্থানের দিক থেকে তাঁরা বিধ্বস্ত হলেও তাঁরা তাঁদের মধ্যবিত্ত মূল্যবোধকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চেয়েছিলেন। অর্থনৈতিক কারণেই তা সবসময় সম্ভব হয় নি, তাঁদের সেই শ্রেণিচ্যুতির ইতিহাস গল্পে উপন্যাসে আমরা পাই, পাই সিনেমাতেও। এটি একটি উদাহরণমাত্র। বাংলার যাবতীয় শিল্পমাধ্যমের বিস্তারিত পটভূমিকায় আমরা মধ্যবিত্ততারই জয়গান শুনতে পাই, মধ্যবিত্ত লেখক,চিত্রী, শিল্পী, চলচ্চিত্রীদের হাতে মধ্যবিত্ততার বহুকৌণিক বিশ্লেষণ বাংলার সংস্কৃতি ও শিল্পের মূলস্রোত হয়ে ধরা দিয়েছে, লোকশিল্প সেখানে প্রান্তিক বলে পরিগণিত অথবা মধ্যবিত্তের হাতে পড়ে ‘এন্টিক’, ‘এথনিক’ ইত্যাদি শব্দে রূপান্তরিত। এই মধ্যবিত্ততা এবং তার বিচ্ছিন্নতাবোধ সাহিত্যের মতো সিনেমাকেও কীভাবে দখল করেছিল, সত্তরের উত্তাল রাজনৈতিক পটভূমিতেও বাংলা সিনেমা গতানুগতিক মধ্যবিত্ততাকে আশ্রয় করেছিল, তা এবার লক্ষ করা যাক।
‘বাঙালির মর্মাশ্রয় করিতে হইলে ধর্মাশ্রয় করিতে হইবে’- গিরিশচন্দ্রের এই নিদান বাংলা সিনেমার ক্ষেত্রেও খাটে। আমরা যদি বাংলা সাহিত্যের যাত্রাপথটি লক্ষ করি, তাহলে দেখব প্রাচীন থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত ধর্মই ছিল সাহিত্যের কেন্দ্রীয় বিষয়, নরনারীর প্রেম সাহিত্যের বিষয় হয়েছিল বাংলার বাইরে- আরাকানে। পরবর্তী কালে অর্থাৎ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের আধুনিকতার যুগে ব্যক্তিমনস্তত্ত্ব হয়ে ওঠে তার বিষয়। সেই হিসাবে সিনেমার যাত্রা শুরুই হয়েছিল দেরিতে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করব সাহিত্যের ক্ষেত্রে বাঙালির আধুনিকতায় পৌঁছাতে যেখানে সময় লেগেছিল শত শত বছর, সেখানে বিষয় ও আঙ্গিকের দিক থেকে বাংলা সিনেমা সাবালকত্ব অর্জন করে একশো বছরের মধ্যেই। অথচ শুরুতে সিনেমারও বিষয় ছিল ধর্ম। ধর্ম এবং রোমান্টিকতা- এই দুটিকে বিষয় করে বাংলা চলচ্চিত্র বহুদিন পর্যন্ত দর্শকের মনোরঞ্জন করেছে এই কারণে যে, বাঙালি মধ্যবিত্তের মনস্তত্ত্বে ব্যক্তিপ্রাধান্যের পাশাপাশি প্রাগাধুনিক সামন্ততান্ত্রিকতার চিহ্ন হিসাবে ধর্মবোধের বিশিষ্ট স্থানটি রয়ে গিয়েছে। মিশ্র অর্থনীতির দেশে বাঙালির মনস্তাত্ত্বিকতাও পুঁজিতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রকে বিস্ময়করভাবে লালন করে গেছে, অত্যাধুনিক যুগেও। মজার কথা, কখনো কখনো ব্যবসায়িক প্রয়োজনেই ধর্মের মোড়কে পরিবেশন করা হয়েছে আধুনিক নরনারীর প্রেম, সাতের দশকে বিশ্বজিৎ চট্টোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা রায় অভিনীত বাবা তারকনাথ (১৯৭৭)ছবিটির বিপুল জনপ্রিয়তা যেমন বাঙালির মেজাজমর্জিকে চিনিয়ে দেয়, তেমনি প্রযোজক-পরিচালকও যে সেই মর্জির উপযুক্ত যোগানের মাধ্যমে বিপণন ও ব্যবসার সঠিক পথটি চিনে নিতে পেরেছিলেন, তাও আন্দাজ করা যায়। এর দুবছর পরেই একই কারণে মুক্তি পেয়েছিল ডুব দে মন কালী বলে। আমাদের বক্তব্য হল, স্বাধীনতা-পূর্ব ও পরবর্তী সময়ে যেখানে দেশিয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে নৈরাজ্য ও অশান্তির বাতাবরণ, দেশভাগ, মন্বন্তর, জাতিদাঙ্গা, ভারত-পাক ও ভারত-চিন যুদ্ধ, একাত্তরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও শরণার্থী সমস্যার মতো জ্বলন্ত বিষয়গুলি বাঙালির সমাজ-সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলেছে, তখনো ধর্ম ও রোমান্টিকতার আফিমে মজে আছে বাঙালি দর্শকের সিংহভাগ। সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিকের ছবির দর্শককে ইন্টেলেকচুয়াল শ্রেণির দর্শক হিসাবে আলাদা স্থান দেওয়া হচ্ছে, কিন্তু আম বাঙালির জন্য তৈরি হচ্ছে যে ছবিগুলি- তাতে আলগাভাবে চোখ বুলিয়ে নিলে যে নামগুলি পাই তা এইরকম- নিশিপদ্ম (১৯৭০), ধন্যি মেয়ে (১৯৭১), মেম সাহেব (১৯৭২), বনপলাশীর পদাবলী (১৯৭৩), বিকেলে ভোরের ফুল, মৌচাক (১৯৭৪), অগ্নীশ্বর (১৯৭৫)। উত্তমকুমার ও সুচিত্রা সেনের বিখ্যাত রোমান্টিক জুটি তাদের যাত্রা শুরু করে ১৯৫৩-তে, সাড়ে চুয়াত্তর দিয়ে। বাঙালির এক ধ্বস্ত সময়ে একে একে তৈরি হয়েছে বিখ্যাত রোমান্টিক ছবিগুলিই- অগ্নিপরীক্ষা (১৯৫৪), সবার উপরে, শাপমোচন, দেবদাস (১৯৫৫), হারানো সুর, পথে হল দেরী (১৯৫৭) রাজলক্ষ্মী ও শ্রীকান্ত, ইন্দ্রাণী (১৯৫৮) চাওয়া পাওয়া, (১৯৫৯), সপ্তপদী (১৯৬১) বিপাশা (১৯৬২), দেয়া নেয়া (১৯৬৩)। বলা বাহুল্য, প্রতিটিই বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। আমাদের মনে হয়, বিনোদনের ক্ষেত্রে প্রতিদিনের জীবনবাস্তবতাকে বাঙালি আর জায়গা দিতে চায় নি, বরং যা তার জীবন থেকে হারিয়ে গিয়েছে, সেই সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, পারিবারিক জীবনের আদর্শ, যৌথ পরিবারের রীতিসংস্কৃতি- প্রভৃতিকে সে চলচ্চিত্রে দেখে নির্দয় বাস্তব থেকে দুই-আড়াই ঘণ্টার ছুটি চেয়েছে। এর আরো একটা কারণ, সেই সময়কার জীবনজিজ্ঞাসাকে নান্দনিকভাবে ফুটিয়ে তোলার ক্ষেত্রে শক্তিশালী পরিচালকেরও অভাব ছিল, সত্তরের দশকে সেই অভাব পূরণ করেছিলেন আমাদের আলোচ্য তিন পরিচালক। তাঁদের ছবির দর্শকের শ্রেণি আলাদা হলেও অন্তত সমসাময়িক বিষয়গুলি সিনেমায় উঠে আসতে পেরেছিল তাঁদের ইতিহাসবোধ ও সমাজসচেতনতার প্ররোচনায়। ফলে আমরা দেখি ১৯৭১-এই ধন্যিমেয়ের পাশাপাশি তৈরি হচ্ছে সত্যজিতের সীমাবদ্ধ, মৃণাল সেনের ইন্টারভিউ, ১৯৭২-এ মেমসাহেবের প্রায় সমান্তরালে থাকছে মৃণাল সেনের কলকাতা ৭১, কিংবা ১৯৭৩-এ বনপলাশীরপদাবলীর সঙ্গে অশনি সংকেত ও তিতাস একটি নদীর নাম। ১৯৭৪-এ কাজ শুরু হয়ে ১৯৭৭-এ মুক্তি পায় ঋত্বিক ঘটকের ছবি যুক্তি তক্কো আর গপ্পো।
রূপকথা শিশুসাহিত্য থেকে ডিটেকটিভ গল্প, রবীন্দ্রসাহিত্য থেকে বিভূতিভূষণ হয়ে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা শংকর, পুরাণসাহিত্য থেকে আধুনিক চলচ্চিত্র পর্যন্ত অবাধ বিচরণ করেছেন পরিচালক, চিত্রনাট্যকার, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ সত্যজিৎ রায়। তাঁকে আধুনিক যুগের পরিপূর্ণ শিল্পী বলা যায়। আধুনিক মনন ও মেধার দীপ্তিতে তাঁর ছবিগুলি বাংলা সিনেমার সম্পদ। নাটকীয়তা তাঁর চিত্রনাট্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, শিল্পের সূক্ষ্মতা তাঁর অন্বিষ্ট। স্বভাবতই শিল্পকে তিনি যে প্রচারমূলক বা ‘প্রোপ্যাগান্ডিস্ট’ করে তুলবেন না, তা প্রত্যাশিত। তাঁর বিভিন্ন সাক্ষাৎকার থেকে স্পষ্ট যে সত্যজিৎ বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা মতবাদের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেন নি, বরং শিল্পী হিসাবে উদারপন্থী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। তাঁর রাজনৈতিক ট্রিলজি বা ত্রয়ী, অর্থাৎ প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ এবং জন অরণ্যে-র নায়ক চরিত্রেরা সমাজসচেতন মধ্যবিত্ত, কিন্তু নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মতাদর্শে নিবেদিতপ্রাণ নয়। বরং তাদের চরিত্রের স্ববিরোধ, দ্রোহের ইচ্ছার সঙ্গে কাপুরুষতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও নিজেকে বাঁচিয়ে চলার মনোভাবে যে বহুবর্ণী মানবমন, পরিচালক সত্যজিৎকে তা আকর্ষণ করেছে বেশি। তাই আমরা দেখি প্রতিদ্বন্দ্বীর বুলু পার্শ্বচরিত্র হিসাবে থেকে যায়, উপন্যাসে থাকলেও সীমাবদ্ধতে টুটুলের প্রেমিককে তিনি পর্দার এপারে আনেনই না। আমরা এবার এই তিনটি সিনেমার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করে দেখাতে চাইব, নকশাল আন্দোলনের প্রভাব সত্যজিতের ছবিতে কীভাবে এবং কতোটা এসেছে।
১৯৭০-এ মুক্তি পায় সত্যজিৎ রায়ের প্রতিদ্বন্দ্বী। নায়ক সিদ্ধার্থের ভূমিকায় অভিনয় করেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়। মূল গল্পের লেখক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। আমরা দেখি, একটি নেগেটিভ ইমেজ দিয়ে শুরু হচ্ছে এই ছবির ভূমিকা, সিদ্ধার্থের বাবার শবদেহটি বাড়ির বাইরে আনা হচ্ছে। সিদ্ধার্থ মেডিকেলের ছাত্র ছিল, কিন্তু পিতৃবিয়োগের পর সংসারের দায়িত্ব নিতে গিয়ে অথবা টাকার অভাবে সে পড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। বাড়ির বড়ো ছেলে সে, শুরু হয় তার চাকরি খোঁজা। তার বোন একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করে, বসের নেকনজর আছে তার উপর, বসের সঙ্গে তার নাম জড়িয়ে কুৎসাও তার বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে যায়। আর রয়েছে ভাই বুলু, সে যে নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত, ছবিতে সেই কথা স্পষ্ট বলা না হলেও তার কথাবার্তা, পায়ের ব্যান্ডেজ, গ্রামে গিয়ে কাজ করার কথা ইত্যাদি থেকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হবার কথা নয় যে সে সমসাময়িক রাজনীতি থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে নি।
আমরা দেখি, এই ছবিতে পরিচালক একই পরিবারের তিনটি চরিত্রের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন সিদ্ধার্থ, তারপর তার বোন, তারপর ভাই বুলুকে। বুলুর থেকেও বেশি ‘স্পেস’ নিয়েছে সিদ্ধার্থর বন্ধু ডাক্তারির ছাত্রটি। এই চরিত্রগুলিকে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যাবে, পরিচালক সমসাময়িক রাজনীতি থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন অরাজনৈতিক ঘটনা ও চরিত্রকে, অথচ রাজনীতির উত্তাল পরিবেশকে তিনি এড়িয়ে যেতেও পারেন নি। বলা যায়, সমকালীন রাজনীতি ও সর্বাঙ্গীণ অস্থিরতা চরিত্রগুলিকে যেভাবে অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলছিল, সেই অনিশ্চয়তার মধ্যেই তাদের অর্থাৎ সাধারণ পরিবারের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীদের মানসজগৎকে উন্মোচিত করে দেখানোর প্রবণতা তাঁর মধ্যে কাজ করেছে।

সিদ্ধার্থ এই ছবির নায়ক, সে রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন, কিন্তু সেই একসময়ে ভাই বুলুকে চে গ্যেভারার বই উপহার দিয়েছিল। পিতার মৃত্যুর পরে সে যখন চাকরির সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়ায়, তখনো ইন্টারভিউ বোর্ডের প্রশ্নে সে জানায়, শতাব্দীর সবচেয়ে আলোড়ন তোলা ঘটনা ভিয়েতনামের যুদ্ধ। রাজনৈতিক ঘটনা সরাসরি দেখানো না হলেও দেয়ালে দেয়ালে নকশালবাড়ি আন্দোলনের পক্ষে নানা লিখন, মাও সে তুঙের স্টেন্সিল পটভূমির মতো আসে, আসে সিনেমা হলে বোমা পড়ার ঘটনা, ধর্মতলায় বিরাট জনসভা। আমাদের জানা নেই, সিদ্ধার্থ ডাক্তারি পড়া শেষ করে সুনির্দিষ্ট আয়ের পথটি পেয়ে গেলে আর পাঁচজন সংসারী গৃহস্থের মতো ক্ষণে ক্ষণে সিগারেট ধরিয়ে সমাজভাবনা ভাবত কি না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি আত্মকেন্দ্রিকই। অথচ আত্মকেন্দ্রিক হলেও তার মধ্যে স্বভাবজ নীতিবোধ কাজ করে। সে তার হবু ডাক্তার বন্ধুর মতো ফান্ডের টাকা ভেঙে ফূর্তি করতে পারবে না কোনোদিন। সে বন্ধুর মতো আত্মসর্বস্ব নয়, আবার ভাই বুলুর মতো বিপ্লবচেতনা, সমষ্টির মুক্তির জন্য প্রাণ দেবার মানসিকতাও তার নেই। একটা সময়ে তাকে অসহায় মনে হয়, যখন তার ভিতরকার সমস্ত দ্রোহের ইচ্ছাগুলি জেগে উঠলেও সমাজ-পরিপার্শ্বের চাপে নিজেকে সে দমন করে। সিনেমার ভিতর এমন দু-তিনটি সিচুয়েশন তৈরি করেন সত্যজিৎ। আমরা দেখি, বোনের বস সান্যালের প্রতি তার একটা আক্রোশ আছে, সেটা বোন সম্পর্কে কুৎসার কারণেই হোক বা পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ্যের কারণেই হোক। বোন আর চাকরি করবে না- অভিভাবক হিসাবে যখন এই কথা সে সান্যালকে জানাতে তার বাড়ি যায়, তখন সে ঘুরন্ত পাখার নিচেও প্রবল ঘামছে, চাপা উত্তেজনা ও রাগের বহিঃপ্রকাশ আমরা তার শরীরী ভাষায় খুঁজে পাই। কিন্তু ক্লোজ শটে পরিচালক দেখান পাঞ্জাবির উপর সান্যালের হিরের বোতামটি, সান্যাল জানান সিদ্ধার্থের জন্য তিনি অন্যত্র চাকরির সুপারিশ করতে পারেন। সিদ্ধার্থের যাবতীয় ক্ষোভ সে নিজেই দমন করে, প্রত্যুত্তরে ‘না’ বলার ক্ষমতা তার নেই, আবার সান্যালের মতো মানুষের সুপারিশে চাকরির সন্ধানেও তার মানসিক বাধা কাজ করে। সান্যাল ট্রাঙ্ক কল গ্রহণ করতে যাবার সুযোগে তার পালিয়ে যাওয়া সহজ হয় এবং সে পালিয়ে আসে। এই পলায়ন যেন নিজের থেকেই পলায়ন- নিজের সাবেক মূল্যবোধ থেকে, সংস্কার থেকে। এই পলায়ন আমরা আবার দেখি যখন তার হবু ডাক্তার বন্ধুটি তাকে নিয়ে যায় এক নার্স অথচ দেহোপজীবিনীর কাছে, নিজের নৈতিক অবনমন সে মেনে নিতে পারবে না। সত্যজিৎ দেখান, সিদ্ধার্থের মতো মধ্যপন্থী মানুষ আসলে সর্বত্র একা, সে সত্তরের উত্তাল রাজনীতির আদর্শের সঙ্গে নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত করতে পারে না, একটা গা-বাঁচানো মনোবৃত্তি তার স্বভাবজ। আবার চাকরির ইন্টারভিউ দিতে গিয়ে কর্তৃপক্ষের চরম অব্যবস্থা, প্রার্থীদের সঙ্গে প্রভুসুলভ আচরণ তাকে ক্ষিপ্ত করে। এই দৃশ্যটিকে অদ্ভুতভাবে এঁকেছেন পরিচালক, সেই সময়ে ইন্টারভিউ দিতে যাওয়া যেন সমস্ত প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে দেবার মতোই, একটি ছেলে গরমে মাথা ঘুরে পড়ে যায়। সিদ্ধার্থ দেখে সুদীর্ঘ ও নিষ্ফল প্রতীক্ষায় মানুষগুলি আর মানুষ নেই, জীবন্ত কঙ্কালে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই প্রতিবাদও সিদ্ধার্থের আপোসমুখী, যখন সে দেখে সে একা, পিছন থেকে সঙ্গে আসা দু-চারজন সরে গিয়েছে এবং তার নামধাম জানতে চাওয়া হচ্ছে, তখন চিহ্নিত হয়ে যাবার আশংকায় সেও সরে আসে। দ্বিতীয়বারেও যখন সে সত্যি সত্যি প্রতিবাদ জানায়, তখনো দূর মফঃস্বলে সেলস রিপ্রেজেন্টেটিভের চাকরিটির নিশ্চয়তা অবশ্যই তার মাথায় ছিল বলেই মনে হয়, নতুবা তার মতো সাবধানী চরিত্রের পক্ষে ঐ প্রতিবাদটুকুও করা অসম্ভব হত।
সত্তর দশকের কলকাতার রাজনীতি এই ছবিতে পটভূমি হিসাবে আসে, বরং সেই সময়কার মধ্যবিত্তের সমাজ-সাংস্কৃতিক অবক্ষয় ও অসহায়তা চিত্রণই এই ছবির প্রতিপাদ্য হয়ে ওঠে। পরিবারের একমাত্র রোজগেরে সিদ্ধার্থের বোন, সে চাকরির পর নাচ শেখে, মডেলিং করা তার ইচ্ছা, অফিসের বস সান্যালের সঙ্গে তাকে জড়িয়ে যে কুৎসা ছড়ানো হয়েছে, তাতে সে বিচলিত নয়। আমরা দেখি, সত্যজিতের ছবিতে এই ধরনের নারীচরিত্রের উপস্থিতি, জনঅরণ্য ছবিতে সুকুমারের বোন কণাও এই ধরনের চরিত্র। তারা আর্থিক প্রয়োজনে মধ্যবিত্ত সংস্কার ত্যাগ করে, ক্রমে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠে। সিদ্ধার্থ সেখানে তার পরিবারের সাবেক মূল্যবোধ, সামন্ততান্ত্রিক মনোভাব, পুরুষতান্ত্রিকতা ছেড়ে বেরোতে পারে না, সে থাকতে বাড়ির মেয়ে চাকরি করবে-এটা মেনে নিতে তার সম্মানে লাগে। সিদ্ধার্থের নিঃসঙ্গতা অমোঘ, সমকালের সঙ্গে তার সংযুক্তি ও বিযুক্তির মধ্যে অদ্ভুত দ্বন্দ্ব কাজ করে। ডাক্তার বন্ধুটির কথা অনুযায়ী তখনকার যুবসমাজের মধ্যে দুটি দল- একটি দল কাজ করে, তারা ডুয়ার্স, অন্য দল কাজ করে না, শুধু চিন্তা করে, তারা থিঙ্কার্স। সিদ্ধার্থ অবশ্যই দ্বিতীয় দলের। তার চলাফেরার ভিতর যতোটুকু দ্রোহ, তা তার সামাজিক নিরাপত্তার সীমাকে অতিক্রম করতে পারে না। ফলে অনেক মানুষের ভাবনাচিন্তা যখন সম্মিলিত হয়ে প্রতিবাদের আগুন জ্বালিয়ে তোলে এস্প্লানেডে, তখন সে তার প্রেমিকার সঙ্গে অনেক উঁচু একটি ম্যানসনের গাড়িবারান্দার উপর ব্যক্তিগত সমস্যার কথা আলোচনা করে। তার মধ্যে এক পলায়নপর রোমান্টিকতা কাজ করে সবসময়ে, কলকাতার যাবতীয় প্রাণচাঞ্চল্যের আকর্ষণ ছেড়ে সে মফস্বলে যায় চাকরি করতে। এক পাখির ডাক, যা সে খুঁজছিল অনেকদিন ধরে, তা সে পেয়ে যায় তার নতুন কর্মস্থলে। সত্যজিৎ এখানে পাখির ডাককে রোমান্টিক পলায়নের ইঙ্গিত হিসাবে ব্যবহার করেছেন। সিদ্ধার্থ সমকাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়, মধ্যবিত্তের এই বিচ্ছিন্নতা, স্থির শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি তার চিরাচরিত আকর্ষণ যে আসলে স্থবিরতাধর্মী মৃত্যুরই অন্য পিঠ, তা এই ছবিতে সাংকেতিকভাবে ব্যবহৃত হয় শেষ দৃশ্যে, ‘রাম নাম সৎ হ্যায়’-র শবযাত্রার ধ্বনিতে। সত্যজিৎ রাজনীতিবিমুখ বলে ইতোমধ্যে সমালোচনা করেছেন অনেকেই, কিন্তু আমাদের মনে হয় তাঁর শিল্পীমন রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত না হয়েও সমকালের প্রেক্ষিতে ব্যক্তিমনকে ধরতে চেয়েছে এবং সেক্ষেত্রে সমকালকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় যেমন, তেমনি নকশাল রাজনীতি সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও এই ছবির নায়কচরিত্রের পলায়নী মনোবৃত্তিকে তিনি সমর্থন করেছেন বলেও মনে হয় না, তা না হলে পাখির কূজনের সঙ্গে মৃত্যুগন্ধী শব্দকে তিনি একই শাব্দিক ফ্রেমে আনতেন না।
সীমাবদ্ধ (১৯৭১) ছবিটির কাহিনি শংকরের উপন্যাস থেকে নেওয়া। এই ছবির নায়ক শ্যামলেন্দু চ্যাটার্জির ভূমিকায় অভিনয় করেছেন বরুণ চন্দ। শ্যামলেন্দুর আত্মকথন দিয়ে ছবি শুরু হয় এবং সে জানিয়ে দেয় কলকাতা শহরের শিক্ষিত দশ লক্ষ বেকারের মধ্যে সে পড়ে না। তার এই গর্বিত আত্মঘোষণার মধ্যে দিয়ে পরিচালক সমষ্টি ও সমষ্টিগত সমস্যা থেকে প্রথমেই নায়ককে আলাদা করে নেন। সেই অর্থে সিদ্ধার্থ বা জন অরণ্য ছবির সোমনাথের মতো শ্যামলেন্দুর সমস্যাই নেই, উঁচু পদের চাকরি, প্রচুর অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী, অফিসের দেওয়া ফ্ল্যাট, গাড়ি, টেলিফোন ও একটিমাত্র পুত্রসন্তান নিয়ে সুখের সংসার তার, যদিও সন্তানের উল্লেখ থাকলেও সিনেমায় তাকে দেখা যায় না। সিদ্ধার্থের মতো কোনো দ্বন্দ্বও তার নেই, কারণ সেই অর্থে সে কোনো অনিশ্চিত জীবন যাপন করছে না। তার সমস্যা বলতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা এবং সেই পথে একজন প্রতিদ্বন্দ্বী। তার সাজানো গোছানো সংসারে বেমানান তার বাবা-মা, তাঁরা হঠাৎ বালিগঞ্জ থেকে তার বাড়িতে পার্টি চলাকালীন উপস্থিত হয়ে নিজেরাই অস্বস্তিতে পড়েন। এই বাড়িতে শ্যালিকা টুটুল (শর্মিলা ঠাকুর চরিত্রটি অভিনয় করেছেন) আসার পর শ্যামলেন্দু তার সাজানো সংসারের ফাঁকফোকরগুলি দেখতে পায়। তার স্ত্রী দোলন সংসারের কর্ত্রী হয়েও অগোছালো, নিজের সাজগোজ, রূপচর্চা, ম্যাগাজিন পড়া, বাইরে খাওয়া, শ্যামলের অন্য সহকর্মীদের স্ত্রীদের সঙ্গে গল্পগাছা করে সময় কাটানোর মধ্যে এক ধরনের পরিপাটি সাজানো জীবন রয়েছে, কিন্তু টুটুলের মতো সংবেদনশীল মন তার নেই। বই গুছিয়ে রেখে, গ্রামোফোনে সেতারের সুর বাজিয়ে টুটুল যে আবহ তৈরি করে, সেই আবহে তার সঙ্গে এক ধরনের অন্তরঙ্গতা তৈরি হয় শ্যামলেন্দুর, কিন্তু তা শোভনতার স্তরেই থাকে। বরং ভিতরে ভিতরে টুটুলের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিকে একটু সমীহ করে সে, শেষ পর্যন্ত কারখানায় সাজানো স্ট্রাইক, ধর্মঘট, তালা ঝোলানো আর বোমা পড়ার ভিতর যে তার হাত রয়েছে, তা টুটুলের কাছে ধরা পড়ে যায়। শেষ দৃশ্যে তার উপহার দেওয়া হাতঘড়িটি ফেরত দিয়ে দেয় টুটুল।

সীমাবদ্ধ ছবিতে চরিত্রের কোনো দ্বন্দ্ব নেই, সবটাই লিফট অথবা সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠার মতো মসৃণ। শুধু উপরে ওঠার শেষ দৃশ্যে লিফট খারাপ হওয়ায় সিঁড়ি দিয়ে আটতলা পর্যন্ত ওঠার ক্লান্তিটুকু পরিচালক ইঙ্গিতবহ করে তোলেন। সিঁড়ি যেন শেষ হয় না, যেমন শেষ হয় না মানুষের চাহিদা বা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ক্লান্ত হলেও মানুষ সেই পথে এগোয়, যেমন শ্যামলেন্দুরও একসময়ে সিঁড়ি বাওয়া শেষ হয়। কিন্তু গোটা সিনেমায় এই ক্লান্তি, টুটুলের ঘড়ি ফেরত দেওয়া, বোমায় আহত ওয়াচম্যানকে হাসপাতালে দেখতে যাওয়া কিংবা বোমা ফেলা নিয়ে মৃদু দ্বিধা ছাড়া তার চরিত্র বা ঘটনার মধ্যে কোনো বিপ্রতীপতা নেই। পরিপাটি সাজসজ্জা, মেল শভিনিজমের আড়ালে সে প্রায় নির্দ্বিধায় ড্রিংক নিতে নিতে তালুকদারের সঙ্গে কারখানা বন্ধের সমগ্র পরিকল্পনাটি হাসতে হাসতে করে ফেলতে পারে, তালুকদার তাকে অভয় দেয়- “মশাই আপনি তো কোনো অন্যায় করছেন না।” সবকিছুর সঙ্গে কোম্পানির স্বার্থ জড়িত, কোম্পানিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না, এক্সপোর্ট মার্কেটে কোম্পানির সুনাম অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই অজুহাতে রাতারাতি বারোশো কর্মীর চাকরি খেয়ে নেওয়াকে অনৈতিক মনে হয় না তার।
মূল উপন্যাসে টুটুলের কলকাতা ভ্রমণ ছিল, ছিল নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনকে কাছ থেকে দেখা। এখানে তা বাদ দিয়েছেন পরিচালক, বরং দিদিদের সঙ্গে রেসের মাঠে, ক্লাবে, ক্যাবারে নৃত্যসম্বলিত বারে দেখতে পাওয়া যায় তাকে। এই ছবিতে নকশাল রাজনীতি করে, এমন চরিত্রের উল্লেখটুকু আছে মাত্র, উপস্থিতি নেই- সে টুটুলের প্রেমিক। চরিত্রদের মুখে শুধু সেই রাজনীতির কথা আসে। টুটুল যখন পাটনা থেকে আসে, তখন জানায়, কলকাতা শহর ঘিরে সকলের আতঙ্কের কথা। সে জানতে চায় যারা মারছে, তাদের শ্যামলেন্দু চেনে কি না। শ্যামলের স্ত্রী দোলন আটতলার ফ্ল্যাট পেয়ে খুশি, সেখানে মশা মাছি বা শহরের অন্য উৎপাতগুলি পৌঁছায় না। শুধু মাঝে সাঝে বোমা পড়ার শব্দ আসে। সান্ধ্য পার্টিতে আলোচনা হয় মদ খেতে খেতে, প্রশ্ন ওঠে কলকাতা শহরে এসব কী হচ্ছে। একজন বলে “ ওদের ধরে ধরে চাকরি দিয়ে দাও”, প্রত্যুত্তর আসে- “চাকরি দিয়েই বা লাভ কী, সেখানেও একটা ইউনিয়ন করে বসবে।” শ্যামলেন্দু বলে যে ওদের মতে পুরো ব্যবস্থাটাই পচে গেছে, চাকরি ওরা চায় না। তখন আর একজন বলে যে ওরা বিপ্লব চায়। সৌমেনের মুখ থেকে বেরিয়ে আসে, এখন দরকার ডিক্টেটর। শ্যামলেন্দু বলে এই অনাস্থার ব্যাপারটা ‘ইউনিভার্সেল’। সৌমেন তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলে- “ ইউনিভারসেল মাই ফুট। বিদেশে একটা কিছু চলছে সেটারই অনুকরণে এখানে কিছু চলছে। ওরাও করছে আমরাও করছি।” তখন শ্যামলেন্দু দেশভাগের আগের ও দেশভাগের পরের ছাত্রনেতাদের মধ্যে পার্থক্য দেখাতে চায়, কিন্তু সে যুববিদ্রোহের পক্ষে কথা বলছে কি না তা আর জানা যায় না।
সীমাবদ্ধ ছবিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ভোগসর্বস্ব, স্বার্থপর এক পরিবারকে দেখানো হয়েছে। এই ধরনের পরিবারের অস্তিত্ব কলকাতা শহরে ছিল, যেখানে বাইরে গুলি, বোমার শব্দেও এদের ব্যক্তিগত সুখের নিভৃতিটুকুতে কোনো ছেদ পড়ত না। কারখানার শ্রমিক ও শ্রমিকনেতাদের বিদ্রোহ ছাড়া এখানে আর কোনো বিদ্রোহ দেখানো হয় নি। এইটুকুর বাইরে তৎকালীন রাজনীতির ছিটেফোঁটাও এই ছবিতে নেই, টুটুলের বিপ্লবী প্রেমিকের কথা নাম ছাড়াই উল্লেখিত হয়েছে মাত্র।
জন অরণ্য (১৯৭৫) ছবির নায়ক সোমনাথ ব্যানার্জি, চরিত্রটি অভিনয় করেছেন প্রদীপ মুখোপাধ্যায়। এই ছবিরও কাহিনিলেখক শংকর। অন্য দুটি ছবির তুলনায় এই ছবিতে অন্তত নকশাল আন্দোলনের কর্মীদের ক্রিয়াকলাপের টুকরো ছবি দেখতে পাওয়া যায়, যদিও তা একটু নঞর্থকভাবেই দেখিয়েছেন পরিচালক। ছবি শুরু হয় একটি পরীক্ষাকেন্দ্রের দৃশ্য দিয়ে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক স্তরের ইতিহাস পরীক্ষা। সেই পরীক্ষাকেন্দ্রের বাইরের দেওয়ালে নানা নকশালপন্থী স্লোগান লেখা থাকে- সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করো, সশস্ত্র বিপ্লবই সর্বহারাদের একমাত্র পথ, শ্রেণিশত্রু খতম করো ইত্যাদি। এদিকে কেন্দ্রের ভিতরে পরীক্ষার নামে চলতে থাকে গণটোকাটুকি। প্রচলিত পরীক্ষাব্যবস্থাকে নকশালপন্থীরা অস্বীকার করেছে, টোকাটুকি, প্রশ্ন ফাঁসের ঘটনাও ঘটেছে। কিন্তু অতিবামপন্থী মতাদর্শের সারবত্তাকে, সিস্টেমকে না মানার পিছনে প্রতিষ্ঠান বা রাষ্ট্রবিরোধিতার তত্ত্বকে ব্যাখ্যা না করে শুধুমাত্র তাদের টোকাটুকির বিষয়টিকে দিয়ে সিনেমা শুরু করায় এই আন্দোলন সম্পর্কে পরিচালকের উদাসীনতা শুধু নয়, নেতিবাচক মনোভাবটিই ধরা পড়ে। বরং তাঁর সহানুভূতি থাকে সেই চরিত্রটির প্রতি, যে এই অবস্থাতেও সৎভাবে পরীক্ষা দিয়ে পরীক্ষকের দৃষ্টিক্ষীণতার কারণে গড় নম্বর পায়। সেই চরিত্রটিই গল্পের নায়ক সোমনাথ, সোমনাথের বেকারত্ব এবং তা থেকে উত্তরণ এই ছবির বিষয়। সত্যজিৎ দেখান, বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে চাকরি করার গতানুগতিক পন্থা ছেড়ে সোমনাথ ব্যবসার পথ ধরে, বাড়িতে অনুমতি পেতে তার অসুবিধা হয় না। পূর্বপরিচিত বিশুদার পরামর্শে ও সহযোগিতায় সে দালালির ব্যবসা শুরু করে, লাভের মুখ দেখে। একসময়ে সে একটি বড়ো বরাত পাবার জন্য সে বন্ধু সুকুমারের বোন কণাকে ব্যবহার করে, কণা তখন সবে দেহব্যবসার কাজে নেমেছে পরিবারের অনটন সামাল দিতে।

এই ছবিতে দালালির ব্যবসায় নামার আগে বড়োবাজারের রাস্তায় কলার খোসায় পা লেগে সোমনাথের পড়ে যাবার ঘটনাটি ‘সিম্বলিক’। সোমনাথের নৈতিক অবনমন ঐ পতনের দ্বারা প্রতীকায়িত হয়। টাকার চাহিদা, ভবিষ্যৎকে সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সোমনাথ যখন নৈতিক পতনের শেষ ধাপটিতে পৌঁছায়, ভগিনীসমা কণাকে অন্যের হাতে তুলে দিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করে, তখন তার বাড়িতে বাজে রবীন্দ্রনাথের গান- ছায়া ঘনাইছে বনে বনে। মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ শুধু নয়, মানবিক নীতিবোধেও ঘন ছায়া পড়ে, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। সিদ্ধার্থের মতো সোমনাথের তেমন দ্বন্দ্ব নেই, কণাকে হোটেলের নির্দিষ্ট রুমে পৌঁছে দেবার আগে সামান্য জড়তা ও মৃদু আপত্তি ছাড়া তার মধ্যে আর কিছু খুঁজে পাওয়া যায় না। আমাদের প্রশ্ন জাগে, কণা যদি পূর্বপরিচিত না হতো, তাহলে কি তার মধ্যে সামান্যতম বিচলনও ঘটত? যদি মিসেস গাঙ্গুলি বা বিধবা মহিলাটির কনিষ্ঠা কন্যাটি, যারা অর্থের প্রয়োজনে দেহব্যবসায় নামতে বাধ্য হয়েছেন অথচ সমাজে ভদ্র গৃহস্থের পরিচিতিটুকু ছাড়তে পারেন নি, তারা যদি কণার জায়গায় থাকতেন, তাহলে মনে হয় না সোমনাথের কোনোরকম কুণ্ঠা দেখা যেত। আসলে এই ছবিতেও সত্যজিতের লক্ষ্য সমকালীন রাজনীতির চিত্রায়ণ নয়, বরং সেই প্রেক্ষাপটে বেকারত্ব ও মধ্যবিত্ত সংস্কারের গলিঘুঁজিকে তুলে ধরা। দালালি করে অল্প সময়ে বড়োলোক হবার হাতছানির বিপ্রতীপে তিনি উপস্থিত করেন সৎ রোজগারের পথে যাওয়া পরিশ্রমী সুকুমারকে, অথচ সেই পরিবারেরই মেয়ে কণা যেন সোমনাথেরই এক নারী সংস্করণ- সহজে উঁচুতে ওঠার সিঁড়ি হিসাবে সে ব্যবহার করে নিজের শরীর। মিসেস গাঙ্গুলি, নিজের মেয়েদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা বিধবা মহিলাটি সেই ভোগসর্বস্ব শ্রেণিরই প্রতিনিধিত্ব করছে।
এই ছবিতে আর একটি চরিত্র উল্লেখযোগ্য- তিনি হলেন সোমনাথের বাবা। তিনি একসময়ে কংগ্রেস করতেন। গোটা সিনেমায় কেবল এই চরিত্রের ভিতরই দ্বন্দ্ব দেখান সত্যজিৎ, অন্য সকল চরিত্রই একমাত্রিক- হয় আদর্শবাদী নয়তো খুব সোজা সরল, আর তা না হলে ভোগলিপ্সু। সুকুমার, সোমনাথের বৌদিদি প্রথম দলের, দ্বিতীয় দলে অন্যেরা। সোমনাথের বাবা চরিত্রটি যেন প্রতিদ্বন্দ্বীর সিদ্ধার্থ, ছেলের স্নাতক পরীক্ষার ফল নিয়ে তিনি হতাশ, পিতা হিসাবে সেটা স্বাভাবিকও। কিন্তু তিনি যখন বিপ্লবের কথা বলেন এবং সেই বিপ্লবের পিছনে কোনো আদর্শগত চাপ থাকে না, থাকে হতাশাজনিত ক্রোধ, তখন তাঁর মধ্যে আমরা সিদ্ধার্থর প্রতিফলন দেখতে পাই। তাঁর বৌমা, বড়ো ছেলে ভোম্বলের স্ত্রী যখন জিজ্ঞাসা করে যে তাঁর ছেলেরা বিপ্লবী রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ুক তিনি চান কি না, তখন তিনি বলেন যে ছেলের প্রাণসংশয় হতে পারে, এমন কাজে তিনি কী করেই বা সায় দেবেন। তাঁর এই কথা থেকে স্পষ্ট যে, সোমনাথ যদি ভোম্বলের মতো ভালো রেজাল্ট করে চাকরি বাকরি পেয়ে সংসারে থিতু হত, তাহলে তিনি বিপ্লবের কথা ভাবতেন না। তাঁর মতে, ছেলেরা হয় বিপ্লব করছে, নয়তো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ নকশাল আন্দোলনের পিছনে যে আদর্শ কাজ করেছে, তা তাঁর বোধগম্য হয় নি। এখানেও যেন সীমাবদ্ধ ছবির জনৈক চরিত্রের মতো তাঁরও মনে হয়েছে, ছেলেপুলেরা চাকরি বাকরি পায় নি বলেই বিপ্লব করছে, যেন বেকার সমস্যাই এই আন্দোলনের মুখ্য কারণ। অন্য সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের মতো তিনিও চান, তাঁর হয়ে বিপ্লবটা কেউ করে দিক, তিনি এবং তাঁর শ্রেণির মানুষেরা সুফলটুকু ভোগ করবেন শুধু। বেকার সোমনাথের জন্য যখন সম্বন্ধ আসে এই শর্তে যে, বিয়ের পর শ্বশুর জামাইকে তাঁর সিমেন্টের ব্যবসার অংশীদার করে নেবেন, তখন সেই প্রস্তাবটিও মনে ধরে তাঁর। ছেলের জন্য যেভাবে হোক নিরাপদ ভবিষ্যৎ কাম্য তাঁর।
উপরে আলোচিত তিনটি ছবিকে সত্যজিতের রাজনৈতিক ট্রিলজি বলা হয়, যদিও সত্তরের রাজনীতির ছিটেফোঁটাই তাঁর ছবিতে এসেছে। নকশাল আন্দোলনের টুকরো টুকরো নিদর্শন তিনটি ছবিতেই এসেছে ব্যাকড্রপের মতো, কখনো চরিত্রদের বাক্যালাপের বিষয় রূপে। কিন্তু তাঁর চরিত্রদের কেউই এই আন্দোলন নিয়ে, তার আদর্শগত অবস্থান নিয়ে মনোযোগী নয়, তাদের ব্যক্তিগত জীবনে একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বীর বুলু ছাড়া এই আন্দোলনের সঙ্গে কারো কোনো প্রত্যক্ষ যোগ নেই। সেখানেও বুলু পার্শ্বচরিত্র, এবং অদ্ভুতভাবে, চরিত্রগুলি পরস্পরের আপনজন হওয়া সত্ত্বেও তারা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো অবস্থান করে। কেউ কারো ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে বিশেষ আগ্রহী নয়, আগ্রহী হলেও সেখানে তাদের কোনো ভূমিকা গ্রহণ করতে দেওয়া হয় না। প্রতিদ্বন্দ্বীতে সিদ্ধার্থের স্বপ্নে আমরা বুলুর মৃত্যু দেখি, সেখানে গুলি করে তাকে হত্যার দৃশ্যটি নেগেটিভ ইমেজে ফুটিয়ে তোলা হয়। আমরা বুঝি, বুলুর ভবিষ্যৎ নিয়ে দাদা সিদ্ধার্থ চিন্তিত, কিন্তু নকশাল আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে যাওয়া মানেই তার পরিণতি মৃত্যু- এইরকম একটা সরল সমীকরণ পরিচালক সিদ্ধার্থের বয়ানে দেখাতে চান, আমাদের ধারণা সত্যজিতেরও তেমনই মত এবং শুধু সত্যজিৎ নয়, সমকালীন বেশ কয়েকজন স্বনামধন্য সাহিত্যিকও তাঁদের গল্পে-উপন্যাসে এই মৃত্যুগত পরিণতিকে চিহ্নিত করে কোথাও যেন যুবসমাজের প্রতি এক সাবধানবাণী দিতে চেয়েছেন।
রাজনীতি সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন সত্যজিৎ। তার চেয়ে আগ্রহী ছিলেন ব্যক্তিমনস্তত্ত্বের চিত্রায়ণে, ব্যক্তির দ্বন্দ্ব, তার হতাশা, আত্মবিশ্বাস, ক্লান্তি, স্ববিরোধ,উচ্ছ্বাস, নীতিহীনতা ইত্যাদির বিচিত্র মার্গে তাঁর স্বচ্ছন্দ যাত্রা। কিন্তু, ব্যক্তির সঙ্গে তার সমাজবাস্তবতাকে, ব্যক্তির সমষ্টিগত অবস্থানকে দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের মাধ্যমে তুলে ধরার ক্ষেত্রে পরিচালক সত্যজিতের অনীহা ছিল। তিনি বেকারত্বের সমস্যাকে অত্যন্ত বিশ্বাসযোগ্যতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন, একটি শ্রেণির স্বধর্মচ্যুতির সঙ্গে তার হঠাৎ আমদানি হওয়া ভোগাকাঙ্ক্ষাকে চিত্রায়িত করেছেন, কিন্তু সমস্যাগুলির মূলগত কারণকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস তাঁর সিনেমায় দেখা যায় না। নকশাল রাজনীতিকে তিনি সামান্য কয়েকটি দৃশ্যগত ও শব্দগত ফ্রেমে ঠাঁই দিয়েছেন, কিন্তু সমকালীন এই আন্দোলন- যার সম্পর্কে কলকাতার ভিতরে বাইরে ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, তার আদর্শকে কখনো মনোযোগ দিয়ে বোঝার চেষ্টা করেন নি তিনি। রাজনীতিবিদ্ বা নেতাকে তিনি এঁকেছেন প্রায় কমেডিয়ান করে, অথচ আদর্শহীন বিভ্রান্ত সময়ে দাঁড়িয়ে চিন্তাশীল মানুষের দার্শনিক ভিত্তি কী হবে বা হতে পারে, সে সম্পর্কে কোনো মতামতও তিনি দিতে চান নি। রাজনৈতিক ট্রিলজি হলেও উক্ত ছবিগুলিতে আমরা কোনো রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা পাই না, ব্যক্তিমানুষের জীবনজিজ্ঞাসাকে তিনি তার সমাজবাস্তবতার সঙ্গে যুক্ত করেন না। তবু নকশাল রাজনীতিকে চলচ্চিত্রে স্থান দেবার যে টেকনিকাল অসুবিধাগুলি ছিল, সে কথা আমরা আগেই আলোচনা করেছি যেহেতু, সেহেতু সত্যজিতের পক্ষেও যে সিনেমায় নকশাল রাজনীতির পক্ষে কথা বলার জায়গা ছিল না, সেটা মেনে নিতে হবে। তবে সিনেমার মতো দৃশ্যমাধ্যমের যেখানে শক্তি অনেক, চিত্রকল্প, সঙ্গীত ও শব্দব্যবহারের কৌশলে পরিচালকের রাজনৈতিক বক্তব্য যে একেবারে দেওয়া যায় না- তেমনটাও নয়। সত্যজিতের শিল্পীসত্তা আসলে তাঁর স্বভাবগতভাবেই রাজনীতিবিমুখ, উদারপন্থী ব্যক্তিবাদে তিনি বিশ্বাসী। ফলে রাজনীতি তাঁর ছবিতে বহুবিচিত্র বিষয়ের মধ্যে একটি-এই পর্যন্তই। গভীর রাজনৈতিক জিজ্ঞাসা যেহেতু তাঁর কোনো ছবিতেই নেই, সত্তরের উত্তাল পরিবেশেও তিনি ব্যক্তিগতভাবে যেখানে ছবি, টাইপোগ্রাফি, বিজ্ঞাপনজগৎ নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, সেহেতু নকশাল রাজনীতি তাঁর সিনেমায় ব্যাকড্রপের বেশি গুরুত্ব পায় না, এই কথা মেনে নিতেই হয়।
মৃণাল সেন স্বঘোষিত বামপন্থী।
“যখন ফরিদপুরে ছিলাম তখনই আমি সেখানে বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনের দিকে ঝুঁকেছি। সেই তখনই আমি একবার ফ্রাঙ্কো বিরোধী মিছিলে শ্লোগান দিয়েছি।”২
সুতরাং তাঁর ছবিতে সমাজবাস্তবতা থাকবে, তা প্রত্যাশিত। চলচ্চিত্রবিদ্ সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় সত্যজিৎ রায়ের সমকালীনতা অতিক্রমী সৌন্দর্যবোধ, ঋত্বিক ঘটকের উদ্বাস্তু সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে পুরাণ ও সাম্প্রতিকতার বিস্ময়কর মেলবন্ধনের সঙ্গে মৃণাল সেনের পরিচালিত ছবিগুলির তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেন,
“মৃণাল সেনের প্রধান গুণ বা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল মৃণাল এই পথের অনুসারী নন। তাঁর কাছে দৈনন্দিনতাই মুখ্য।”৩
এই প্রসঙ্গে তিনি ইতালির নিওক্লাসিকাল ফিল্ম এবং ফরাসি সিনেমার নবতরঙ্গ আন্দোলনের কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে, মৃণাল সেনের সিনেমায় এই দুইয়ের প্রভাব রয়েছে- ভাবনা ও আঙ্গিক দুই দিক থেকেই।
অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় বলেন,
“মৃণাল সেনকে আমরা যখন সত্তর দশকে আবিষ্কার করি, তখন আমরা আবিষ্কার করেছিলাম প্রতিবাদের ইস্তাহারলেখক হিসাবে। ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১, পদাতিক- এই যে তিনটে ছবি, যদি একে সত্যজিৎ রায়ের তিনটে ছবির সঙ্গে তুলনা করি- প্রতিদ্বন্দ্বী, সীমাবদ্ধ এবং জন অরণ্য একই সময়ে তোলা, যদি একে ঋত্বিক ঘটকের যুক্তি, তক্কো আর গপ্পোর সঙ্গে তুলনা করি ১৯৭৪ সাল, তাহলে আমরা আবারও দেখব যে, মৃণালের বৈশিষ্ট্য তিনি সারফেস লেয়ার, ভূমিতল থেকে রাজনৈতিক যে উচ্চারণ, তাকে উদ্ধার করেন এবং আমরা ১৯৬৯ সালে যে তাঁকে এতো প্রিয় ভেবেছিলাম তার মূল কারণই হল, তিনি যখন ম্যানিকুইনের হাত থেকে পোষাক ছিঁড়ে নিলেন, তখন আমরা বুঝতে পারলাম যে আসলে তিনি বলতে চাইছেন সাম্রাজ্যবাদ কাগজের বাঘ, তার অন্তরে সে নগ্ন এবং নপুংসক। তার কোনো জননেন্দ্রিয় নেই। এই যে যুবকের ক্রোধ, এই যে সামগ্রিকভাবে কলকাতা শহরের ঔপনিবেশিক স্মৃতিকে চ্যালেঞ্জ জানানোর জন্য তাঁর চলচ্চিত্রে যে চেষ্টা, যেটা বাইরে, খোলা মাঠে, বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর, জনজীবনের আড্ডায় প্রতিফলিত হয়ে যাচ্ছে, যা জনজীবনে আলোচিত হচ্ছে, তাকেই মৃণাল সেন কলকাতা ৭১ এ দেখাতে চাইছেন অনন্তকাল ধরে-একবার সমরেশ বসুর গল্পে, একবার প্রবোধ সান্যালের গল্পে, একবার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে।”৪
মধ্যবিত্তের উত্থানপতন মৃণালের সিনেমাতেও আসে, কিন্তু তা আসে অর্থনৈতিক বাস্তবতার সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে। তাঁর সিনেমাকে অনেকটাই সাংবাদিকতাধর্মী মনে হলেও কোনো প্রচারধর্মিতা একেবারেই থাকে না। আমরা লক্ষ করি, সিনেমায় গল্প বলার ঝোঁক তাঁর কম, তার চেয়ে একটি বিশেষ পরিস্থিতি বা ভাবকে ফোটানোই তাঁর উদ্দেশ্য হয়ে ওঠে। দু-একটি ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। কিন্তু নিওক্লাসিকাল সিনেমার ধরণে অল্প বাজেটের ছবি তিনি করেন, সেই ছবিতে নিয়ে আসেন সিনেমা-বহির্ভূত জনসাধারণের অংশগ্রহণ, নায়কচরিত্রে অচেনা মুখ। ‘ফ্রিজড শট’, ‘জাম্পকাট’, ‘ট্র্যাকিং শট’, ‘লং শট’ থেকে ‘ক্লোজ শটে’র দিকে ক্যামেরার চলন ইত্যাদি প্রকৌশলে তিনি তুলে আনেন বিশেষ মুহূর্তের মহিমা, নবতরঙ্গের ‘ফ্রিজড শটে’র টেকনিক চলচ্ছবির কোনো একটি মুহূর্তকে বর্তমান কালেই স্তব্ধ করে রাখে, বোঝা যায় পরিচালক ঐ বিশেষ মুহূর্তটিকে আলাদা করে গুরুত্ব দিচ্ছেন। পদাতিক ছবির একেবারে শেষ দৃশ্যে ক্যামেরা যখন সুমিতের মুখের উপর এভাবেই স্তব্ধ হয়ে যায়, আমরা বুঝতে পারি তার বাবার বলা ‘বি ব্রেভ’- এই শব্দে তার আনন্দ, উচ্ছ্বাস ও এই সিনেমার প্রবল ইতিবাচকতার মুহূর্তটিকে মৃণাল শেষ হতে দিতে চাইছেন না। হয়তো এই শটেই তুলে ধরতে চাইছেন কথকেরও অর্থাৎ পরিচালকেরও রাজনৈতিক বক্তব্যটিকে।
এই অধ্যায়ে আমরা মৃণাল সেনের তিনটি ছবিকে আলোচনার জন্য বেছে নিয়েছি- ইন্টারভিউ, কলকাতা ৭১ এবং পদাতিক। সত্যজিতের রাজনৈতিক ট্রিলজির থেকে এই তিনটি ছবি মেজাজে ও বক্তব্যে সম্পূর্ণ আলাদা। সত্যজিৎ যেখানে সত্তরের রাজনৈতিক পটভূমিতে মধ্যবিত্তের বিচ্ছিন্নতাবোধ, তার দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, পলায়নী মনোভাবকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ করেছিলেন, ব্যক্তিমনস্তত্ত্বের উপর আলো ফেলে সেই বিচ্ছিন্নতাকে সৌন্দর্যের পৃথিবীতে স্থাপন করেছিলেন, মৃণাল সেন তা করেন নি। নান্দনিকতার চাইতে প্রতিদিনের এবং প্রতিমুহূর্তের কলকাতার মর্ষতা ও উচ্ছ্বাসকে রিপোর্টাজের ভঙ্গিতে নিরপেক্ষ ও নির্লিপ্তভাবে তুলে ধরাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। পদাতিকে তাও একটি বৃত্তায়িত গল্প পাওয়া যায়, অন্যগুলির বেলা শুধুই গল্পসূত্র। তাঁর সিনেমা সম্পর্কে সাহিত্যিক বাণী বসু মন্তব্য করেছেন-
“মৃণাল সেন একেবারেই গল্প বলতে চান না। তাঁর অনেক ছবিই প্রবন্ধ কিম্বা উঁচুমানের সাংবাদিকতা (কলকাতা ৭১, আকালের সন্ধানে)। যে সব সাহিত্য-গল্প নিয়ে তিনি ছবি করেছেন- ভুবন সোম, খণ্ডহর,একদিনপ্রতিদিন, একদিন অচানক প্রত্যেকটিই মানুষকে টেনেছে। কিন্তু ভুবন সোম ও খণ্ডহর ছাড়া অন্যগুলিতে নান্দনিক উদ্দেশ্য অনেকটাই গৌণ হয়ে গেছে। গল্পের নির্বাচনে আমাদের কতকগুলি জ্বলন্ত সামাজিক বা চারিত্রিক প্রসঙ্গের ওপর ফোকাস থাকে। আর ঘনত্ব এতটাই যে দেখতে দেখতে আমাদের দম বন্ধ হয়ে আসে। উৎকণ্ঠায়, কষ্টে, প্রতিবাদে। এটাই তাঁর অভীষ্ট। তিনি চলচ্চিত্রকে সামাজিক-রাজনৈতিক অন্যায়ের দর্পণ ও প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেন যদিও তার মধ্যে একদেশদর্শিতা বা প্রচারমুখিনতা থাকে না।”৫
মৃণাল সেনের ইন্টারভিউ ছবিটি (সাদাকালো, ৩৫ মিমি, ৮৭ মিনিট) মুক্তি পায় ১৯৭০-এ। মৃণাল সেন প্রোডাকশন্সের ব্যানারে এই ছবির কাহিনি লেখেন আশিস বর্মন, চিত্রনাট্য ও পরিচালনা মৃণাল সেন। চিত্রগ্রাহক-কে.কে. মহাজন, অভিনয়ে রঞ্জিত মল্লিক, করুণা বন্দ্যোপাধ্যায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, আলি নো মারিস, এম.সুব্রহ্মণ্যম, মমতা চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। কেন্দ্রিয় চরিত্র রঞ্জিতের জীবনের একদিনের ঘটনা নিয়ে এই ছবি। এক পারিবারিক শুভাকাঙ্ক্ষী মারফত রঞ্জিত এক বহুজাতিক সংস্থায় ইন্টারভিউয়ের ডাক পায়। ইন্টারভিউতে উপস্থিত হলেই চাকরিটা তার হয়ে যাবে, এইরকমই কথা ছিল। ঐ দিন সকালে চুল কাটতে গিয়ে সেলুনে লম্বা লাইন দেখে সে ফিরে আসে, তার একমাত্র স্যুটটি ছিল লন্ড্রিতে, বন্ধুর থেকে ধার নেওয়া স্যুটটি সে বাসে পকেটমার ধরতে গিয়ে ফেলে আসে এবং শেষে ধুতি পাঞ্জাবি পরে ইন্টারভিউ দিতে যায়। চাকরি তার হয় না। সে ক্ষোভে ফেটে পড়ে।

এই ছবিতে পরিচালক দেখাতে চান যে, স্বাধীনতার পর এতগুলি বছর কেটে গেলেও ঔপনিবেশিকতা থেকে আমাদের মুক্তি ঘটে নি। মৃণাল সেন দেখান ঔপনিবেশিক ইতিহাসের ধারক শহর কলকাতাকে।
এই ছবিটি সম্পূর্ণভাবেই নিওরিয়ালিস্টিক। ছবির নায়ক রঞ্জিত মল্লিক স্বনামেই উপস্থিত, সমস্ত ছবিটিই এমনভাবে দেখানো হয় যেন সবকিছুই বাস্তবে ঘটছে, এমনকি শুটিং দেখতে আসা জনগণও এই সিনেমার অংশ হয়ে ওঠে। স্বয়ং পরিচালক এর ইতিহাস বলতে গিয়ে জানান,
রঞ্জিত সত্যিই ট্রামে ওঠেন, যেখানে এক ভদ্রমহিলার হাতের ফিল্ম ম্যাগাজিনে মৃণাল সেনের নতুন নায়ক হিসাবে তাঁর ছবি ছাপা হয়েছে। সন্দিগ্ধ ও উৎসুক জনতাকে তখন রঞ্জিত বলেন- “আমার নাম রঞ্জিত মল্লিক। আমি ভবানীপুরে থাকি। একটি সাপ্তাহিকে কাজ করি। আমি প্রেসে যাই, প্রুফ দেখি এবং কিছু বিচিত্র কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকি। তেমন বিশেষ কোনও ঘটনা আমার জীবনে নেই। যে কোনও কারণেই হোক মৃণাল সেনের আমাকে পছন্দ হয়েছে। উনি বলেছিলেন, ভোর থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত উনি আমার পেছনে ছুটবেন। আমাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবেন। একটা দিনের জন্য। দেখুন ওদিকে কে কে মহাজন তাঁর ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে। বলুন তো এসবের কোনও মানে হয়!৬
স্বয়ং পরিচালক এই ছবির গঠন সম্পর্কে ফ্যাক্ট, ফিকশন এবং ফ্যান্টাসি- এই তিনটি শব্দ ব্যবহার করেছেন-
“সেই বহুজাতিক কোম্পানিতে নায়কের ইন্টারভিউ হয়ে যাওয়ার পর ছবির চারিদিকেই যেন আরও একটা ইন্টারভিউ। একজন, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছবির নায়ককে তাড়া করে ফিরছে, যার গলাই শুধু শোনা যাচ্ছে, যাকে দেখা যাচ্ছে না, সেই মানুষটিই ছবির শেষে ইন্টারভিউ করে নায়ককে। শেষ পর্যন্ত ছবিটা ভয়ংকর একটা মোড় নেয়, যাকে এক কথায় বলা যায় ফ্যাক্ট-ফিকশন-ফ্যান্টাসি।”৭
নকশাল আন্দোলনের কথা প্রত্যক্ষ ভাবে না এলেও যুবসমাজের হতাশা, সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের বিপক্ষে, গোটা সিস্টেমের বিরুদ্ধে ফেটে পড়া ক্ষোভ এই ছবির মুখ্য বিষয়। অথচ সিনেমার শুরুর দিকে চলমান কলকাতার দারিদ্র্য, অনাহারের ছবি সকলের, এমনকি নায়কের চোখে পড়লেও সে এই ব্যাপারে উদাসীনই থেকেছিল, তার ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ তৎকালীন যুবসমাজের ক্ষোভের সঙ্গে একীভূত হয় সিনেমার শেষে, তখন ব্যক্তি আর ব্যক্তি থাকে না, হয়ে যায় সমষ্টির প্রতিনিধি। সত্তরের উত্তাল সময় নিয়ে ছবি করার কথা ভেবেছিলেন মৃণালসহ তাঁর ইউনিটের লোকজনেরাও, সেই সময়ের সমাজবাস্তবতাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তির মনস্তত্ত্ব নিয়ে কাজ করার মতো রাজনীতিবিমুখ ঔদাসীন্য মৃণাল সেনের মতো বামপন্থী শিল্পী দেখাতে পারেন নি-
রাজনৈতিক সংগ্রামে ১৯৬৭ সালের সেই সময়টা উত্তরবঙ্গের সেই অভূতপূর্ব অগ্নিঝড় সমগ্র দেশে ছড়িয়ে গেল। কৃষি উৎপাদনের জায়গায় চাষি, ভাগচাষির যেখানে অর্থের সংস্থান হয়, সেখানে শুরু হয়ে গেল নকশাল আন্দোলন। ... সেই দশক ছিল প্রতিবাদের দশক। প্রতিবাদের ভাষা ছিল হিংসা।”৮
তাঁর জীবন অভিজ্ঞতা দিয়ে মৃণাল সেনের মনে হয়েছে, নকশাল আন্দোলনের চারিত্রটি নাগরিক, যদিও এই আন্দোলনের সূচনা গ্রামবাংলার কৃষকের বিক্ষোভ থেকে-
“ঠিক বা বেঠিক যাই হোক না কেন এ আন্দোলন শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেল। অর্থাৎ চারিত্র্যটা তার নাগরিকই রয়ে গেল।”৯
এই নাগরিকতা, বিশেষ করে ঔপনিবেশিক শহর কলকাতার নাগরিকতা এবং সেই নাগরিকতার ভিতরকার যাবতীয় মর্ষতা, মালিন্য, দারিদ্র্য, হতাশা, ক্ষোভ, সৌন্দর্যহীনতার ভিতরেও শহরের চলমান মুহূর্তগুলো ক্যামেরায় ধরেছেন পরিচালক তাঁর কলকাতা ট্রিলজির দ্বিতীয় ছবি কলকাতা ৭১-এ।

একটি কুড়ি বছরের ছেলে, যে হাজার বছর ধরে দারিদ্র্য,বঞ্চনা, শোষণের ইতিহাসের সাক্ষী, তারই বয়ান দিয়ে ছবিটি শুরু হয়। আমরা দেখি, হাজার বছর ধরে পথ চলার জীবনানন্দীয় রোমান্টিকতা ছেড়ে সত্তর দশকের ছবি কীভাবে গুলিবিদ্ধ হওয়া রক্তাক্ত যুবকের ভাষ্যে শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা করে, পরিচালক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে এই ছেলেটিকে সেই দশকের বাংলার সমস্ত পরিবার চিনে থাকবে, সে কারো সন্তান, কারো ভাই। ছবির শুরুতে স্ক্রিনে ভেসে ওঠে কবিতার ছত্রের মতো কয়েকটি লাইন-
আমার বয়স কুড়ি
কুড়ি বছর বয়স নিয়ে
আমি আজও হেঁটে চলেছি
হাজার বছর ধরে
দারিদ্র্য
মালিন্য
আর
মৃত্যুর ভিড় ঠেলে
আমি পায়ে পায়ে চলেছি
হাজার বছর ধরে
হাজার বছর ধরে
দেখছি
ইতিহাস
দারিদ্র্যের ইতিহাস
বঞ্চনার ইতিহাস
শোষণের ইতিহাস
সংবাদপাঠকের গম্ভীর কণ্ঠস্বরে এরপর শোনা যায় গুলিবিদ্ধ হয়ে একটি কুড়ি বছরের ছেলের মৃত্যুর কাহিনি। সরু গলি থেকে বড়ো রাস্তা, ভিড় রাস্তা, গ্রাম থেকে অরণ্য, সমুদ্রের ধার থেকে ভোরের কুয়াশা ঢাকা পার্কের ভিতর পর্যন্ত পৌঁছে হঠাৎ গুলির শব্দে শুরু হয়ে যায় মানুষ মারার ইতিহাস, এরপর গুলির শব্দে একঝাঁক পাখির উড়ে যাওয়ার দৃশ্য।
তিন, চার এবং পাঁচের দশকের কালপটভূমিতে যথাক্রমে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রবোধকুমার সান্যাল এবং সমরেশ বসুর কাহিনি অবলম্বন করে কেবলমাত্র একদিনের গল্প সাজিয়ে দিয়েছেন পরিচালক। সেই তিনটি কাহিনির মধ্যে নকশাল আন্দোলনের কোনো চিহ্ন নেই, আছে নিদারুণ দারিদ্র্যের কাহিনি। প্রথম গল্পে এক ভয়ংকর বৃষ্টির রাতে এক হতদরিদ্র পরিবারের আশ্রয়হীনতার কাহিনি, পরিচালক তীক্ষ্ণ সংলাপে দেখাতে চান আর্থিক অস্বাচ্ছন্দ্য কীভাবে একই পরিবারের সদস্যদের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা সৃষ্টি করে, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায় অভিনীত বাবা চরিত্রটি সংসারের মানুষগুলির মুখে অন্ন তুলে দিতে না পেরে নিজের প্রতিই অসম্ভব ঘৃণার বশে উন্মাদপ্রায় হয়ে যায়, কখনো সে লাঠি নিয়ে কুকুরের দিকে তেড়ে যায়, কখনো ঘরের চাল ফুটো হওয়া বৃষ্টির জল গায়ে মাখে। দ্বিতীয় গল্পে এই আর্থিক কারণেই পারিবারিক সম্পর্কগুলির কুশ্রীতা আরো প্রকট। ব্ল্যাক আউটের দিনে অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালে শোভনাদের পরিবার নিজেদের পুরনো বাসা ছেড়ে ঊঠে আসে দয়া করে থাকতে দেওয়া এক ভদ্রলোকের বাড়ির একটি ঘরে, কিন্তু সেখানকার পরিবেশ যে ভদ্র পরিবারের বসবাসের উপযুক্ত না, সেই কথা টের পেয়ে যায় দিল্লি থেকে আসা সরকারি চাকুরে শোভনার মামাতো দাদা নলিনাক্ষ। তার মধ্যবিত্ত দৃষ্টিতেই এই পরিবারটির সার্বিক শ্রীহীনতা দৃষ্ট হয়, যেখানে বাড়ির ছোটো ছেলে হারু পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে চায়ের দোকানে বাসন ধোয়, বিনিময়ে তার খাওয়া জোটে, শোভনা সামান্য একটা কাজ করে আর ছোটো বোন মিনুকে তার মা নানা ছুতোয় ওপরতলার মেসে পাঠায় যেখানে লোভী পুরুষমানুষের বাস। গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য নিজেদের শ্রেণিগত মূল্যবোধকে বিসর্জন দেওয়া এই পরিবারটির অসহায়তা, অথচ বাইরের লোকের কাছে আব্রু রক্ষা করার ব্যর্থ চেষ্টা নলিনাক্ষকে আর সেখানে দাঁড়াতে দেয় না, সে ব্ল্যাক আউটের দোহাই দিয়ে প্রায় পালিয়ে যায়। এই বাড়ির বড়ো ছেলে পরিবারের এই নীতিহীন অবনমন দেখতে না পেরে বাড়িছাড়া। তৃতীয় গল্পে গ্রাম-মফঃস্বলের কয়েকটি কিশোর ফুটবল খেলা ছেড়ে রুটিরুজির জন্য ট্রেন থেকে চালের বস্তা চুরি করে, নেশা, গালিগালাজ, চটুল রসিকতায় তারা বয়সোচিত সারল্য হারায়। অন্যদিকে এক ব্ল্যাক মার্কেটিয়ার হঠাৎ বড়োলোক হয়ে নিজের বিত্তবৈভব প্রকাশ করে, মাঝে মাঝে পার্টি দেয় এবং সেখানে অনাহারী মানুষদের জন্য ছদ্ম সহানুভূতি প্রকাশ করে। আকালে, মন্বন্তরে মৃতপ্রায় মা ও শিশুর স্কেচ তার ডাইনিং রুমের শোভা বর্ধন করে। প্রথম গল্পের নিদারুণ দারিদ্র্য, দ্বিতীয় গল্পে দারিদ্র্যের কারণে শ্রেণিচ্যুতি ও মধ্যবিত্ত মূল্যবোধের অবনমন এবং তৃতীয় গল্পে আর্থসামাজিক বৈপরীত্যের সঙ্গে হঠাৎ বড়োলোক শ্রেণির চূড়ান্ত নীতিহীনতা ও ‘হিপোক্র্যাসি’- এই তিনটি বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে কুড়ি বছরের মৃত ছেলেটি। সিনেমার শেষে ফ্ল্যাশব্যাকের মতো তিনটি কাহিনি থেকেই অংশবিশেষ তুলে এনে একটি কোলাজের মতো উপস্থাপন করা হয় এবং কালো পর্দায় কথকের মতো মৃত ছেলেটির মুখের ক্লোজ আপ বসিয়ে তাকে দিয়ে কিছু কথা বলানো হয়। সে এই দারিদ্র্য, মালিন্য, শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাসের সাক্ষী এবং এই ইতিহাসকে অস্বীকার করতে চেয়ে একদিন ভোরের বেলা, যখন আকাশবাণীর প্রথম অধিবেশন বসে, ততোটাই ভোরের বেলা একটি পার্কের ভিতর রাষ্ট্রযন্ত্রের গুলির আঘাতে সে প্রাণ দেয়। নকশাল আন্দোলন এই ছবিতে সরাসরি না এলেও প্রচলিত সিস্টেমকে ভেঙে দিতে গিয়ে শহিদ হবার ঘটনাটি যেভাবে প্রদর্শিত হয়, তাতে সাম্প্রতিক ইতিহাসের পাতা থেকে সত্তরের কালপটভূমিটিই উঠে আসে।
সরাসরি নকশাল আন্দোলনের প্রসঙ্গ এসেছে ত্রয়ীর তৃতীয় ছবি পদাতিক-এ। পদাতিকে একটি স্পষ্ট আখ্যান আছে, মৃণাল সেন ও আশিস বর্মনের চিত্রনাট্য অনুযায়ী, নকশালকর্মী একটি ছেলে তিনটে গুলি খেয়ে একের পর এক গলি পেরিয়ে ছুটছে, বিরাট পর্দায় ভেসে ওঠে তার মুখ, এরপর গুলির শব্দ, মুখটা জ্বলে গিয়েছে আর ভেসে উঠছে টাইটেল। ছবির শেষাংশ এভাবে দেখিয়ে শুরু হয় গল্প, যেখানে সেই ছেলেটি, সুমিত( অভিনয় করেছেন ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) প্রিজন ভ্যান থেকে পালিয়ে বেশ কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকে এদিক ওদিক। একসময়ে সে এক অভিজাত এলাকায় এক ভদ্রমহিলার ফ্ল্যাটে আশ্রয় নেয়, ভদ্রমহিলা পঞ্জাবি। তিনি সেপারেটেড এবং বাবার সাজিয়ে দেওয়া ফ্ল্যাটে তিনি থাকেন, একটি দুধ উৎপাদনকারী কোম্পানির বিজ্ঞাপনবিভাগে তিনি চাকরি করেন, আবার নারীস্বাধীনতা বিষয়ে বিভিন্ন বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার নিতেও তাঁকে দেখা যায়। তাঁর একটিমাত্র পুত্রসন্তান পাহাড়ি এলাকায় বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশোনা করে। তাঁর বাসস্থানটি সুমিতের অজ্ঞাতবাসের সেরা জায়গা হয়ে ওঠে, একমাত্র সহযোদ্ধা বিমান ছাড়া বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সে যোগাযোগবিচ্ছিন্ন। ভদ্রমহিলা শীলাদেবীর ভাই রাজনৈতিক ডামাডোলে পঞ্জাবের রোপারে নিহত হয় পুলিশের গুলিতে, তারপর থেকে তিনি পার্টির সমর্থক। এই সূত্রে তিনি বাড়িতে রাজনৈতিক কর্মীকে আশ্রয় দিয়েছেন। অন্যদিকে সুমিতের মা শয্যাশায়ী, বাবা (অভিনয় করেছেন বিজন ভট্টাচার্য) একটি ছোটো প্রতিষ্ঠানের সামান্য কেরানি, তিনি একসময়ে স্বাধীনতা সংগ্রামী ছিলেন। সুমিতদের পার্টির মতাদর্শ তিনি বুঝতে পারেন না, তাদের বিপ্লবের পন্থার সঙ্গে একমত হতে পারেন না, তাই ছেলের সঙ্গে তাঁর রাজনীতি নিয়ে তর্ক হয়।

শীলার বাড়িতে থাকাকালীন অখণ্ড অবসরে সুমিতের মনে নানা প্রশ্ন জাগে পার্টির কাজ নিয়ে। সে ভাবতে থাকে কী করে ফ্রন্ট তৈরি করা যায়। অনেক প্রশ্ন ও মতদ্বৈধ নিয়ে একটি চিঠি সে লেখে পার্টির বড়ো নেতা নিখিলদার (জোছন দস্তিদার) কাছে, চিঠি সে একনিষ্ঠ কর্মী বিমানের হাত দিয়ে পাঠায়। প্রত্যুত্তরে বিমানকে আর সুমিতের সাথে যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করা হয়, টেলিফোনে সুমিতের সঙ্গে নিখিলদার কথা কাটাকাটি হয়, সুমিত জানায় কিছু বিষয় থাকবে যা তার ব্যক্তিগত। অন্যদিকে পার্টির বারণ থাকলেও বিমান এসে সুমিতের মার অসুস্থতার খবর দিয়ে যায়, বাড়ি গিয়ে সুমিত দেখে মা আর নেই। কিন্তু পলাতক সুমিতের বাড়ি আসার খবর পুলিশের কানে পৌঁছে যায়, পুলিশের গাড়ির শব্দ শোনার আগে সুমিত জেনে যায় তার বাবার অফিসে ফতোয়া জারি করা হয়েছিল যাতে সমস্ত কর্মী মুচলেকা দেয় তারা কোনো ইউনিয়ন, হরতাল করবে না। কিন্তু সুমিতের বাবা সেরকম মুচলেকা দেন নি। মৃণাল বলছেন,
“একটি ফ্রিজ শট। পলাতক আনন্দে হতবাক হয়ে গেল। বাবার দিকে গভীর দৃষ্টিতে তাকাল। ড্রাম বেজে উঠল। রাতের নীরবতার মধ্যে পুলিশ ভ্যানের আগমন। বাবা তাঁর পলাতক ছেলেটিকে পালানোয় সাহায্য করতে করতে বললেন: ‘বি ব্রেভ।’ ”১০
সুমিতের গুলিবিদ্ধ হওয়াটাই যদিও পরিণতি এবং তা টাইটেল দেখানোর আগেই দর্শককে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু ছবির শেষে প্রবল এক ইতিবাচকতা দর্শককে তৃপ্ত করে। কিন্তু এই কথাও স্মরণে রাখতে হবে যে, এই ইতিবাচকতা দেখানোর ভিতর কোনোভাবেই প্রচারমুখিনতা নেই, পরিচালকের দৃষ্টিভঙ্গির ভিতর বামপন্থী মনোভাবের প্রকাশ দেখলেও কোনোভাবে বলা যাবে না যে ছবিটি একদেশদর্শী কিংবা অতিবামপন্থার সপক্ষে ছবিটি নির্মিত হয়েছে। সুমিতের বাবার মতপরিবর্তনের ঘটনাটি অবশ্যম্ভাবী ছিল, যে কোনো ঋজু মেরুদণ্ডের মানুষের কাছে অপমান, অবমাননা সহ্য না করাটাই অনিবার্য। দর্শকের তৃপ্তির কথা ভেবেও ছবির শেষটি ইতিবাচক নয়, বরং দর্শকের তৃপ্তি এই কারণে যে, দীর্ঘদিনের বঞ্চনা, শোষণের যে বুর্জোয়াতন্ত্র সাধারণ মানুষের কণ্ঠরোধ করেছে, যে সিস্টেমের বিরুদ্ধে প্রাণ দিয়ে লড়াই করছে সত্তরের যুবসমাজ, একজন প্রবীণ স্বাধীনতা সংগ্রামী জীবনের উপান্তে পৌঁছেও নতুন করে সংগ্রাম শুরু করলেন, মিছিলে হাঁটলেন। তাত্ত্বিক বিরোধ সত্ত্বেও যেখানে অমোঘ হয়ে ওঠে প্রতিদিনের অপমান সহ্য করা, সেখানে বিরোধিতাই একমাত্র অস্ত্র- সুমিতের বাবা নতুন করে আবার অস্ত্র ধরলেন। আমরা মনে করতে পারি জন অরণ্য ছবির সোমনাথের বাবাকে, তিনিও নকশাল আন্দোলনের পিছনে তাত্ত্বিক শক্তির জায়গাটি বুঝতে চেয়েছিলেন, বলেছিলেন নতুন কিছুকে জানতে বুঝতে বয়সটা বড়ো কথা নয়। কিন্তু তাঁর প্রেক্ষাপট আলাদা, মনোভঙ্গিও আলাদা। তাঁর বড়ো ছেলে ভোম্বলের ভবিষ্যৎ সুনিশ্চিত, ছোটো ছেলে সোমনাথের গ্রাজুয়েশনের ফলাফলই তাঁকে বিচলিত করেছিল। সোমনাথ যদি ভালো ফল করত, যদি ভোম্বলের মতো তারও ভবিষ্যতের পথ মসৃণ হতো, তাহলে তিনি নকশাল আন্দোলন নিয়ে উৎসাহ দেখাতেন বলে মনে হয় না। তিনি স্পষ্টই বলেছেন, যেখানে সন্তানের প্রাণসংশয় উপস্থিত, সেখানে বাবা হয়ে কী করে তিনি এইসব আন্দোলনে জড়িয়ে পড়তে ছেলেকে সায় দেবেন। কিন্তু সুমিতের বাবা তাত্ত্বিক বিরোধ সত্ত্বেও ছেলের আদর্শগত সততা ও নিষ্ঠাকে সম্মান করেছেন, একসময়ে নিজেও প্রচলিত সিস্টেমের বিরুদ্ধে, মাথা না নুইয়ে মিছিলে হেঁটেছেন। সামান্য কেরানি তিনি, বিত্তবৈভবের মুখ কোনোদিন দেখেন নি। তাঁর ক্ষেত্রে তথাকথিত মধ্যবিত্ত ভীরুতা, সংশয় অনুপস্থিত। মৃণাল সেন তথাকথিত মধ্যবিত্ততাকে অস্বীকার করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে বিনা আপোসে রুখে দাঁড়ানোর বার্তাই এই ছবিতে রেখেছেন, অথচ এমনটা নয় যে তিনি সচেতনভাবে কোথাও নকশাল আন্দোলনের পক্ষে কথা বলেছেন। সুমিতের বাবা যে মিছিলে হাঁটেন, তা প্রকাশ্য দিবালোকে বড়ো রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায়। তাতে বোঝা যায়, যে এই বামপন্থী মিছিল আর যাই হোক, নকশাল পরিচালিত নয়।
বরং নকশাল কর্মীদের মধ্যে আত্মসমালোচনার প্রয়োজনীয়তার কথাই ভেবেছেন পরিচালক। সুমিতের লেখা দীর্ঘ চিঠি তার প্রমাণ। পার্টির যান্ত্রিক নিয়মতন্ত্র, কর্মীদের ব্যক্তিগত ‘স্পেস’কে অস্বীকার করা, নির্দিষ্ট কোনো দলের পরিবর্তে অল্প কয়েকজন নেতার প্রতি নির্ভরশীলতা, কর্মপন্থার ব্যাপারে নেতাদের একনায়কত্ব, মনীষীদের মুর্তি ভাঙার মতো বিভ্রান্তিকর পদক্ষেপ ইত্যাদি পার্টির ভিতকে দুর্বল করে তোলে। মৃণাল সেন এই ছবির উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন-“ আমার মনে হল এমন ছবি দরকার যেখানে একটি যুবক নিজেকে প্রশ্ন করবে। সে যুবকটি স্রোতের বিরুদ্ধে যাবে!
আমি ও আশিস বর্মন একটি চিন্তাভাবনা খাড়া করলাম, নতুন ছবি ‘পদাতিক’-এর আউট লাইন তৈরি হল।”১১
ছবিটি স্বভাবতই নকশাল আন্দোলনের সমর্থকদের ভালো লাগে নি, মৃণাল নিজে এক নকশালপন্থী সাংবাদিক বন্ধুর কথা তাঁর বইতে উল্লেখ করেছেন (পৃ ১০৭,ঐ), যেখানে ঐ ব্যক্তি ছবিটিকে ‘একটি পুলিশের রিপোর্ট’ বলে সমালোচনা করেছেন। পরিচালক এর কারণ খুঁজতে গিয়ে বলেন-
“ বললেন, সম্ভবত এই জন্যেই যে, এ-ছবিতে আত্মসমালোচনার একটা পর্ব ছিল। বিপ্লবী রাজনীতির কর্তৃত্ববাদী মানসিকতাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল।”১২
মৃণাল সেনের তিনটি ছবি পর্যালোচনা করে আমরা দেখতে পেলাম যে, নকশাল আন্দোলন কমবেশি তাঁর তিনটি ছবিতেই এসেছে- ছবির পটভূমিরূপে নয়, বিষয় রূপেই। তাঁর এই ছবিগুলির কনটেন্ট একান্তভাবেই রাজনৈতিক এবং তাঁর রাজনীতিবোধের সঙ্গে আরো দুটি বিষয় প্রবলভাবে যুক্ত হয়ে আছে- সাম্প্রতিকতা বা বর্তমানতা এবং কলকাতা শহর। কিন্তু নির্দিষ্ট কোনো রাজনৈতিক দলের প্রচার তিনি করেন নি, বরং কিছুটা বামপন্থী মনোভাব নিয়ে সার্বিকভাবে বঞ্চনা, শোষণের বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামের পক্ষে মত দিয়েছেন। সাতের দশকের নকশালবাড়ি আন্দোলন সেই সাম্প্রতিকতা, কলকাতা শহর এবং সার্বিক সংগ্রামের সূত্রেই তাঁর ছবিতে এসেছে, সেই আন্দোলনের শক্তিকে যেমন তিনি চেয়েছেন সিনেমায় দেখাতে, তেমনই জানিয়েছেন এই আন্দোলনের সদুদ্দেশ্য সত্ত্বেও কিছু কিছু সংশোধনের জায়গা ছিল।
ঋত্বিক ঘটকের শেষ ছবি যুক্তি তক্কো আর গপ্পোকে আমরা তাঁর রাজনৈতিক সিনেমা হিসাবেই দেখতে চেয়েছি। তাঁর প্রথম ছবি নাগরিক এবং শেষ ছবি যুক্তি তক্কো আর গপ্পো একইসঙ্গে মুক্তি পায় (১৯৭৭) তাঁর মৃত্যুর পরে। সাতের দশকের নকশাল আন্দোলনকে তিনি বঙ্গীয় ইতিহাসের এক বিশাল প্রেক্ষাপটে স্থাপন করেছেন এই ছবিতে, ফলে বিশেষ রাজনৈতিক দর্শনের প্রতি পক্ষপাত এই ছবিতে থাকার কথাই নয়। এই বিষয়ে তাঁর নিজের বক্তব্য-
“(রাজনৈতিক মতাদর্শ) ব্যাখ্যার কথা না। ওতে ১৯৭১ সাল থেকে ’৭২ সালে পশ্চিমবাংলার যে-রাজনৈতিক পটভূমি এবং সেটাকে আমি নিজের চোখে যা দেখেছি from a point of view of not a politician. Political কোন মতবাদকে, যেমন Naxalite মতবাদকে আমার please করার কথা না, ইন্দিরা গান্ধিকে please করার কথা না, CPM কে please করার দরকার নেই, CPI- কেও please করার দরকার নেই- আমার থাকলেও ছবিতে আমি slogan-এ বিশ্বাস করি না।” ১৩
সত্যজিতের ছবির মধ্যবিত্ত বিচ্ছিন্নতাবোধ, মৃণাল সেনের সিনেমার দৈনন্দিন সমাজবাস্তবতার পরিবর্তে ঋত্বিকের ছবিতে আমরা পেয়েছি সমকালীনতা-অতিরিক্ত এক বৃহত্তর ইতিহাসবোধ, পুরাণ ও মেলোড্রামার যুগলবন্দিতে তিনি আবিষ্কার করতে চান ঔপনিবেশিকতা-অতিক্রমী বাংলার সাংস্কৃতিক চালচিত্র, দেশভাগ ও উদ্বাস্তুসমস্যা তাঁর সিনেমার অনিবার্য পটভূমিরূপে আসে। প্রতিমুহূর্তের বাস্তবতাকে প্রায় অস্বীকার করে তিনি জন্ম দেন এক অতিকথার, যার মধ্যে একই সঙ্গে পৌরাণিকতা ও সাম্প্রতিকতা মিলেমিশে থাকে, যুক্তি তক্কো আর গপ্পো তার ব্যতিক্রম নয়। নীলকণ্ঠ, দুর্গা, নচিকেতা, জগন্নাথ, পঞ্চানন প্রভৃতি নামগুলোর সঙ্গে তাই অবলীলায় একাসনে বসে বঙ্গবালা তথা বাংলাদেশের আত্মা।

ছবির শুরুতে দেখা যায়, নীলকণ্ঠ বাগচি (অভিনয় করেছেন ঋত্বিক স্বয়ং) নামের এক মাতাল বুদ্ধিজীবীর ঘর ছেড়ে কাঞ্চনপুর নামের এক জায়গায় স্কুলশিক্ষকতার চাকরি নিয়ে পুত্রসহ চলে যাচ্ছেন তাঁর স্ত্রী দুর্গা। পুত্র সত্যকে তিনি সুশিক্ষায় বড়ো করে তুলতে চান, যা নীলকণ্ঠের সঙ্গে থাকলে সম্ভব নয়। ইয়ারবন্ধু আর দেশি মদ নিয়ে নীলকণ্ঠের দিন চলে। নীলকণ্ঠ নিজের পরিচয় দেন ভাঙা বুদ্ধিজীবী বা ব্রোকেন ইন্টেলেকচুয়াল বলে, যার আর সমাজ সংস্কৃতিকে দেবার কিছু নেই, শহুরে দুর্নীতি, ভণ্ডামি, মিথ্যাচার দেখে দেখে তিনি ক্লান্ত। একমাত্র মদ খাবার পয়সা জোটানোর প্রয়োজন ছাড়া তিনি মিথ্যা বলেন না। দুর্গা চলে যাবার সাত দিনের মধ্যে বাড়িওয়ালা তাঁকে ঘর ছাড়তে বলে, নচিকেতা নামের এক শিক্ষিত বেকার প্রায় সন্তানসম এক যুবকবন্ধুকে নিয়ে তিনি ঘর ছাড়েন, দেখা হয় বঙ্গবালা নামের এক মেয়ের সাথে, একাত্তর সালে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অস্থিরতা ও মিলিটারি বর্বরতার শিকার হয়ে সে এপারে চলে আসে। নীলকণ্ঠ তাকে মা সম্বোধন করে, বলেন –“তুমি কি বাংলাদেশের আত্মা?” আমরা দেখি, সংলাপ এবং অভিনয়ের অতিনাটকীয়তায় বঙ্গবালার মধ্যে অখণ্ড বাংলাদেশের মাতৃপ্রতিমাকে আবিষ্কার করতে চাইছেন ঋত্বিক।

বঙ্গবালা ও নচিকেতাকে নিয়ে পথে বেরোন নীলকণ্ঠ, দেখা হয় ওপার বাংলা থেকে চলে আসা আর এক আশ্রয়প্রার্থী সংস্কৃতের শিক্ষক জগন্নাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে। তাঁরা সকলে কলকাতার পথে, স্টেশনে, নদীর ধারে ঘুরে বেড়ান উদ্দেশ্যহীনভাবে, শহুরে লেখক বুদ্ধিজীবীদের আড্ডায় আর মন বসে না নীলকণ্ঠের। তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে পুরুলিয়ায় আসেন পদব্রজে, দেখা হয় একসময়ের নাম করা ছৌ শিল্পী পঞ্চানন মাস্টারের সঙ্গে। ছৌ শিল্পীদের সঙ্গে জোতদারের লড়াইয়ের মাঝে অতর্কিতে প্রাণ যায় পণ্ডিত জগন্নাথের। চোখের জলে তাকে বিদায় দিয়ে সকলে আসেন দুর্গার কাছে, দুর্গার কাছে নীলকণ্ঠ বলেন সত্যকে নিয়ে একটিবার শালের জঙ্গলে যেতে পরের দিন ভোরবেলায়, প্রথম সূর্যের আলোয় ছেলের মুখ দেখতে চান তিনি। এই বলে তিনি চলে যান জঙ্গলে, নচিকেতা ও বঙ্গবালাও সঙ্গে যায়। এখানে নকশাল ছেলেদের সঙ্গে দেখা হয় তাঁর, এই দৃশ্যে মার্কস, লেনিনের তত্ত্ব, বুদ্ধিজীবীর অবস্থান ইত্যাদি বিষয়ে দীর্ঘ সংলাপ আছে তাঁর। কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ আসে, নকশালদের সঙ্গে এনকাউন্টারে মাঝখান থেকে গুলিবিদ্ধ হন নীলকণ্ঠ। সকালে দুর্গা আসে, মৃত্যুর দৃশ্যে তার হাতটি ধরে নীলকণ্ঠ নিয়ে আসেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্পী গল্পের মদন তাঁতির প্রসঙ্গ, যে তার রুটিরুজির জন্য হলেও নিজের সমাজের সঙ্গে বেইমানি করতে পারে নি। ফুরিয়ে আসা, সমাজ ও সংসারকে কিছুই না দিতে পারা নীলকণ্ঠও কখনো মিথ্যাচার করতে পারে নি।
রূপকের আশ্রয় নিলেও এই ছবির বাস্তবতা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। ছবির কাহিনি ছাড়া ছাড়া, তবু এক গল্পসূত্র রেখেছেন ঋত্বিক। সমস্ত কাহিনিটুকু মানুষের অন্তহীন যাত্রা গল্প, নিঃসঙ্গতা ও ‘কার্নিভাল’ নিয়ে বৈচিত্র্যমণ্ডিত সেই যাত্রা। আরো স্পষ্ট করে বলে, এই যাত্রা একান্তই নীলকণ্ঠের, সমর সেনের কবিতার মতোই নাগরিক ক্লান্তি ও বর্বরতা থেকে মুক্ত হবার ঐকান্তিক ইচ্ছাটুকু সম্বল করে তিনি পথে নামেন। শহুরে রাজনীতি, সত্তরের উত্তাল দশকেও এক শ্রেণির বুদ্ধিজীবীর মধ্যে গা বাঁচানো মনোভাব ও ক্ষমতার তোষণকে সহ্য করতে না পেরে তিনি ফিরে যান অরণ্যের কাছে, ক্ষয়ে যাওয়া শরীর ও মন নিয়ে আশার আলো খুঁজতে চান একালের তরুণদের মধ্যে, ভোরের আলোয় শিশুর মুখ দেখার আকুতি তাঁর প্রবল হয়ে ওঠে। সমকালীন রাজনীতিকে তোলপাড় করে দেওয়া নকশাল আন্দোলনের কর্মীরা তাঁর চোখে শ্রদ্ধার যোগ্য, কিন্তু ‘মিসগাইডেড’। এই প্রসঙ্গে বলেছেন,
“ (নকশালদের প্রতি) স্নেহপ্রবণ তো হতে বাধ্য আমি। ... হিশেবের বাইরে কেন? আমি তাদের সঙ্গে, তাদের মতামত এবং তাদের আদর্শের সঙ্গে একদম একমত নই। কিন্তু তাদের সততা? সেটাকে শ্রদ্ধা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। আর তো কাউকে দেখি না। এই বাচ্চা বাচ্চা ছেলেগুলো- এদের আর কিছু নয়- এরা সম্পূর্ণ misguided. যেটা আমার ছবিতেও আমি বলেছি। কিন্তু এদের সততার কোন তুলনা নেই। এরা নিজেদের জন্য কিছু চায় না, এরা দেশের জন্য চায়। সেটাকে আমি শ্রদ্ধা করব না?” ১৪
দেশকে মাতৃকল্পে দেখা ঋত্বিকের প্রিয় থিম, বঙ্গবালার কল্পনায়, নামকরণে, দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে ‘কেন চেয়ে আছ গো মা’ গানে এই ছবিতেও তিনি দেশের মাতৃমূর্তি স্থাপন করেন, বাংলাদেশের আত্মার সন্ধান তাঁর শিল্পীমানসের অন্যতম অন্বিষ্ট। যুক্তি তক্কো আর গপ্পো প্রবলভাবে রাজনৈতিক ছবি এই কারণে নয় যে তাতে পুলিশের সঙ্গে নকশাল ছেলেদের এনকাউন্টার দেখানো হয়েছে কিংবা নীলকণ্ঠের মুখে রাজনৈতিক দর্শনের বুলি তুলে দেওয়া হয়েছে, বরং তা এই কারণে রাজনৈতিক যে, এই ছবিতে উদ্বাস্তু সমস্যা, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং নকশাল আন্দোলনের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক অধ্যায়গুলিকে বাংলাদেশের বৃহত্তর ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে স্থাপন করা হয়েছে। অথচ ঋত্বিক কোথাও এই বিষয়গুলিকে জোর দিতে গিয়ে তাঁর সমাজ-সংস্কৃতিবোধের সামগ্রিকতাকে হারান না, সমকালীনতা কোথাও উচ্চকিত না হয়েও বাংলাদেশের সামগ্রিক ইতিহাসের অংশ হয়ে যায়। আবার একইসঙ্গে তিনি রাজনীতির প্রতি দায়বদ্ধ, নিজে মার্কসবাদী রাজনীতি করেছেন, আই.পি.টি.এ.-র সদস্য ছিলেন, তাঁর কাছে অরাজনৈতিক বলে কিছু হয় না-
“রাজনীতি জীবনের একটা বিরাটতম অংশ, রাজনীতি ছাড়া কিছুই হয় না, প্রত্যেকেই রাজনীতি করে, যে করে না বলে, সে-ও করে। Apolitical বলে কোন কথা নেই। You are always a partisan, for or against.”১৫
কিন্তু রাজনীতি মানে তাঁর কাছে শুধু কিছু দল, মত, মতবিরোধ নয়, এক বৃহত্তর দেশিক বোধ তাতে সম্পৃক্ত হয়ে থাকে -
“তখনও ভেবেছি, এখনও ভাবি রাজনীতির সঙ্গে সঙ্গে দর্শন, ভারতীয় ঐতিহ্য সমস্ত কিছুকে নিয়ে। কারণ নতুন ছবির ব্যাপারে ভারতীয় প্রাচীন জীবনটাকে, ভারতের যে-বিরাট ব্যাপারটা, তাকে ভীষণভাবে neglect করা হচ্ছে, অর্থাৎ এ সব নিয়ে পড়াশোনা করাটা যেন progressive নয়। আমি মোটামুটি এসব নিয়েই করে যাচ্ছি এবং যাব, যতদিন বেঁচে থাকব।”১৬
আমাদের এই অধ্যায়ের আলোচ্য তিন পরিচালক, একই সময়পটভূমিতে রাজনীতিকে ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিকে দেখেছেন- সত্যজিৎ তাকে বাইরের ঘটনা হিসাবেই রেখেছেন তাঁর ছবিতে, তাকে শুধু পটভূমি রূপে ব্যবহার করে মূল ফোকাস নিয়ে এসেছেন মধ্যবিত্ত মানুষের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণে। মৃণাল সেন সেই রাজনীতিকেই, অর্থাৎ নকশাল রাজনীতিকে জীবন্ত করে তুলেছেন দৈনন্দিনতার প্রতি মুহূর্তে- শুধু সত্তর দশক নয়, তিনি দেখাতে চেয়েছেন হাজার বছরের শোষণ, বঞ্চনার প্রচলিত সিস্টেমেরই প্রতিষেধ হয়ে উঠছে যুবশক্তির বিদ্রোহ, আবার শিল্পীর সততায় তাঁর সমকালের বিপ্লবী রাজনীতির ত্রুটিবিচ্যুতিকেও সিনেমায় এনেছেন। আর ঋত্বিক লো এঙ্গেল শটের অনবদ্য ব্যবহারে, মানুষের মুখের ক্লোজ আপ নিত নিতে হঠাৎই চলে গেছেন সবুজ বঙ্গপ্রকৃতির বিরাটত্বে, রাজনীতি তাঁর সিনেমার অবিচ্ছেদ্য বিষয়, কিন্তু তা বৃহত্তর দেশকালের সঙ্গে সম্পৃক্ত।
উল্লেখপঞ্জি
১। মৃণাল সেন, তৃতীয় ভুবন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি., ৫ম মুদ্রণ, ২০১৮,পৃ. ৭।
২। ঐ, পৃ. ১৮।
৩।(https://youtube.be/_n-Pv6Ob2Lo) accessed on 13.08.19
৪। ঐ
৫।বাণী বসু, সুবর্ণরেখাঃ অঙ্গাররেখা, চিত্রভাষ, ঋত্বিক ঘটক ও সুবর্ণরেখা বিশেষ সংখ্যা, বর্ষ ৩৯, বইমেলা ২০০৫, পৃ ৭৫
৬। মৃণাল সেন, তৃতীয় ভুবন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি.,৫ম মুদ্রণ, পৃ. ৯৭-৯৮।
৭। ঐ, পৃ. ৯৬।
৮। ঐ, পৃ. ৯৪।
৯। ঐ, পৃ. ৯৪।
১০। ঐ, পৃ. ১০৯।
১১। ঐ, পৃ. ১০৮।
১২। ঐ, পৃ. ১০৭।
১৩।(ঋত্বিককুমার ঘটক, নিজের পায়ে নিজের পথে, সিনে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা এবং মনফকিরা, ২০১০, পৃঃ ৩০-৩১)
১৪। ঐ, পৃ. ২৮।
১৫। ঐ, পৃ. ১৫।
১৬। ঐ, পৃ. ১৫।
