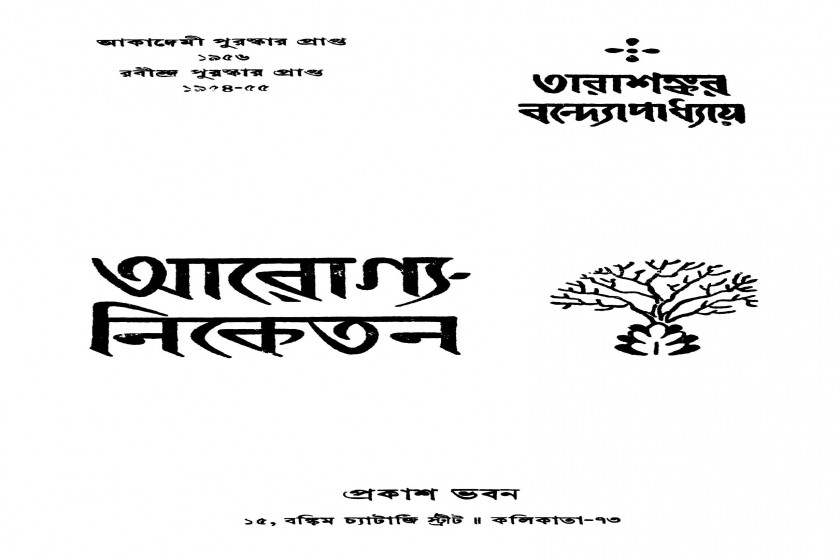
‘আরোগ্য-নিকেতন’ ও কয়েকজন চিকিৎসক : আমার চোখে তারাশঙ্করের গল্পভুবন
- 18 March, 2022
- লেখক: নীতা মণ্ডল
(১)
‘শ্রীহীন গ্রাম দেবীপুর, দারিদ্র্যের ভারেই শুধু নিপীড়িত নয়, কালের জীর্ণতাও তাঁকে জীর্ণ করে তুলেছে। লক্ষ করে দেখবেন-গ্রামের বসতির উপর যে গাছগুলি মাথা তুলে পল্লব বিস্তার করে রয়েছে তার অধিকাংশই প্রবীণ প্রাচীন, নতুন গাছের লাবণ্যময় শোভা কদাচিৎ চোখে পড়বে। ... প্রথমেই চোখে পড়বে- ঝড়ে শুয়ে পড়া শূন্যগর্ভ বকুলগাছতলায় ধর্মঠাকুরের আটন। তারপরেই পাবেন একটি কামারশালা... ওই সামনেই দেখছেন- মা কালীর থান, বাঁয়ে চন্দমশায়ের লটকোনের দোকান- ডাইনে ভাঙবেন- দেখবেন বাঁধানো কুয়ো; সরকারী কুয়ো, তার পাশেই জীবনমশায়ের কবরেজখানা, অর্থাৎ আরোগ্য-নিকেতন।’
‘আরোগ্য-নিকেতন’ উপন্যাসের সূচনায় খোদ মহানগর থেকে দেবীপুরের আরোগ্য-নিকেতনে যাবার পথ বাতলে দিয়েছেন লেখক তারাশঙ্কর। রেলপথে এসে নবগ্রামে নেমে তার নিকটবর্তী গ্রাম দেবীপুর। দত্ত পরিবার বংশ পরম্পরায় সেখানেই বসবাস করে আসছেন। তিনপুরুষ ধরে কবিরাজি চিকিৎসায় সুনাম অর্জন করে তাঁরা লাভ করেছিলেন ‘মহাশয়’ উপাধি। পরিবারের তৃতীয় প্রজন্ম জীবনবন্ধু দত্ত ওরফে জীবনমশায় এই কাহিনির মূল চরিত্র।
জীবনমশায়ের যৌবনকালকে তারাশঙ্কর চিহ্নিত করেছিলেন কালান্তর হিসেবে। যেখানে দেবীপুরের লাগোয়া বর্ধিষ্ণু গ্রাম নবগ্রামে কালান্তরের ছাপ সুস্পষ্ট। মহানগরী থেকে শতাধিক মাইল ট্রেনে আসার পর জংশন স্টেশন থেকে আরও দশমাইল আসতে হয় ছোট লাইনে। সেখানেই গ্রাম্য স্টেশন নবগ্রাম।
উপন্যাসের সময়কালকে পেছনে ফেলে আজকের দিনেও যদি রেলপথে সেই রাস্তায় যান তাহলে পৌঁছে যাবেন লেখকের স্বগ্রাম লাভপুরে। অবশ্য সেই ছোটলাইন আর পাওয়া যাবে না তবে দুপাশে বিস্তীর্ণ ধানক্ষেতের মধ্যে বড় লাইনের ট্রেনে যেতে যেতে মনে হবে, এই পথ চেনা পথ। যেমনটা পড়েছি উপন্যাসে। ট্রেন থেকে নেমে দেবীপুরের খোঁজে বেরিয়ে পড়তে হবে লেখকের পথ নির্দেশ মেনেই। যেতে যেতে চোখ রাখতে হবে পথের দুপাশে। সেই যে কালান্তরের কথা লেখক বলেছিলেন তার নিশানা খুঁজতে খুঁজতে মনে হবে তারপর যে কতবার কালান্তর ঘটে গিয়েছে তার হিসেব নেই। সময়ের চাকা ঘুরেছে আর একটা কালকে পেছনে ফেলে দিয়ে এগিয়ে এসেছে নতুন কাল। প্রাচীনকে বিদায় জানিয়ে নবীনের জয়যাত্রা বারংবার ঘটেছে এই মাটিতে। পথের ধারে ধারে শতাব্দীপ্রাচীন প্রাসাদোপম বাড়িগুলির দেওয়ালে দেওয়ালে খচিত হয়ে আছে কত ইতিহাস। সাদা মর্মর ফলকে সাল তারিখসহ বাড়ির কর্তা বা গিন্নীর নাম জ্বলজ্বল করছে। আর আছে প্রাচীন মন্দির ও দেবালয়। যত বনেদী বংশ, তত দেবদেবী।
কাহিনির নবগ্রাম এবং বাস্তবের লাভপুর কখন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে বোঝা যায় না। দেবীপুরের উদ্দেশে উত্তরমুখে এগিয়ে যেতে যেতে কখন যে একটা গ্রাম শেষ হয়ে অন্য গ্রাম শুরু হয়ে যায় আজ তাও বোঝার উপায় নেই। জীবনমশায়ের সময় এই রাস্তাই ছিল খানাখন্দে ভরা। খানাখন্দগুলির বিচিত্র সব নাম ছিল। ‘চোরধরির গাদ (কাদা)’ অর্থাৎ যে খন্দে পড়লে চোর উঠে পালাতে না পেরে ধরা পড়ে অথবা ‘গোরুমারির খাল’ অর্থাৎ যে গাড্ডায় পড়ে কারও গোরু মারা গেছে।
এখনকার রাস্তা কনক্রিটে তৈরি। পরিচ্ছন্ন। সেই কালের অনুপাতে জনসংখ্যা বেড়েছে কয়েকগুন। একদা রাস্তার ধারে ধানের জমিগুলিতেও বসতি স্থাপন হয়েছে। বেশীরভাগই ছোট ছোট ইটের ঘর। খুব যে সচ্ছলতার ছাপ আছে এমন নয় তবে জীর্ণ পুরনো ব্যবস্থাকে বাতিল করার একটা চেষ্টা আছে। যেতে যেতে রাস্তার বামদিকে একটি প্রাচীন বকুলগাছের উপর নজর পড়লেই থামতে হবে। আশ্চর্য! ‘ঝড়ে শুয়ে পড়া শূন্যগর্ভ বকুলগাছে’র কান্ডটি আজও শুয়ে রয়েছে! জায়গাটি ধর্মরাজতলা। ‘আরোগ্য-নিকেতনে’র শেষ ভাগে দেখা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত জীবনমশায় নিজের নাড়ী বিচার করে মৃত্যু সম্পর্কে বলছেন, ‘সে আসছে। মনে হচ্ছে গ্রামের বাইরে তার পায়ের শব্দ উঠছে; গ্রামে ঢুকবার মুখে ধর্মরাজ স্থানের বকুলতলায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে।’ এর তিনমাস পর দ্বিতীয়বার আক্রান্ত হলে তিনি এই কালের ডাক্তারকে বলেছিলেন, ‘এইবার সে বকুলতলা থেকে বিশ্রাম সেরে উঠে দাঁড়াল।’
মহুগ্রামের ধর্মরাজতলাকে ‘দেবীপুরের ধর্ম ঠাকুরের আটন’ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারলেই উপন্যাসের পটভূমিতে ঢুকে পড়া যায়। এরপর সামান্য এগিয়ে গেলে কালীমন্দির। রাস্তার ডানদিকে। বামদিকে ‘চন্দমশাইয়ের লটকোনের দোকান’ অর্থাৎ মুদি দোকান। না দোকানপাট নেই, তবে চন্দ্রদের একটি বিশাল দোতলা পাকাবাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে। কালীমন্দিরের কাছে ডানদিক ঘুরলেই দেখতে পাওয়া যাবে বাঁধানো কুয়োর দেহাবশেষ। সেই ‘সরকারী কুয়ো’। এককালে যখন জীবনমশায় রাজনৈতিকভাবে গণ্যমান্য হয়েছিলেন তখন চিকিৎসক হিসেবেও তাঁর পসার ছিল রমরমা। চতুর্দিকের গ্রাম থেকে রোগী এসে অপেক্ষা করত। এক এক বেলায় ষাট সত্তরজন। তখন এই কুয়োর জলে রোগীর পরিজনরা তৃষ্ণা মিটিয়েছে, চিড়ে মুড়ি ভিজিয়ে খেয়েছে। কুয়োটি এখন বুজিয়ে দেওয়া হয়েছে। আন্দাজ করা যায় অচিরেই সেই বাঁধানো অংশটুকুও বিলুপ্ত হবে। এই কুয়োর ডানদিকেই ছিল সেকালের স্বনামধন্য কবিরাজ মাখনলাল দত্তের চিকিৎসালয়। তার কোনও চিহ্ন আজ অবশিষ্ট নেই। তার একমাত্র পুত্র জঙ্গলের মৃত্যু হয়েছিল যৌবনেই। মাখনলালের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরসূরিরা এই গ্রামের বাস তুলে দিয়ে অন্যত্র বসবাস শুরু করে। ডানদিকের রাস্তার দুপাশে একটার পর একটা ছোটছোট ছিমছাম একতলা পাকাবাড়ি। তাই এবার যেটুকু দেখার, দেখতে হবে মনশ্চক্ষে। হয়ত দেখতে পাওয়া যাবে ‘দিক-হস্তীর মতো প্রাচীন’ জীবনমশায় খোড়ো কোঠাঘরের লম্বা সিমেন্টের ফুটিফাটা বারান্দায় দাবার ছক পেতে বসে আছেন অথবা তাঁর উদাসী দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে ঊর্ধ্বলোকে, আকাশের নীলে। ভাবছেন তাঁর ফেলে আসা জীবনের বিচিত্র সব অভিজ্ঞতার কথা। অথবা শুনতে পাওয়া যাবে ভারী পদক্ষেপে গ্রামের রাস্তা ধরে রোগী দেখে ফিরে আসছেন আরোগ্য-নিকেতনে।
ভাবনার গভীরতায় ডুবে গেলে কিন্তু আপনার চারপাশে ভিড় জমে যাবে। পাড়ার লোকজন কৌতূহলী হয়ে বেরিয়ে এসে প্রশ্ন করবে, ‘কী মশায়, কোত্থেকে?’ যেই আপনি উচ্চারণ করবেন ‘আরোগ্য-নিকেতন’। নিমেষে ওদের চোখেমুখে আলো জ্বলে উঠবে। শতাব্দী প্রাচীন একজন কবিরাজের সম্পর্কে অনেক লৌকিক অলৌকিক কাহিনি আপনি তাঁদের মুখে শুনতে পাবেন। সে সব বিশ্বাস করবেন কি করবেন না তা আপনার ব্যাপার তবে ধীরে ধীরে আপনি আবিষ্কার করবেন এদের পরিবারগুলিই কয়েক প্রজন্ম পূর্বে মাখনলাল দত্ত অর্থাৎ জীবনমশায়ের প্রতিবেশী ছিল। তারা সেই প্রবাদপ্রতিম কবিরাজের কথা তাদের পিতামহ বা প্রপিতামহের মুখে শুনেছে। শুনেছে তাঁর নিদেন হাঁকার কথা এবং তাঁর ছেলে জঙ্গল (কাহিনিতে বনবিহারী) এর মৃত্যুর কথাও।
ভালো লেগে গেলে প্রাচীন এই গ্রামখানি ঘুরে আসুন আমরা ততক্ষণে চোখ রাখি ইতিহাসের পাতায়। সেকালের নাড়ীটেপা ডাক্তারদের চিকিৎসাপদ্ধতি থেকে আধুনিক চিকিৎসাপদ্ধতির বিবর্তনের ইতিহাসে।
(২)
দ্বিতীয় শতাব্দীতে পশ্চিমা বিশ্বে একজন প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসাবিদ ছিলেন। তাঁর নাম ছিল গ্যালেন। গ্রীসে জন্ম হলেও গ্যালেনের কর্মভূমি ছিল রোম। টানা কয়েক দশক ধরে রোমান সম্রাটদের গৃহ চিকিৎসকের ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। প্রাচীন গ্রীক চিকিৎসাশাস্ত্রীয় জ্ঞান এবং নিজের গবেষণার ফলাফল মিলিয়ে আবিষ্কার করেছিলেন অসামান্য কিছু চিকিৎসা পদ্ধতি। তখন রোমে মানবদেহ ব্যবচ্ছেদ করা নিষিদ্ধ থাকায় গ্যালেন শূকর বা অন্যান্য প্রাণী ব্যবচ্ছেদ করে গবেষণার কাজ করতেন। তাঁর কাজগুলি এতটাই জনপ্রিয় হয়েছিল যে সেগুলোকে আলাদা করে বলা হত গ্যালেনিজম। সবই যে তাঁর মৌলিক আবিষ্কার ছিল তা নয়। বহু প্রাচীন চিকিৎসকের তত্ত্ব, যেগুলি তিনি সঠিক বলে মনে করেছিলেন তা গ্রহণ করেছিলেন। গ্যালেনিজমের মূল তত্ত্বগুলির অন্যতম ছিল রোগীর পালস বা নাড়ীর স্পন্দন সূক্ষ্মভাবে পরিমাপ করে রোগ নির্ণয় করা সম্ভব।
ভারতবর্ষের মতো দেশে আয়ুর্বেদ হল পঞ্চম বেদ। প্রাচীনকাল থেকে শতাব্দীর পর শতাব্দী বায়ু-পিত্ত-কফ আর তার খুঁটিনাটির বিদ্যা প্রয়োগ করে মানবদেহের রোগনির্ণয় আর তার প্রতিকারের উপায় নির্ধারণ করে এসেছেন একদল চিকিৎসক। দেখিয়েছেন রোগমুক্তির পথ। সেই সব ভিষগাচার্যরা রোগীর মণিবন্ধে হাত দিয়ে চোখ বন্ধ করে অনুভব করতেন নাড়ীর গতি আর ছন্দ। সেই থেকে রোগ নির্ণয় করতেন। এই কাজে আয়ুর্বেদের জ্ঞানের সঙ্গে প্রয়োজন হতো অধ্যাবসায় ও প্রখর অনুভবশক্তি। নাড়ীর গতি প্রকৃতি অনুভব করে তাঁরা রোগের সময়কাল বলে দিতে পারতেন। কখন রোগের প্রকোপ বাড়বে, কখন কমবে, কখন ব্যাধি এসেছে কালরূপে অর্থাৎ মৃত্যুর দূত হয়ে, কখন আবার কঠিন রোগেও রোগী লড়াই করে জিতে যাবে এ সবই নাকি তাঁরা নাড়ী ধরে বুঝতে পারতেন। সেই মতো তাঁরা ওষুধ ও পথ্য দিতেন। গ্রাম বাংলায় এইসব ভিষগাচার্যরাই ছিলেন মানুষের জীবন মরণের ভরসা।
ইউরোপে রেনেসাঁ আগমনের আগে পর্যন্ত গ্যালেনের তত্ত্বই ছিল চিকিৎসাবিজ্ঞানের মৌলিক নীতি। ত্রয়োদশ শতকে ইবনুন আল নাফিস নামের একজন আরবি চিকিৎসাবিদ পালমোনারি সারকুলেশন আবিষ্কার করে প্রথম গ্যালেনের চিকিৎসা পদ্ধতির উপর প্রশ্ন তুলেছিলেন। এর প্রায় দুশো বছর পর স্যার উইলিয়াম হার্ভে (১৫৭৮-১৬৫৭) আবিষ্কার করেছিলেন শরীরে রক্ত সঞ্চালনের সঠিক গতিপথ। তিনি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন যে, নাড়ীর স্পন্দনের উৎস নাড়ী নয়, হৃৎপিণ্ডের বাম নিলয়। সপ্তদশ শতকে গ্যালিলিওর পেন্ডুলাম আবিষ্কারের পর স্যান্টারিও স্যান্টারিয়াম (১৫৬১-১৬৩৬) আবিষ্কার করলেন পালসোলজি। এরও প্রায় একশ বছর পরে জন ফ্লয়ার (১৬৪৯-১৭৩৪) আবিষ্কার করলেন পালস ওয়াচ। প্রতি মিনিটে নাড়ীর স্পন্দন নির্ভুলভাবে গণনা করা সম্ভব হল। এরপর উনিশ শতকে বিশ্বজুড়ে নাড়ীর স্পন্দন সংক্রান্ত গবেষণা দ্রুতগামী রথে চেপে অনেকগুলি মাইলফলক পেরিয়ে গেল। আবিষ্কার হল স্ফিগমোমিটার, টাইমোগ্রাফ, স্ফিগমোগ্রাফ এবং পালস ওয়েভ ভেলোসিটির তত্ত্ব। নাড়ীর স্পন্দন গণনা হয়ে উঠল সূক্ষ্ম যন্ত্র নির্ভর এবং পুরোপুরিভাবে বিজ্ঞানসম্মত।
অন্যদিকে কবিরাজ মহাশয়দের নাড়ী পরীক্ষার পদ্ধতি কতটা বিজ্ঞানসম্মত ছিল, তা যাচাই করার মতো কোনও বিশ্বস্ত উপায় ছিল না। বিংশশতাব্দীর শুরুর লগ্নেও এদেশের বুকে ‘নাড়ী-টেপা’ কবিরাজরা নিজেদের পেশায় টিকে থাকলেও ধীরে ধীরে তাঁদের নাড়ীর স্পন্দনের অনুভব ক্ষীণ হয়ে এল। এদেশের মানুষের কাছে কাম্য হয়ে উঠল আধুনিক অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা। সেই সময়টিকে চিকিৎসা ক্ষেত্রে যুগসন্ধিক্ষণ বললে ভুল হবে না। সেই কালের ছবি যথার্থ ফুটে উঠেছে তারাশঙ্করের বর্ণনায়, ‘তখন দেশে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসা রাজকীয় সমারোহে রথে চড়ে আবির্ভূত হয়েছে। কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ, হাসপাতাল, বর্ধমান মেডিক্যাল স্কুল... ইংরেজ সাহেব ডাক্তার, দেশী নামজাদা ডাক্তারদের পোশাক গলাবন্ধ কোট, প্যান্টালুন, গোল টুপি, গার্ডচেন, বার্নিশ করা কাঠের কলবাক্স। ঝকঝকে লেবেল আঁটা সুন্দর শিশিতে ঝাঁঝালো রঙীন ওষুধ, ওষুধ তৈরীর সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়া, সব মিলিয়ে সে যেন এক অভিযান।’
‘আরোগ্য-নিকেতন’ উপন্যাস চিকিৎসাবিজ্ঞানের এই যুগসন্ধিক্ষণের সময় এবং প্রাচীন ও আধুনিক চিকিৎসকের দ্বন্দ্বকে তুলে ধরে। তারাশঙ্করের নিজের চোখে দেখা পল্লী অঞ্চল, সেখানকার আপামর জনসাধারণ, তাঁদের স্বাস্থ্যবিধি এবং তৎকালীন কবিরাজী এবং অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসকদের নিয়ে কাহিনি গড়ে উঠেছে। ‘আরোগ্য-নিকেতনে’র অজস্র চরিত্রের মধ্যে কয়েকজনের পরিচয় লেখক নিজেই প্রকাশ করে দিয়েছেন। উপন্যাসটি প্রকাশিত হওয়ার পর তারাশঙ্কর ব্যোমকেশ মজুমদারকে চিঠিতে লিখেছিলেন, ‘জীবনমশায় ছিলেন। তাঁকে দেখেছি, তাঁর ওষুধ খেয়েছি। এবং যে সব রোগী ও রোগের কথা লিখেছি তার পনের আনাই সত্য। কৃষ্ণদাসবাবুর যে ছেলেটির টাইফয়েড হয়েছিল- যাতে রঙলাল ডাক্তার এসেছিলেন- কিশোর যার নাম- তাঁর বাল্য বয়সটাই আমি। ... রঙলাল ডাক্তার সত্যকারের মানুষ। তিনি সাহিত্যিক ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ সহোদর।’
জীবনমশায়ের আরোগ্য-নিকেতনের সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। হয়ত এতক্ষণে মহুগ্রাম ঘুরে দেখেছেন। ভাবছেন ‘মহুগ্রাম কি তবে ‘গণদেবতা’র মহাগ্রাম!’ সে আলোচনা পরে হবে, চলুন ‘রঙলাল’ ডাক্তারের সন্ধান করি। লেখক নিজেই তো তার সূত্র দিয়ে দিয়েছেন, ‘রঙলাল ডাক্তার থাকেন এখান থেকে মাইল চারেক দূরে। এ অঞ্চলে তিনিই প্রথম অ্যালোপ্যাথি নিয়ে এসেছেন।’
(৩)
বেশ কিছুটা দূরে যেতে হবে যখন, ততক্ষণ উপন্যাসের পাতায় চোখ রাখা যেতেই পারে। জীবনমশায় তখন বালক। তাঁর পিতা জগৎমশায় নাম করা কবিরাজ। জীবনের স্বপ্ন তিনি পাশ করা ডাক্তার হবেন। এলাকার দুইজন চিকিৎসককে দেখে এই স্বপ্ন তাঁর মনে দানা বেঁধেছে। তাঁদের একজন ভুবন ডাক্তার। তিনি কলে যান ঘোড়ায় চেপে। অন্যজন রঙলাল ডাক্তার। তিনি আসা যাওয়া করেন পালকিতে।
রঙলাল ডাক্তারের কথা অনেকবার এসেছে উপন্যাসে। তিনি ‘অদ্ভুত চিকিৎসক। প্রতিভাধর ব্যাক্তি। মেডিক্যাল কলেজ বা ইস্কুলে তিনি পড়েন নি; নিজে বাড়িতে চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন। নদী থেকে, শ্মশান থেকে শব নিয়ে এসে গ্রন্থের নির্দেশ অনুসারে কেটে অ্যানাটমি শিখেছেন। বিস্ময়কর সাধনা। তেমনি সিদ্ধি। ... এসেছিলেন এ জেলায় হাই ইংলিশ ইস্কুলে শিক্ষকতার কর্ম নিয়ে। ইংরাজিতে অধিকার ছিল নাকি অসামান্য। আর তেমনি ছিল অগাধ আত্মবিশ্বাস। ... তিনি হঠাৎ কোনও আকর্ষণে ময়ূরাক্ষী –তীরে নির্জন একটি গ্রামে এসে এই সাধনা করেছিলেন তপস্বীর মতো। তারপর একদিন বললেন চিকিৎসা করব। এবং কিছুদিনের মধ্যেই এই অঞ্চলে অসামান্য প্রতিষ্ঠা লাভ করলেন। রঙলাল ডাক্তারের চিকিৎসার খ্যাতি রঙলালকেই প্রতিষ্ঠা দেয় নি- তাঁর সঙ্গে অ্যালোপ্যাথিরও প্রতিষ্ঠা করেছিল।’
ছাত্রজীবনে প্রেমে পড়া এবং তার পরবর্তী ঘটনা পরম্পরায় জীবন দত্তের সেই গরদের পাতলুন, বুকে সোনার চেনে বাঁধা সোনার পকেট ঘড়ি শোভিত গলাবন্ধ কোট পরে, থার্মমিটার-স্টেথোস্কোপ-কলবাক্স সহযোগে সাদা ঘোড়ায় চড়ে এই অঞ্চলে ঘুরে বেড়ানোর স্বপ্ন ভেঙে চুরমার গিয়েছিল। কলেজে পড়ার ইচ্ছাকে জলাঞ্জলি দিয়ে পিতার কাছেই কুলবিদ্যায় দীক্ষা নিয়েছিলেন। কবিরাজ হিসেবে সুনামও অর্জন করেছিলেন। তবে রঙলাল ডাক্তারের প্রতি মুগ্ধতা তাঁর যায় নি। অ্যালোপ্যাথি শেখার জন্যে শেষপর্যন্ত গিয়েছিলেন রঙলালের কাছে। কিছুটা শিক্ষা গ্রহণ করলেও মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদের মতো বীভৎস দৃশ্য সহ্য করতে পারেন নি। রঙলাল বিরক্ত হয়েছিলেন। আসলে তিনি চেয়েছিলেন জীবনকে চিকিৎসক হিসেবে তৈরি করতে কিন্তু বুঝতে পেরেছিলেন, যেমনটা তিনি চেয়েছিলেন তেমন হবার নয়। তাই বলেছিলেন, ‘তোমার ডাক্তারি শেখাটা বোধ হয় ঠিক হল না জীবন। ওই সব বিচিত্র অবিশ্বাস্য মুষ্টিযোগ নিয়ে যদি গবেষণা করতে পারতে! কিন্তু তাও পারতে না তুমি। তোমার সে বৈজ্ঞানিক মন নয়। কার্য হলেই তোমার মন খুশী। কেন হল- সেই অনুসন্ধিৎসা তোমার মনে নাই। যাক তুমি বরং ডাক্তারি, কবিরাজি, মুষ্টিযোগ তিনটে নিয়েই তোমার ট্রাই সাইকেল তৈরি করো। ওতে চড়েই তোমার যাত্রা শুরু করো।’
কাহিনির ‘রঙলাল’ বাস্তবে ছিলেন রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায়। মহুগ্রাম-লাভপুর ছাড়িয়ে আপনি উত্তরের যে অঞ্চলে পা রেখেছেন আজও সেই অঞ্চলে উনবিংশ শতাব্দীর কিংবদন্তী চিকিৎসক রঙ্গলালের নাম লোকের মুখে মুখে ফেরে। বৃহত্তর সমাজে তাঁকে ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হিসেবে পরিচয় দেওয়ার প্রয়োজন হলেও এখানে হয় না।
১২৫০ (১৮৪৩ খৃষ্টাব্দ) বঙ্গাব্দে ২৪শে আষাঢ় উত্তর চব্বিশপরগণার রাহুতা গ্রামে রঙ্গলালের জন্ম। কৈশোরে বাবা মাকে হারান তিনি। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনিই জ্যেষ্ঠ। কাজেই বিদ্যালয়ের পাঠ শেষ না করেই তাঁকে চাকরির সন্ধান করতে হয়। ততদিনে যেটুকু বিদ্যাশিক্ষা করেছিলেন তা স্কুলে শিক্ষকতা করার জন্যে যথেষ্ট। প্রথমে হুগলী অঞ্চলে এবং পরে ইছাপুরে শিক্ষকতা করেন। সেই সময় তিনি বারে বারে ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন। ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রক্ষা পেতে ইছাপুর ছেড়ে কলকাতায় যান। সেবারে চাকরি টাঁকশালে। কলকাতায় গিয়েও ম্যালেরিয়ার হাত থেকে পরিত্রাণ পান নি। আবার আক্রান্ত হয়েছেন। শেষে হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে একজন আত্মীয়ের কাছে গেলেন উত্তরপ্রদেশের গাজিপুরে। রোগমুক্তি ঘটলে সেখানকার পুলিশ বিভাগে চাকরি নিলেন। কিন্তু সে চাকরিও ভালো লাগল না। অতঃপর তিনি এসে পৌঁছলেন বীরভূমের দাঁড়কা গ্রামে। মাইনর স্কুলে প্রধান শিক্ষক হিসাবে যোগদান করলেন। সময়টা ১২৭৩ বঙ্গাব্দ। তখন রঙ্গলাল তেইশ বছরের তরুণ। স্কুলের পড়া শেষ করতে না পারলেও তিনি স্বভাবে ছিলেন জ্ঞান তপস্বী। নানারকম পেশায় কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে নিরলস জ্ঞানের চর্চা করে গিয়েছেন। সংস্কৃত, ইংরাজি, গণিত এবং চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সুযোগ মতো পণ্ডিতদের সহায়তা গ্রহণ করেছেন।
বছর পাঁচেক শিক্ষকতা করার পর রঙ্গলাল স্কুলের চাকরি ছেড়ে চলে যান দাঁড়কার অদূরে লাঘোষা গ্রামে। ময়ূরাক্ষীর তীরবর্তী নির্জন জায়গায় তৈরি করেন নিজের বাসগৃহ। শোনা যায় সেই বাড়িতে একটি কাঁচের ঘর তৈরি করেছিলেন। একজন ডোম ছিল তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর। ময়ূরাক্ষীতে বেওয়ারিশ মৃতদেহ ভেসে এলে সে মৃতদেহ তুলে এনে সে রঙ্গলালকে দিত। রঙ্গলাল তাঁর কাঁচের নিভৃত ঘরটিতে শব ব্যবচ্ছেদ করতেন আর বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেন। লোকে ভাবত তিনি নিভৃতে তন্ত্র সাধনা করেন। এভাবেই তিনি নিজে নিজে চিকিৎসাবিদ্যা আয়ত্ত করেছিলেন। চিকিৎসক হিসেবে তাঁর খ্যাতি বীরভূম ছাড়িয়ে বর্ধমান ও মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল। চিকিৎসা করে প্রভূত অর্থ উপার্জন করে ১২৯০ বঙ্গাব্দে তিনি একটি ছাপখানা তৈরি করেছিলেন। ভাই ত্রৈলোক্যনাথের সঙ্গে যুগ্মভাবে বাংলা ভাষায় প্রথম বিশ্বকোষ প্রকাশ করতে শুরু করেন। কিন্তু ত্রৈলোক্যনাথ বিলেত চলে যাওয়ায় প্রকাশনার সত্ত্ব তুলে দিতে হয় নগেন্দ্রনাথ বসুর হাতে। রঙ্গলাল আবার ফিরে আসেন লাঘোষায়। তারপর আমরণ সেই গ্রামেই ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে এই অঞ্চলের ভয়াবহ ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত, নিউমোনিয়া, যক্ষা পীড়িত লক্ষ লক্ষ আর্তজনের চিকিৎসা করে ১৩১৬ বঙ্গাব্দের ১৭ই কার্তিক মৃত্যু বরণ করেন। তাঁর নির্দেশ মতো মৃত্যুর পর তাঁকে দাহ না করে সমাহিত করা হয় ময়ূরাক্ষীর তীরেই।
এতক্ষণে যদি লাঘোষায় পৌঁছে গিয়ে থাকেন গ্রামের মানুষ আপনাকে ‘রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মৃতি প্রাথমিক বিদ্যালয়’খানি নিশ্চয় দেখাবে। দেখাবে রঙ্গলালের আবক্ষ মূর্তি। সেসব দেখে আপনি পৌঁছে যাবেন মহানগরীর কোলাহল থেকে অনেক দূরে, নিভৃত-নির্জন তৃণ আচ্ছাদিত রঙ্গলালের সমাধিস্থলে। সমাধির মর্মর ফলকে আপনার চোখ আটকে যাবে।
রঙ্গলাল কোনও সাধারণ শিক্ষক বা চিকিৎসক ছিলেন না। তিনি ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী। বিদ্বান, বিজ্ঞানমনস্ক এবং নিরলস কর্মযোগী এই মানুষটিকে নবজাগরণের একজন পথিকৃৎ বললেও অত্যুক্তি হবে না। তাঁর সময়কাল তো সেই উনবিংশ শতক, যে সময় বঙ্গসমাজে জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য ক্ষেত্রে প্রবল আলোড়ন উঠেছিল।
সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, সমাজ এবং ভারতীয় ঐতিহ্য সব ক্ষেত্রেই রঙ্গলালের ছিল অবাধ বিচরণ। তাঁর কাব্যপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের রাজা মহাতাপ চাঁদ তাঁকে ‘কাব্য রত্নাকর’ উপাধি দিয়েছিলেন। সেই আমলে তিনি লাঘোষায় একটি ধর্মসভা গড়ে তুলেছিলেন। অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও ইতিহাস বিষয়ক প্রবন্ধ লিখেছিলেন। রচনা করেছিলেন নাটক ও উপন্যাস। এই যে সামনের মর্মর ফলকটি আপনি পড়ছেন, তাতে রয়েছে তাঁরই রচনা করা শ্লোক।
‘দয়াসিন্ধুর্মহাযোগী বিশ্বকোষ প্রবর্তকম্।
জিয়াচ্চিরং রঙ্গলালো হৃদয়ে বিশ্ববাসিনাম্।।‘
অর্থাৎ দয়াসিন্ধু এবং মহাযোগী, যার দ্বারা বিশ্বকোষ প্রবর্তিত হয়েছিল, সেই রঙ্গলাল বিশ্ববাসীর হৃদয়ে বিরাজ করছেন।
রঙ্গলালের জন্ম-মৃত্যুতিথির নিচেই লেখা,
‘ঘটস্থং যাদৃশম ব্যোম ঘটেভগ্নে হপি তাদৃশম্।
নষ্টে দেহে তথ্যৈবাত্মা সমরূপো বিরাজতে।।’
অর্থাৎ ঘট সদৃশ এই দেহ পরিত্যক্ত হলে, আত্মা আদিরূপেই অবস্থান করে।
১৯৭৮ সালের ময়ূরাক্ষীর বন্যায় এই সমাধিক্ষেত্র ক্ষতিগ্রস্ত হলে পুনরায় তা নির্মাণ করা হয়েছে।
রঙলাল ডাক্তারের কথা জানার পরও যদি কৌতূহল অবশিষ্ট থাকে ঘোড়ায় চেপে চিকিৎসা করতে যাওয়া ভুবন ডাক্তারের কথা জানার, তবে সে কৌতূহলও মিটবে। ময়ূরাক্ষীর পাড় ধরে আরও কয়েক কিলোমিটার ভ্রমণ করে আধঘণ্টার মধ্যে আপনি পৌঁছে যাবেন ভোগপুর গ্রামে। ভোগপুরের জটিলেশ্বর ঘোষ ওরফে জটিল ডাক্তারের কথা আজও লোকে ভোলে নি। রঙ্গলাল উনবিংশ শতাব্দীর চিকিৎসক ছিলেন। জটিল ডাক্তার বিংশশতাব্দীর। তিনি তারাশঙ্করের বন্ধু ছিলেন। আর জীবনমশায় অর্থাৎ মাখনলাল দত্ত ছিলেন তারাশঙ্করের আর এক বন্ধু জগবন্ধুর জ্যাঠামশায়। তিনজনই তাঁর দেখা ভিন্ন সময়কালের মানুষ। কাহিনির প্রয়োজনে তিনি সকলকে একত্রিত করেছিলেন।
তাঁর অশ্বপ্রীতির কথাও বহুল প্রচলিত। প্রতিদিন বিকেলে নিয়ম করে ঘোড়া চড়াতেন। নিজে ঘোড়ার জন্যে ঘাস কাটতেন। অনেকে সেই সময় ডাক্তারের সন্ধানে এসে তাঁর কাছেই ডাক্তারের খোঁজ করত। খুব আশ্চর্যজনক ভাবেই ঘোড়ার কামড়ে সেপ্টিক হয়ে মৃত্যু হয়েছিল তাঁর।
(৪)
‘আরোগ্য-নিকেতন’ উপন্যাসের বিষয়বস্তুর সঙ্গে তারাশঙ্করের যে নিবিড় যোগাযোগ ছিল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর প্রথম জীবনে লোকহীতকর কাজে আত্মনিয়োগের কথা অল্প বিস্তর সকলেই জানেন। কলেরা রোগীর সেবা অথবা সর্পদংশনের প্রাথমিক চিকিৎসায় তাঁর দক্ষতা ছিল। ‘ধাত্রীদেবতা’র ফ্যালা ডোমের স্ত্রী বা ‘কবি’ উপন্যাসে স্বৈরিণী, ঝুমুর দলের নর্তকী বসনের চিকিৎসা করেছিলেন নিজে।
‘আরোগ্য-নিকেতনে’র পূর্বে তারাশঙ্করের একাধিক রচনায় উপজীব্য ছিল চিকিৎসক অথবা চিকিৎসা বৃত্তি। ১৯৩৪ সালে বঙ্গশ্রীর আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত ‘শ্রীনাথ ডাক্তার’, ১৯৪৪ সালে শারদীয়া আনন্দবাজার প্রকাশিত ‘বোবাকান্না’ এবং ১৯৪৫ সালের প্রসাদমালার শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত ‘দেবতার ব্যাধি’ গল্পগুলি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও আয়ুর্বেদ সম্পর্কে তাঁর আঞ্চলিক পর্যবেক্ষণ সুস্পষ্ট হয়েছে সর্পদংশনের চিকিৎসার ক্ষেত্রে। ‘নাগিনী কন্যার কাহিনী’র ধূর্জটি কবিরাজ ও শিবরাজ কবিরাজকে নিয়ে লেখায় তা ফুটে ওঠে।
‘আরোগ্য-নিকেতন’ তারাশঙ্করের পরিণত বয়সের সৃষ্টি। কেবল বাংলাসাহিত্য নয় সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যে এ রচনা বিশিষ্ট বলে স্বীকৃত। ১৯৫২ সালের শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ‘সঞ্জীবন ফার্মাসী’ নামে। ১৯৫৩ সালে পুস্তকাকারে প্রকাশ করার সময় নাম পরিবর্তন করে হয় ‘আরোগ্য-নিকেতন’। আপন স্বভাব অনুযায়ী বইটির দ্বিতীয় সংস্করণে তারাশঙ্কর অনেকখানি পরিমার্জন ও পরিবর্তন করেছিলেন। এই রচনার জন্য ১৯৫৫ সালে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কারে পুরস্কৃত হয়েছিলেন তারাশঙ্কর। পরের বছর লাভ করেছিলেন আকাদেমী পুরস্কার। ১৯৬৯ সালে সাহিত্য আকাদেমীর ফেলোশিপ প্রদানের সময় ‘প্রশস্তি-পত্রে’ বিশেষ করে ‘আরোগ্য-নিকেতন’ উপন্যাসের উল্লেখ করা হয়েছিল। সম্বর্ধনার উত্তরে ধন্যবাদ জানিয়ে তারাশঙ্কর বলেছিলেন ‘বাংলার পল্লী অঞ্চলের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে প্রাণলীলা প্রত্যক্ষ করেছি, সাহিত্যে তাকেই রূপদানের চেষ্টা করেছি।’
সাহিত্য আকাদেমী থেকে ‘আরোগ্য-নিকেতন’ মালয়ালম, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, তামিল, তেলুগু এবং হিন্দীসহ অনেকগুলি ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়।
---
তথ্যসুত্রঃ ১। https://roar.media/bangla/main/biography/the-roman-medical-scientist-who-was-the-doctor-of-the-gladiators
২। বিশ্বকোষ প্রবর্তক রঙ্গলাল মুখোপাধ্যায় স্মরণিকা; পরিকল্পনা ও সম্পাদনা সিরাজুল হক।
৩। ক’টি ছায়া ও একটি গল্প; (প্রবন্ধ) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪) জটিল ডাক্তার; প্রবন্ধ: মিছিল - প্রবন্ধ সংকলন; তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
তথ্যঋণঃ ডঃ সুকুমার চন্দ্র, সুভাষ আচার্য, কেদারনাথ আচার্য ও অলোক মিশ্র।
