
ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
- 15 August, 2021
- লেখক: নীতা মণ্ডল
১৩১২ সালের তিরিশে আশ্বিন। ভোরবেলা জেগে উঠেছে লাভপুর গ্রাম। এ ওকে, ও তাকে ডেকে ফিরছে। সকলে বেরিয়ে এসেছে ঘরের বাইরে। একজন বলল, ‘বঙ্গভঙ্গের দুঃখে হিন্দু-মুসলমান সবাই বেদনা পেয়েছে। কলকাতায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বিজ্ঞাপন দিয়ে বঙ্গবাসীর কাছে আর্জি জানিয়েছেন, রাখীবন্ধন করতে।’
এমন সময় স্কুলের বোর্ডিং থেকে ভেসে এল ‘বন্দেমাতরম’ ধ্বনি। সবাই সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াল। সে এক মস্ত মিছিল। মিছিলের সামনে বোর্ডিঙের ছেলেরা। গ্রামের রাস্তা ধরে মিছিল চলেছে। খোল করতাল বাজিয়ে বোর্ডিঙের ছেলেরা গান গাইছে,
‘বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল...’
মিছিল থামল গ্রামের প্রান্তে দেবী মন্দিরে। মন্দিরের সামনে দীঘির জলে স্নান সেরে উঠে সবাই একে অন্যকে আলিঙ্গন করল। পরস্পরের হাতে বেঁধে দিল হলুদে ছোপানো সুতো। হল রাখীবন্ধন।
এ দৃশ্য দেখে সাত বছরের বালক তারাশঙ্কর অভিভূত হলেন। ঘরে ফিরে আসতেই মা বড়মামার কাছ থেকে একটি রাখী নিয়ে বেঁধে দিলেন তারাশঙ্করের হাতে। মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করলেন,
‘বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল,
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক হে ভগবান...’

আর পাঁচজন শিশুর মতো তারাশঙ্কর শৈশবে গল্প শুনতে ভালোবাসতেন। তাঁর মা প্রভাবতীদেবী ছিলেন চমৎকার কথক। তিনি একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে সামনে থেকে দেখেছিলেন। ছেলের কাছে প্রভাবতীদেবী বড় বড় মনীষীদের, সাধকদের কথা বলতেন। কখনই বিত্তবান মানুষের গল্প বলতেন না। কাহিনি শেষে কখনও কখনও স্বগতোক্তি করতেন, ‘হ্যাঁ যদি হতে হয়, এমনই মানুষের মা হতে হয়।’ সম্ভবত সেই কারণে তারাশঙ্করের ধারণা হয়, কীর্তিমান মানুষ মানে বড় মানুষ। বড়লোক নয়।
তারাশঙ্করের বাবা হরিদাসের বৈঠকখানার মজলিশ ছিল বিখ্যাত। বহু বিচিত্র মানুষ সেখানে আসত। প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত চলত মজলিশ। কেউ বাইরে চাকরি করে, সে বাড়ি ফিরে চাকরি জায়গার গল্প বলত। কেউ তীর্থ করে ফিরেছে, সে এসে ভাগ করে নিত আপন অভিজ্ঞতা। এছাড়া সাধু সন্ন্যাসীদের প্রতি হরিদাসের আকর্ষণ থাকায়, তাঁরাও আসতেন। তাঁরা বলতেন দূর বিদেশ, পাহাড় ও নদীর গল্প। তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন রামজী গোঁসাই। সন্ন্যাস গ্রহণের পূর্বে তিনি সিপাই ছিলেন। তিনি যুদ্ধের গল্প বলতেন। গোঁসাইজীর গল্পের আকর্ষণে রাতে ঘুমোতে যেতে চাইত না বালক তারাশঙ্কর।
পিসিমার কাছে শুয়ে গল্প শুনতে চাইলে একটাই গল্প পিসিমা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতেন, ‘এই সিঁদুর দিয়ে রাঙিয়ে রক্তমাখা মুখ, হাতে এই রক্তমাখা টাঙি। কাঁধে তির ধনুক। ধি-তাং-তাং, ধি-তাং-তাং শব্দে মাদল বাজাতে বাজাতে এসে পড়ল। যাকে দেখলে তাকে কাটলে টাঙির ঘায়ে। যে পালাল তাকে মারলে কাঁড়, কাঁড় মানে লোহার ফলাওলা দু হাত লম্বা তির। ভদ্রলোকে যে যেদিকে পারলে পালালে।’
আপন গৃহের অঙ্গনের বাইরে তারাশঙ্করের দুনিয়া অর্থাৎ তাঁর গ্রাম লাভপুর ছিল বৈচিত্রে পরিপূর্ণ। ভৌগলিক কারণে সেখানে আদিবাসী, বাউরি, হাড়ি, বাগদী, চন্ডাল, ডোম, কাহার, বেদে ইত্যাদি জনজাতির বাস। আপন গ্রামেই উচ্চবর্ণ ব্রাহ্মণ, শতাব্দীপ্রাচীন বনেদী জমিদার, অভিজাত শ্রেণী, দরিদ্র, চোর-লাঠিয়াল-ঠ্যাঙাড়ে, সাধক এবং পাষণ্ড নানা স্তরের ও বিচিত্র জীবিকার মানুষের সঙ্গে ছোটবেলাতেই পরিচয় গড়ে উঠল তারাশঙ্করের। তারপর যখন তাঁর সাত বছর বয়স তখন বাংলাদেশে সেই অদ্ভুত দিনটি এল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে রাখীবন্ধনের দিন, যে দিনের কথা দিয়ে এই লেখার শুরু। সেই দিনটা বালক তারাশঙ্করের জীবন ও চিন্তায় এক গভীর ছাপ তৈরি করে, যা পরে ক্রমশ ডালপালা মেলেছে।
চলে আসা যাক বছর তিনেক পরের কথায়। এর মাঝে তারাশঙ্করের পিতৃবিয়োগ হয়েছে। মা ছোটছোট ভাইবোনদের নিয়ে ব্যস্ত থাকেন। তারাশঙ্করের নাওয়া, খাওয়া, ঘুম সব পিসিমার কাছে। মায়ের প্রতি তাঁর কিছুটা সম্ভ্রম মিশ্রিত ভয় আছে। সেবার পিসিমা তীর্থে যাওয়ায় রাতে মা’র কাছে শুতে হল। ঘুম আসছে না। গভীর রাতে একমনে জানলার বাইরে চেয়ে আছেন। মা দেখতে পেয়ে বললেন, ‘কিরে ঘুম আসছে না।...বই পড়ি, শোন।’ পড়তে শুরু করলেন ‘কপালকুণ্ডলা’। তারাশঙ্কর আছন্ন হয়ে গেলেন মায়ের পাঠের মাধুর্যে। অনুচ্ছেদ শেষ হল, ‘প্রদীপ নিভিয়া গেল’।
তারাশঙ্করের মনোজগতে যেন আলো জ্বলে উঠল। অবাক হয়ে ভাবলেন, এমন সুন্দর কথাও লেখা যায়! প্রদীপটি নেভার আগে কিশোর তারাশঙ্করের মনের প্রদীপে অগ্নি সংযোগ ঘটিয়ে দিল।
কিছুদিন বাদে তারাশঙ্কর গ্রামের সমাজ-সেবক সমিতির সদস্য হলেন। মহামারি, দুর্ভিক্ষ, খরা, বন্যা অথবা অগ্নিকান্ডে মানুষের পাশে ছুটে যান। রাত বিরেতে, ভিন্ন গ্রামে বিপদ হলে ছোটদের নেওয়া হয় না। তারাশঙ্কর তখন চোদ্দয় পড়েছেন। গ্রীষ্মকালের এক রাত্রে গ্রামের উত্তরদিক থেকে ভেসে এল চিৎকার, ‘আগুন আগুন’। আগুনের শিখায় লাল হয়ে উঠেছে গ্রামের মাথা। তারাশঙ্কর ছুটে গেলেন। পেছন থেকে মা, পিসিমা ডাকলেন। সে ডাক তাঁর কানে প্রবেশ করল না। তিনি চলে গেলেন প্রতিবেশী গ্রামে। মই বেয়ে উঠে আগুনে জল ঢেলে সকলে মিলে আগুন নেভালেন। ফিরে এলেন শরীরে বেশকিছু ফোস্কা ও ক্ষতচিহ্ন নিয়ে। গ্রামের বয়স্করা বলল, ‘ছেলেটা দেখতে দেখতে ডাঁটো হয়ে উঠল গো।’
বাঁধন ছেঁড়া দুরন্ত কৈশোরের ডাক সত্যিই পেলেন তারাশঙ্কর। কতদিকে তাঁর মন ছুটে যায়! পরাধীনতার গ্লানি এবং সমাজের নীচের তলায় পড়ে থাকা বৃহৎ সংখ্যার মানুষের যন্ত্রণা ও বঞ্চনা অস্থির করে তোলে। স্বামী বিবেকানন্দের সন্ন্যাসীরূপ মুগ্ধ করে। উদ্বেল করে কিশোর ক্ষুদিরামের ফাঁসির সংবাদ। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতায় তারাশঙ্কর আপন আত্মার বাণী শুনতে পানঃ
‘এই- সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে
দিতে হবে ভাষা, এই-সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা।’
এত কিছুর মাঝে তারাশঙ্কর কবিতাও লেখেন। তার জন্যে স্কুলে তিরস্কৃত হন। তবুও গ্রামীণ সাহিত্য সভায় নিজের কবিতা পাঠ করেন। দুর্গাপুজোর মণ্ডপে টাঙিয়ে দেন নিজের লেখা কবিতা। ম্যাট্রিক পাশ করে তারাশঙ্কর পড়তে যান কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। সেখানে বিপ্লবীদের সংস্পর্শে আসেন। সেই বারই পুজোর ছুটিতে বাড়ি এসে একদিন বাল্যবন্ধুদের সঙ্গে হইচই করে সন্ধ্যেবেলায় ফিরে দেখলেন বৈঠকখানায় একজন অপরিচিত মানুষ বসে রয়েছেন। পথে রাত হয়ে যাওয়ায় এখানেই আশ্রয় নিয়েছেন। তারাশঙ্কর গল্পে মেতে গেলেন। ভদ্রলোক মনযোগ দিয়ে সব কথা শুনছেন দেখে উৎসাহিত হয়ে অনেক কথা বলে ফেললেন। নিজের স্বপ্নের কথা বললেন। নিজের লেখা কবিতা শোনালেন। সেবার পুজোর কবিতায় দেশমাতৃকাকে জেগে ওঠার মিনতি জানিয়েছেন তিনি;
‘মাটির হাতে আর খেলার প্রহরণ
জননী মিছে তুমি ধরো না ধরো না’
ছুটির শেষে কলকাতায় ফেরার পর তারাশঙ্করের খোঁজে এল একদল পুলিশ। সেই দলে সেই ভিনদেশী পথিকও রয়েছেন। গোয়েন্দা সাব ইনস্পেক্টর। বিল্পবী দলের সঙ্গে তারাশঙ্করের যোগাযোগ আছে কিনা অনুসন্ধান করতেই সেবার লাভপুরে গিয়েছিলেন তিনি। ‘ডিফেন্স অফ ইন্ডিয়া’ আইনে তারাশঙ্কর গৃহবন্দি হলেন।
শুরুতে বিপ্লবীদের প্রতি আকৃষ্ট হলেও পরে যুবক তারাশঙ্কর গান্ধীজীর অহিংসার পথ অবলম্বন করলেন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিলেন। পল্লী উন্নয়ন ও সেবার মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করলেন। প্রায় এক দশক কাল ধরে জনসেবার এক অভূতপূর্ব নজির রাখলেন তারাশঙ্কর। ১৯২৪-২৫ সালে লাভপুরের আশেপাশে কলেরা এসেছিল মহামারি রূপে। সেই বারে ত্রিশ-চল্লিশটি গ্রামের মানুষের জন্যে ছয়মাস ধরে কাজ করেছিলেন। মানুষগুলির বেশিরভাগই ছিল অন্ত্যজশ্রেণীর। জেলখাটা আসামী থেকে দেহপোজীবিনী স্বৈরিণী কেউ তাঁর সেবা থেকে বঞ্চিত হয় নি। পরে একটি বাই-ইলেকশনে জিতে ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন তারাশঙ্কর।
১৯৩০ সালের ২ জানুয়ারি লাহোর কংগ্রেস কমিটির বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, সেই বার ২৬ জানুয়ারি দেশ জুড়ে ‘পূর্ণ স্বরাজ’ বা ‘স্বাধীনতা দিবস’ উদযাপন করা হবে। সেই উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধী রচিত একটি শপথবাক্য বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় অনুবাদ করে দেশের গ্রামে গ্রামে পাঠানো হয়েছিল। তারাশঙ্কর লাভপুরে পতাকা উত্তোলনের উদ্যোগ নিলেন। বাধা এল দুদিক থেকে। প্রশাসনিক স্তরের একজন অফিসার সাবধান করলেন, এর জন্যে জীবনে বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হবে তাঁকে। ভবিষ্যতে তাঁর সন্তানদেরও এর ফল ভোগ করতে হবে। অন্যদিকে, পতাকা তুলবার জন্য তিনি যে স্থানই নির্বাচন করতে গেলেন, গ্রামের জমিদারেরা এসে বাধা দিল। শেষ পর্যন্ত ফুল্লরা মন্দিরের উত্তরে একটি পতিত জমিতে পতাকা উত্তোলন হল। তেরঙ্গা পতাকা। মাঝখানে চরকার ছবি।
সেবা সমিতির সদস্যদের সঙ্গে তারাশঙ্কর শপথবাক্য পাঠ করলেন, ‘যে কোনও দেশবাসীর মতো ভারতবাসীরও অবিচ্ছেদ্য অধিকার রয়েছে স্বাধীনতা আর যাতে আত্মবিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ মেলে, তার জন্য নিজ শ্রমের ফলভোগের ও জীবনধারণের পক্ষে প্রয়োজনীয় উপকরাণদি পাওয়ার—এই আমাদের বিশ্বাস। আমাদের বিশ্বাস, কোনও সরকার যদি ওই সব অধিকার থেকে কোনও জাতিকে বঞ্চিত করে ও তার উপরে অত্যাচার চালায়, তবে সে জাতির অধিকার আছে ওই সরকার পরিবর্তনের, উচ্ছেদ সাধনের।’
আইন অমান্য আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণেই ১৯৩০ সালে তারাশঙ্কর কারাবন্দি হয়েছিলেন। জেলে থাকাকালীন তাঁর চোখে পড়েছিল রাজনৈতিক ব্যক্তিদের ভণ্ডামি ও নীচতা। তখনই তিনি স্থির করেছিলেন সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে আসবেন।
জেল থেকে বেরিয়ে এসে ভাইকে সঙ্গে নিয়ে বোলপুরে একটি ছাপাখানা খুললেন তারাশঙ্কর। তখন বীরভূমের জেলাশাসক ছিলেন গুরুসদয় দত্ত। ব্রতচারী আন্দোলনকে কটাক্ষ করে একটি প্যারোডি কবিতা ছাপা হয়েছিল সেই প্রেস থেকে। তাতেই গুরুসদয় দত্ত চটে গেলেন। প্রেসে খানাতল্লাশি হল। দুহাজারটাকা জরিমানা ধার্য হল। এরই মাঝে বোলপুরে তারাশঙ্করের সাক্ষাৎ ঘটল নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সঙ্গে। তাঁর কাছে তারাশঙ্কর ঘটনাটি খুলে বলেছিলেন। শেষ পর্যন্ত নেতাজীর পরামর্শ অনুযায়ী তিনি জরিমানা দিতে অস্বীকার করেছিলেন। ফলে প্রেস বন্ধ করে দিতে হয়েছিল।
দুর্ভোগের সেখানেই সমাপ্তি ঘটে নি। বীরভূমের তৎকালীন এস পি সামসুদ্দাহ তারাশঙ্করকে বিষ নজরে দেখতেন। কোনও না কোনও উপায়ে রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধে তারাশঙ্করকে আবার জেলে পাঠাতে তিনি উঠে পড়ে লেগেছিলেন।
তারাশঙ্কর চলে গেলেন কলকাতায়। নানান প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও রচনা করে গেলেন ছোট ছোট গল্প। ধীরে ধীরে সাহিত্য এবং কলকাতা শহর, দুটি জায়গায় তারাশঙ্করের আসন পাকা হল। নিরলস সাহিত্যসেবা করে তিনি পার করে দিলেন এক দশকেরও অধিক সময়।
এল ১৯৪২ সাল। অগাস্ট মাসে মহাত্মা গান্ধী ডাক দিলেন ‘ভারত ছাড়ো’। সেই ডাকের প্রতিধ্বনি হল বাংলার ঘরে ঘরে। ঠিক সেই সময় বন্যা ও সাইক্লোনে বিধ্বস্ত হল মেদিনীপুর। বিপর্যস্ত মানুষকে ইংরেজ শাসক ভাতে মারার ব্যবস্থা করল। তবুও মেদিনীপুরবাসী বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে লড়াই করল এবং মৃত্যুবরণ করল। ডিসেম্বর মাসে জাপানের সেনাবাহিনী কলকাতায় বোমা ফেলল। কলকাতার অবস্থা হল ভয়াবহ। আকাশে উড়ল এরোপ্লেনের ঝাঁক। সাইরেন বাজল। ব্ল্যাক-আউট হল। এই ধ্বংসলীলার হাত ধরে এল ১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষ। লক্ষ লক্ষ মানুষ অনাহারে রাস্তায় মরে পড়ে থাকল।
সেই বছর ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি গঠন করেছিল, ফ্যাসি বিরোধী সাহিত্যিক ও শিল্পী সংঘ (পরবর্তী দিনে যার নাম, প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স এ্যাসোসিয়েশন)। তৃতীয় বৎসরে তারাশঙ্কর সংঘের সভাপতি মনোনীত হয়েছিলেন। সদস্যদের সঙ্গে রাজনৈতিক মতবিরোধের জন্যে পরে তিনি সেই পদ ছেড়ে দেন।
তারাশঙ্কর তখন বাগবাজারে থাকেন। ১৯৪৬ সালের এগারোই ফেব্রুয়ারি আজাদ হিন্দ ফৌজের অন্যতম নায়ক রসিদ আলি খাঁর কারাদণ্ডের আদেশের প্রতিবাদে ছাত্ররা পথে নামে। প্রতিবাদ মিছিলে ছাত্রদের উপর অবাধে লাঠি চার্জ করা হয়। কলকাতার রাজপথ রক্তে ভেসে যায়। শুরু হয় আন্দোলন। যেন সমগ্র জাতির বুকে জমে থাকা পরাধীনতার গ্লানি আর ক্ষোভের বিস্ফোরণ ঘটে। আন্দোলন কলকাতা ছাড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ে হাওড়া থেকে চব্বিশ পরগণা পর্যন্ত। তাদের দমন করতে শাসক সর্বশক্তি প্রয়োগ করে। মোতায়েন হয় সশস্ত্র বাহিনী, গোরা পল্টন, মিলিটারি। ট্যাঙ্ক বসে শ্যামবাজার পাঁচমাথার মোড়ে। কলকাতার রাজপথ পরিণত হয় রণক্ষেত্রে।
মাত্র ক’মাসের ব্যবধান। অগাস্ট মাসে কলকাতার পথঘাট আবার রক্তে ভাসল। ফেব্রুয়ারি মাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি হিন্দু-মুসলমানের যে মিলিত উৎসাহ দেখা দিয়েছিল তার মূলে একটি অতি প্রাচীন সামন্ততান্ত্রিক কৌশল প্রয়োগ করল স্বার্থান্বেষী কিছু রাজনীতিবিদ। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তারা দলের অনুচরদের খেপিয়ে তুলল। মহম্মদ আলী জিন্না ‘ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে’ নামে দেশ জুড়ে একটি প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দিলেন। তারই ফলে ঘটল ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। জ্বলে ছাই হয়ে গেল ঘরবাড়ি, দোকানপাট। অগুনতি নিরীহ মানুষের প্রাণ গেল সেই হত্যালীলায়।
শেষ পর্যন্ত সাতচল্লিশ সাল এল। তারাশঙ্কর ততদিনে দেশের একজন অগ্রগণ্য সাহিত্যিক। জুলাই মাসে পঞ্চাশে পা দিয়েছেন। লাভপুর থেকে চিঠি এল। মা লিখেছেন, ‘তোমাকে আসতে হবে। লাভপুরে স্বাধীনতার পতাকা তোমাকেই তুলতে হবে। ...তোমার পিসিমা ও আমার ইহা একান্ত ইচ্ছা।’
চোদ্দই অগাস্ট বিকেলে তারাশঙ্কর নামলেন আমোদপুর ষ্টেশনে। একটি সাজানো ট্রলি এসেছে তাঁকে নিয়ে যেতে। একদল ছেলে ট্রলিটি ঠেলতে ঠেলতে পৌঁছল লাভপুরে। তখন সন্ধ্যে নেমেছে। তবুও প্রচুর মানুষ দল বেঁধে অপেক্ষা করছে। হ্যাচাকের আলোয় চারিদিক আলোকিত। তারাশঙ্করকে তারা স্বাগত জানাল। সেদিন মাঝরাতের নিরবতাকে ভেঙে দিয়ে লাভপুরের আকাশ বাতাস মুখরিত হল শঙ্খধ্বনিতে। শব্দবাজি ফাটল। কয়েকঘণ্টা বাদে স্বাধীন ভারতবর্ষের আকাশে প্রথম সূর্যোদয় হল। লাভপুরের বুকে তেরঙ্গা পতাকা তুললেন এ মাটির শ্রেষ্ঠ সন্তান, তারাশঙ্কর।
সাহিত্যঃ
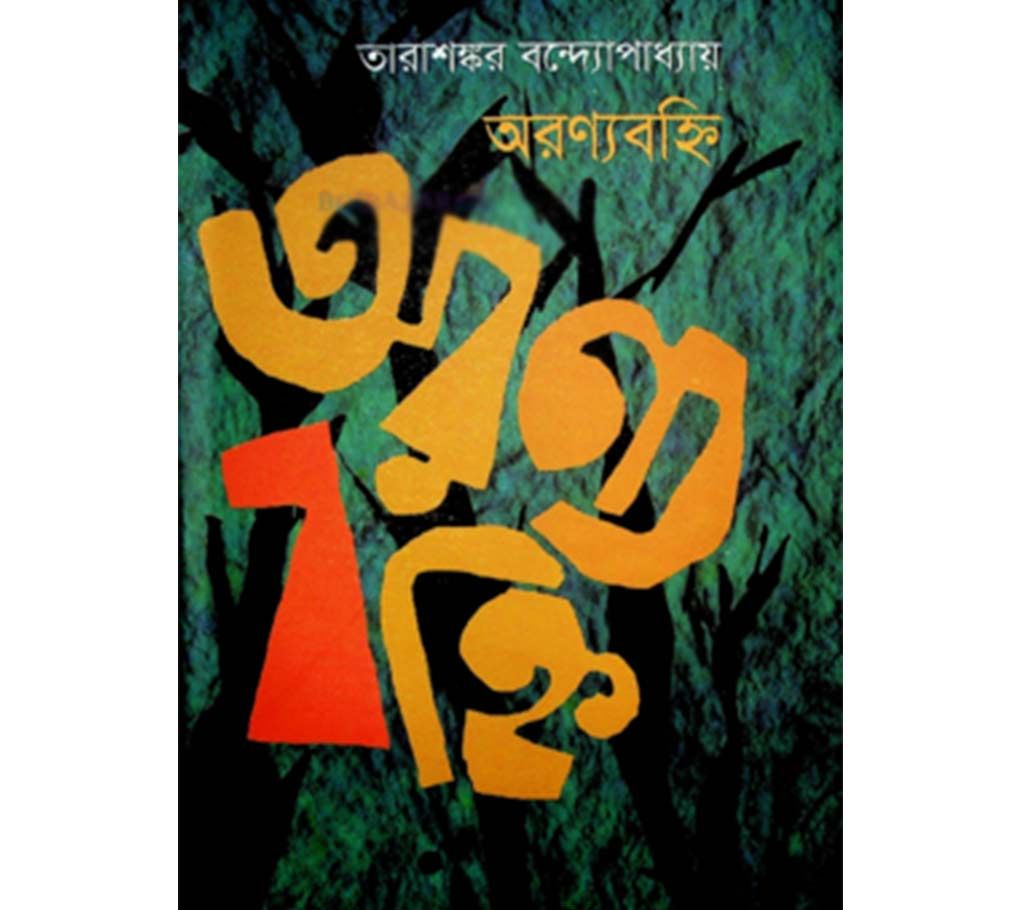
অরণ্য-বহ্নিঃ একবার দুমকা থেকে সাহেবগঞ্জে যাওয়ার পথে বন ও পাহাড়ের মাঝে তারাশঙ্করের গাড়ি খারাপ হয়ে গেল। তখন সন্ধ্যে নামছে। একদল সাঁওতাল সরকারী বাংলোর সন্ধান দিল। বাংলো পর্যন্ত গাড়িটিকেও ঠেলে পৌঁছে দিল। পারিশ্রমিক দিতে গেলে বলল, ‘আমাদের লিতে নাই। বারণ করে গেইছে আমাদের শুভোবাবু। সিধু আর কানহু আমাদের শুভোবাবু ছিল। সাঁওতালরা যখন হুলু করলে, সাহেবদের সঙ্গে লড়াই করলে তখুন তারা বলে গেইছে কি- দেখ মানুষের জখুন বিপদ হবে তখন তাকে বাঁচাবি, রাখবি, নিজের জানটা দিবি, কিছু লিবি না তার কাছে। আমাদিগে টাকা লিতে নাই বাবু।’
জঙ্গলের দিকে দেখিয়ে ওরা বলল, ‘উইখানে আমাদের শুভোবাবু সিধু কানু তুদের দুগগাপুজো করেছিল সে হুলুর সময়ে।... কিন্তুক কি দোষ হল – হেরে গেল। সিধু মল গুলিতে কানহুর ফাঁসি হল।’
সেদিন রাতে তারাশঙ্করের ঘুম এল না। সঙ্গে বীরভূম জেলার হ্যান্ডবুক ছিল। পড়তে পড়তে দেখলেন আলি হান্টার লিখেছেন, ‘... two brothers inhabitants of a village (Bagnadihi) that have been oppressed beyond bearing by Hindu usuary, stood forth as the deliverers of their countrymen, claimed a divine mission, and produced heavensent tokens as their credentials. The god of Santals, they said had appeared to them on seven successive days; next as a flame of fire, with a knife glowing in the midst; then in the form of wheel of a bullock cart.
... carried off Brahman priests to perform the great October festival (Durgapuja)’
তারাশঙ্করের চোখের সামনে ভেসে উঠল সাঁওতালদের বিজয়াদশমীর উৎসব। মাথায় ময়ূরের পালক গুঁজে, মাদল বাজিয়ে নাচ। পরদিন বন ঘুরে দেখলেন। চারিদিকে উঁচু উঁচু শালগাছের মাঝে মা বোঙ্গার ঠাঁই অর্থাৎ দুর্গাপুজোর স্থানটি খুঁজে পেলেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের পূর্বে সাঁওতাল পরগণা ও বীরভূম একই প্রদেশ ছিল। ছোটবেলায় তারাশঙ্করের পিসিমা এই বিদ্রোহের কাহিনিই শোনাতেন তাঁকে। পিসিমার দিদিমা, যার কাছে পিসিমা সে গল্প শুনেছিলেন এ বিদ্রোহের সময় তিনি জীবিত ছিলেন।
সাঁওতাল বিদ্রোহের একশ কুড়ি বছর পর সিধু কানুর কথা খুঁজতে তারাশঙ্কর গ্রামের পর গ্রাম পাড়ি দিলেন। শেষ পর্যন্ত খোঁজ মিলল চরণপুর গ্রামে। সেখানে থাকে একজন মৃৎশিল্পী, নয়ন পাল। নবতিপর বৃদ্ধ। তারই ঠাকুরদা সাঁওতালদের দুর্গা প্রতিমা গড়েছিলেন। তার জ্যাঠা সিধু কানুর সঙ্গে হুলে যোগ দিয়েছিলেন। সিউড়ি আদালতে বিচারে তাঁর সাত বছর জেল হয়। নয়ন পালের বাবা সমগ্র হাঙ্গামার খুঁটিনাটি পটে এঁকে রেখেছেন। তাতে সাহেবদের অত্যাচারের কথা আছে। আছে হিন্দু মহাজনদের পাপের কথাও। নয়ন পালের কাছে পটের গান শুনে শৈশবে শোনা কাহিনিকে কল্পনার রঙে রাঙিয়ে উপন্যাস লিখলেন। বিদেশী শাসক, বাঙালি মহাজন এবং পশ্চিমা ব্যবসায়ীদের শোষণে কী ভাবে আদিম অরণ্যচারী জাতি ধ্বংসের মুখে পড়েছিল সেই কাহিনি লিপিবদ্ধ হল ‘অরণ্য-বহ্নি’তে।
বর্ণিত হল সাঁওতালদের রুখে দাঁড়ানোর কাহিনি। সিধু যেন স্ফুলিঙ্গ। তার ঝলকানিতে আগুন ছড়িয়ে পড়ল প্রতিটি সাঁওতালের মনে,
‘সিধু বললে- ই আমাদের দেশ, আমরা লিব।
সিধুর সঙ্গে সঙ্গে কানু একসঙ্গে বলে উঠল – হ, ইটো আমাদের দেশ বটে। আমাদের দেশ।
চমকে উঠল বিশু। শুধু বিশু কেন, সিধু কানু- নিজেরা বলেও নিজেরাই এ কথায় চমকে উঠল- আমাদের দেশ! ... সেই রাত্রির অন্ধকারে নিজেদের এই আশ্চর্য কথা দুটি তাদের সারা অন্তরে চকিত একটি বিদ্যুৎরেখা টেনে দিয়ে, মেঘের ডাকের মতো বেজে উঠল- ই আমাদের দেশ।’

কালিন্দীঃ কালিন্দী মানবপ্রেমের কাহিনি। এই মানবপ্রেম মৃত্তিকাপ্রেম থেকে উদ্ভূত। অহীন্দ্র নামে একজন জমিদারতনয়কে ঘিরে কাহিনি গড়ে উঠলেও মৃত্তিকা অর্থাৎ কালিন্দীর চর এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র। নদীর স্রোতে বয়ে আসা বালি ও পলিমাটি জমে গড়ে উঠে চর। এর সন্ধান প্রথমে পায় যারা সত্যিকারের ‘মাটির মানুষ’। খাদ্যের দাবী ছাড়া মাটির কাছে তাদের আর কোনও দাবী নেই। তারা সাঁওতাল আদিবাসী। অক্লান্ত পরিশ্রমে তারা চরের রূপ পালটে দিল। আগাছার জঙ্গল হয়ে উঠল ফুল-ফল-শস্যে সাজানো বাগান। গ্রামের সদগোপ চাষিদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়ল তার উপর। চাষিরা শুধু খাদ্যে সন্তুষ্ট নয়। তারা মুনাফাও চায়। এরপর এল জমিদার। সে শস্য এবং মুনাফার সঙ্গে চায় প্রভুত্ব। শেষে কুটিল ষড়যন্ত্রী মুনাফা সর্বস্ব ব্যবসাদারের আবির্ভাব হল। পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠল। শুরু হল বিবাদ, মামলা মোকদ্দমা এবং দাঙ্গা। মৃত্যু যার অবধারিত পরিণাম। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে চর ছেড়ে পালিয়ে যেতে বাধ্য হল সাঁওতালরা। যারা যেতে পারল না তারা ক্রীতদাসে পরিণত হল।
এ যে কেবল কালিন্দীর ইতিহাস নয় তা লেখকই অহীন্দ্রের মাধ্যমে বলেন, ‘বিশ্বচরাচরে আদিকাল থেকে যা ঘটে ওই চরেও ঠিক তাই ঘটল বন্ধু। সাঁওতালগুলো ওই ভাবেই বঞ্চিত হতে বাধ্য, ওই মেয়েটার ওই দুর্দশাই স্বাভাবিক। চরটা আর তোমার মধ্যেকার টাইম আর স্পেসের ডাইমেনশন বাড়িয়ে নাও না, দেখবে চরটা বেমালুম পৃথিবীর সঙ্গে মিশে গেছে, পার্থক্য নেই।’
এসব দেখে অহীন্দ্র স্থির থাকতে পারে না। সদ্য বিবাহিত তরুণ অহীন্দ্র ডুবে থাকে কার্ল মার্কসের জীবনীতে। স্ত্রীকে সে লেনিনের স্ত্রীর গল্প পড়ে শোনায়। শেষ পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উজ্জ্বল ছাত্র ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভবনা জলাঞ্জলি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে স্বাধীনতার আন্দোলনে।
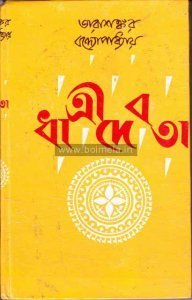
ধাত্রীদেবতাঃ ধাত্রীদেবতা উপন্যাসের সময়কাল ১৯২১ সাল পর্যন্ত বিস্তৃত। এই উপন্যাস শিবনাথের কৈশোর থেকে যৌবনে উপনীত হওয়ার কাহিনি। এ কাহিনি তার ‘স্বদেশ চেতনা’র বিবর্তন ও পরিণতির যাত্রাও বটে। তাই রাজনৈতিক আন্দোলনের চেয়েও এখানে মুখ্য হয়ে উঠেছে স্বদেশ-বোধ। মানবতা, সেবা এবং সমাজ সংস্কারের মধ্যে সেই বোধের উন্মেষ ঘটেছে। স্বদেশের সমাজ ও সংস্কৃতি মানুষের মনকে পরিপুষ্ট করে। শৈশব ও কৈশোরে শিবনাথের মনের পুষ্টি যুগিয়েছে তার মা, পিসিমা, গোঁসাই বাবা এবং রামরতন মাষ্টারমশায় প্রমুখ বহু মানুষ। পিসিমা দিয়েছেন অধিকার বোধ ও নীতিপরায়ণতার শিক্ষা। গোঁসাইবাবার কাছে সে শুনেছে বীরত্বের কাহিনি। রামরতন মাষ্টারমশায় তাঁকে রবীন্দ্রনাথের অনুরাগী করে তুলেছেন। বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে মা শিবনাথের হাতে রাখী বেঁধে দিয়েছেন। কৈশোরে তাকে পাঠ করে শুনিয়েছেন আনন্দমঠ। ব্যাখ্যা করেছেন দেশ মানে শুধু মাটি নয়।
‘দেশকে খুঁজতে হয় গ্রামের বসতির মধ্যে, শহরের মধ্যে। তুই আমাদের পটো পাড়াটা দেখেছিস শিবু? আর তো পটোরা নেই; সব মরে গেছে, কজন ছিল পালিয়ে গেছে। আমার বিয়ের পরও আমি দেখেছি শিবু, ওই পটোপাড়ার কি চলতি! বড় বড় জোয়ান পট দেখিয়ে গান করত, মাটির পুতুল বেচত মেয়েরা। যে জায়গা দিনরাত্রি হাসি গান আনন্দে মুখর হয়ে থাকত, লক্ষ্মীর কৃপায় সুন্দর হয়ে থাকত, সেই জায়গা আজ কী হয়েছে! ওইখানে ভেবে দেখ, ‘মা কী ছিলেন, কী হইয়াছেন!’’
শিবনাথ তার পরিবার পরিবেশ থেকে ধীরে ধীরে স্বদেশকে অনুভব করতে শিখেছে। কলকাতায় পড়তে গিয়ে রাজনীতিতে যোগ দিয়েছে। ক্রমশ তার স্বদেশ চেতনা গন্ডিমুক্ত হয়ে বৃহত্তর পরিসরে ব্যপ্ত হয়েছে। বিপ্লবের পথ ছেড়ে সে ঝুঁকেছে অহিংসার পথে। যোগ দিয়েছে অসহযোগ আন্দোলনে। ১৯২১ সালে সে কৃষিকাজ, চরকা, নাইট স্কুল, ধর্মগোলা এবং দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি নিয়ে মেতে উঠেছে।
‘গোটা ভারত জুড়ে অনার্য এবং শূদ্র অশিক্ষিত এবং অনাদৃত হয়ে পড়ে আছে শত শত বৎসর ধরে, তাদের অজ্ঞানতার অন্ধকারে রেখে দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন করা উন্মত্ততা ছাড়া আর কিছু নয়।’ হেন বাক্য থেকে এই উপন্যাসে স্বদেশ ও সমাজচেতনার মূল সুরটি খুঁজে পাওয়া যায়।
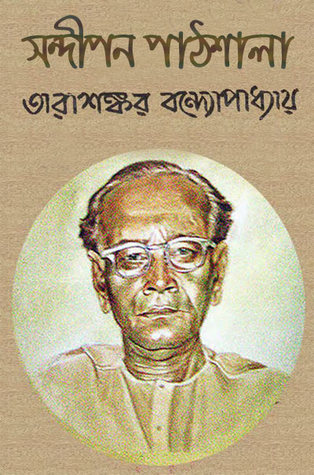
সন্দীপন পাঠশালা
‘সন্দীপন পাঠশালা’ উপন্যাসের কাহিনি অসহযোগ আন্দোলনের সময়কাল থেকে বিস্তৃত হয়েছে স্বাধীনতা উত্তর কাল পর্যন্ত। দরিদ্র চাষি জীবন এই উপন্যাসের উপজীব্য। এ কাহিনি সীতারাম নামের একজন সৎ শিক্ষকের আত্মত্যাগের কাহিনি। সীতারাম ছাড়াও এ উপন্যাসে সমাবেশ ঘটেছে সমাজের অভিজাত সম্প্রদায়ের হিংস্র, কুটিল, ক্ষমতাবান মানুষ এবং কিছু মানবিক চরিত্রের। সময়ের দাবী মেনে এসেছে ‘ধীরানন্দ’। ‘ধাত্রী দেবতার’ শিবনাথের সঙ্গে যার মিল চোখে পড়ার মতো। ধীরাবাবুর প্রতি সীতারামের অসীম শ্রদ্ধা। মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়ে ধীরাবাবুর রাজবন্দি হবার খবরে সে রোমাঞ্চিত হয়। আবেগে বিহ্বল হয়ে পাঠশালায় ছুটি দিয়ে দেয়। তার ফল ভোগ করতে হয় গ্রাম্য পণ্ডিতটিকে। পাঠশালায় পুলিশ আসে। সীতারামকে শুধোয়, ‘সন্দীপন কেন নাম দিলে পাঠশালার? অ্যাঁ? পরিত্রাণায় সাধুনাং? ... তোমার মাথা থেকে এসেছে? অ্যাঁ? কৃষ্ণ তৈরির কারখানা?’
সীতারাম জানায়, তাঁর এই পাঠশালার নামকরণ করেছেন ধীরাবাবু। অতঃপর পুলিশ সাহেব পাঠশালার অন্দরে প্রবেশ করেন। তীক্ষ্ণ নজরে দেখেন দেওয়ালগুলি। সেখানে পেন্সিল দিয়ে যেমন লেখা আছে ‘ভোলা চোর’, ‘আকু ডাকাত’ তেমনি লেখা আছে ‘বন্দে মাতরম’ এবং ‘গান্ধী মহারাজের জয়’।
দারোগা ছাত্রদের জিজ্ঞেস করেন, ‘তোমরা ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় লোকের নাম জান?’
এক একজন এক এক রকম উত্তর দেয়,
- মহারাজ গান্ধী।
- চিত্তরঞ্জন দাশ।
- মতিলাল নেহরু।
- সুভাষ চন্দ্র বসু। জহরলাল নেহরু।
দারোগা শুধোয়, সে ছেলেদের এসব শিখিয়েছে কিনা! ভয়ের শেষ সীমায় পৌঁছে সীতারাম বলে, ‘এসব আজকাল কাউকে শেখাতে হয় না হুজুর, দেশের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। ওরা নিজেই শিখেছে।’
পাঠশালায় সরকারি সাহায্য বন্ধ যায়। ১৯৪০ সালে পাকাপাকিভাবে উঠে যায় পাঠশালা। প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়। পরে দেশ স্বাধীন হয়। বয়সের ভারে সীতারামের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। এমন সময় সে ধীরানন্দের চিঠি পায়, ‘পণ্ডিত, স্বাধীন রত্নহাটাকে প্রণাম করতে যাব। তোমাকে দেখতে যাব।’
এ চিঠি পড়ে সীতারাম আপনমনে ধীরাবাবুর উদ্দেশে বলে, ‘রত্নহাটার মাঝখানে দাঁড়ালে- চারিপাশে গোল হয়ে আকাশ নেমে আসে যে সীমানাটুকু ঘিরে – আমার ভূগোল ততটুকু। তবে দেখলাম এবার ইতিহাস। উনিশশো একুশ সাল থেকে তুমি রত্নহাটার ছেলে- ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধে মাতলে, সে আমার কাছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার যুদ্ধ নয়, রত্নহাটার স্বাধীনতার যুদ্ধ।’
সীতারামের সঙ্গে ধীরানন্দের শেষ সাক্ষাতে সীতারাম বলে, পাঠশালা যখন নাই, তার দৃষ্টিরও প্রয়োজন নাই। তবে সে শুনেছে স্বাধীন দেশে চন্ডাল থেকে ব্রাহ্মণ পর্যন্ত সবাই লেখাপড়ার সুযোগ পাবে। যদি বেঁচে থাকে তাহলে সেদিনের মানুষের মুখগুলো দেখবার জন্যেই কেবল দৃষ্টি ফিরে পেতে চাইবে।
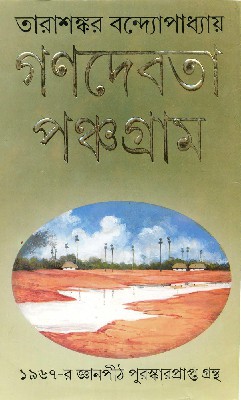
গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম
গণদেবতা ও পঞ্চগ্রাম মিলিয়ে বৃহত্তর উপন্যাসটি যেন ব্যক্তিহীন গণজীবনের শোভাযাত্রা। দেবু পণ্ডিত, অনিরুদ্ধ কামার, গিরিশ ছুতোর, তারাচরণ নাপিত, সতীশ বাউরি, দুর্গা, জগণ ডাক্তার, পঞ্চরত্ন মশায়, ডেটেনিউ বাবু যতীন, উঠতি জমিদার শ্রীহরি এমন অসংখ্য চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে উপন্যাসে। দেবু ঘোষের চোখ দিয়ে লেখক তৎকালীন সামাজিক পরিবর্তন দেখিয়েছেন। দেবু ভালো ছাত্র হওয়া সত্ত্বেও তার পাশ করা হয়ে ওঠে নি। তবুও গ্রাম ছেড়ে ভালো চাকরির সন্ধান করে উপার্জন করতে পারত। তা না করে গ্রামের কথা ভেবে চণ্ডীমণ্ডপে পাঠশালা খুলে বসেছে। তার নব শিক্ষায় শিক্ষিত মন দলিত ও দারিদ্রক্লিষ্ট গ্রামবাসীদের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার দেখে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছে। নিজের অজ্ঞাতসারেই সে এগিয়ে গিয়েছে প্রতিবাদ করতে। অসহায় মানুষদের প্রতিনিধিত্বের ভার যেন আপনি এসে পড়েছে তার উপর। বহু যুগ ধরে জমা অত্যাচারের প্রতিবাদের দায় বর্তেছে। সংগ্রাম করতে গিয়ে নিজের উপার্জনের পথ, স্ত্রী-পুত্র সব সে হারিয়েছে। অকারণে জেল খেটেছে। তারপরও তার ভেতরের বিশ্বাস টলে নি, ‘মানুষের পরম কামনার মুক্তি একদিন আসিবেই। ... সেদিন মানুষের যাহা সত্যিকারের পাওনা তাহা তোমরা পাইবে। সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অন্নবস্ত্র ঔষধপথ্য আরোগ্য অভয় এ মানুষের পাওনা। আমি যাহা শিখিয়াছি তাহা শোন, আমি কাহারও চেয়ে বড় নই, কাহারও অপেক্ষা ছোট নই। কাহাকেও বঞ্চনা করিবার অধিকার আমার নাই, আমাকে বঞ্চিত করিবার অধিকারও কাহারও নাই।’
১৯২১-২২ সালে রামপুরহাট মহকুমায় ইউনিয়ন রেট বা ট্যাক্স বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। সেই আন্দোলনের প্রাণশক্তি ছিল কৃষক সমাজ। নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তারিণী সিংহ। গ্রামের সমস্ত উপজাতি সাঁওতাল, বাগদী, রুইদাস সম্প্রদায় তাতে অংশ গ্রহণ করেছিল। শ্রেণীগত ভাবে জমিদাররা ওই আন্দোলনকে যথাশক্তি দিয়ে বিরোধিতা করে এবং ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে দাঁড়ায়।
ঘটনাটির ছাপ আছে পঞ্চগ্রামে। উপন্যাসে পল্লীজীবনের ঢিলেঢালা গতির মধ্যে বিদ্রোহের আগুন পুঞ্জীভূত হয়ে উঠার কাহিনিটি নির্মিত হয়েছে। পাশাপাশি গ্রামজীবনে বাণিজ্য ও শিল্পকেন্দ্রিক জীবিকার অনুপ্রবেশের মাধ্যমে কাল পরিবর্তনের সূচনাও ফুটে উঠেছে। ন্যায়রত্ন শিবশেখরের কাল পিছিয়ে পড়ছে। এগিয়ে আসছে তাঁর পৌত্র বিশ্বনাথের নতুন চিন্তাধারা। ভারতবর্ষের নবলব্ধ জাতীয়তাবোধ। ছিরু পালের মাধ্যমে দেখতে পাওয়া যায় নব্য ধনী, উচ্চাভিলাষী শক্তির অভ্যুত্থান। দেখতে পাওয়া যায় কীভাবে বণিক সম্প্রদায় পরোক্ষভাবে দেশের শাসন ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রন করছে। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ধনী বা বণিক সম্প্রদায় কেউই দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পিছপা হয় না। ডেটেনিউ যতীনবাবুর মাধ্যমে প্রকাশ পায় ১৯৩০ সালের আন্দোলনের যে প্রবল ঢেউ উঠেছিল তার ধাক্কা থেকে নিরুপদ্রব পল্লীবাসীও নিশ্চিন্ত থাকতে পারে নি।
দীর্ঘ এই উপন্যাসের শেষে কোনও একটি নির্দিষ্ট চরিত্রকে আর আলাদা করে মনে পড়ে না। মনে থাকে না অজস্র ঘটনার ঘনঘটায় চিত্রিত কাহিনির কোনও একটা নির্দিষ্ট ঘটনাকে। এক কে অতিক্রম করে বহুকে ছুঁয়ে ফেলে এই কাহিনি। কোথাও যেন আগামীদিনের গণতন্ত্রের আভাস ফুটে ওঠে।
মন্বন্তরঃ মন্বন্তর উপন্যাসের কালসীমা ১৯৪২ এর ডিসেম্বর থেকে ১৯৪৩ এর মার্চ পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন কলকাতার নাগরিক জীবনের বিপর্যয়কে উপজীব্য করে লেখা এই কাহিনি বাস্তবোচিত এবং বীভৎস। এই কাহিনি মনুষ্য-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ আর তারপর মহামারির কাহিনি। উপন্যাস জুড়ে কালোবাজারি, সাইরেনের আওয়াজ, ব্ল্যাক আউট, বিমানহানা ও বোমাবাজি আর থেকে থেকে ‘চারটি ভাত দাও মা, খানিক ফেন দাও’ এর বিবরণ পড়তে পড়তে দম বন্ধ হয়ে আসে। আগামী নতুন বছরের ছবি দেখে শিউরে উঠতে হয়, ‘মাটির বুক থেকে উঠছে কঙ্কাল সার, ক্রুদ্ধ দৃষ্টি, লোলুপ হাঁ-করা, প্রায় নগ্না এক বিভীষিকাময়ী নারীমূর্তি। সে দুর্ভিক্ষ। তাঁর পায়ের তলা থেকে আরও একটি মুখ উঁকি মারছে। সে মুখে আবার চামড়ার আবরণও নেই।– সে মহামারী। আকাশে উড়ছে চিল শকুনি, গোলা ফাটছে, প্লেন উড়ছে, ধোঁয়ায় সূর্য দেখা যায় না, সমস্ত ঝাপসা। নীচে লেখা নববর্ষ- ১৯৪৩।’
উপন্যাসে চক্রবর্তী পরিবারের করুণ পরিণতি পতনোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের প্রতীক। দেশের ঘোরতর দুর্দিনে কালোবাজারি ব্যবসায়ীর প্রতীক হল রায়বাহাদুর মিস্টার বি মুখার্জির পরিবার। যার ছেলে নির্দ্বিধায় বলতে পারে, ‘আমাদের গুদোমের চাবি যদি এক হপ্তা খুঁজে না পাওয়া যায়- তবে কলকাতায় উনুন জ্বলবে না।’
তাই মনে হয় ‘মন্বন্তর’ শব্দটি আক্ষরিক অর্থের ঊর্ধ্বে উঠে সেই সময়কার অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং নৈতিক অবক্ষয়কেও চিহ্নিত করেছে। এখানেই মানবিকতার প্রতীক হয়ে উঠেছে দেবপ্রসাদের পরিবার। তাঁর ছেলেমেয়েরা সাম্যবাদী। পৃথিবীর মানুষের মুক্তির স্বপ্নে তারা বিভোর। গান্ধীবাদী অহিংস পন্থায় বিশ্বাসী তারাশঙ্করের এই কাহিনিতে অনেকগুলি কম্যুনিস্ট চরিত্র দেখতে পাওয়া যায়। কাহিনি শেষ হয় মহাত্মা গান্ধীর একুশ দিন ব্যাপি অনশন উদযাপনের মধ্যে দিয়ে। ইংরাজি দৈনিকের সম্পাদক কম্যুনিস্ট বিজয়ের মধ্যে লেখকের আপন চিন্তাধারার প্রতিফলন ঘটে। যা তৎকালীন কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক মতাদর্শের চেয়ে ভিন্ন। বিজয় বিদেশী নেতাদের মতো গান্ধীজীকে ‘জনস্বার্থ বিরোধী’ অথবা ‘বিরামহীন বিপর্যয়ের নায়ক’ বলে মনে করে না। সে তাঁর অহিংসা আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে গান্ধীজীর প্রশংসা করে। দমবন্ধ করা কাহিনিটি মানুষের মঙ্গলময় অগ্রগতির আশ্বাস দিয়ে শেষ হয়। কানাই নীলার হাতে হাত রেখে বলছে, ‘কমরেড, মানুষকে এই মন্বন্তরের দুর্যোগ পার করে নিয়ে যেতে হবে। ... মহাযুদ্ধের শেষে আসবে নববিধান।’
ঝড় ও ঝরাপাতাঃ ১৯৪৬ সাল। রসিদ আলি খাঁর কারাদণ্ডের আদেশের ফলে ছাত্রদের প্রতিবাদে এগারোই ফেব্রুয়ারি থেকে পনেরোই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত কলকাতায় যা ঘটেছিল, সেই কথা দিয়ে তারাশঙ্কর লিখেছিলেন ‘ঝড় ও ঝরা পাতা’ উপন্যাস। আকস্মিকভাবে যে ঝড় সেদিন উঠেছিল, তাতে ঝরে গিয়েছিল বেশ কিছু প্রাণ। এই ঝড় সবচেয়ে বেশি যাকে নাড়া দিয়েছিল, সে গোপেন। গোপেন এই কাহিনিতে শুধুমাত্র একটি চরিত্র নয়। নিম্নমধ্যবিত্ত গৃহকর্তা এবং সমগ্র কেরানিকুলের প্রতিনিধি সে। তার চোদ্দ বছরের মেয়ে নেবু, তিন ছেলে দেবা, টেবা, হাবু এবং স্ত্রী শান্তি প্রত্যেকেই এক একটি প্রতীকী চরিত্র।
আন্দোলনের ঢেউ গোপেনের পুত্রকন্যাদেরও গায়ে এসে লেগেছিল। ছোট বাচ্চারা চেঁচিয়েছিল ‘জয় হিন্দ’। গলির মোড়ে লুকিয়ে গোরা পল্টনের দিকে ঢিল ছুড়েছিল। লেখকের ভাষার এরা ‘খুদে পল্টন।’
বাবা মার চোখ এড়িয়ে মাথায় পাঞ্জাবিদের মতো পাগড়ি বেঁধে প্যান্ট পরে ছেলে সেজে বের হয় নেবু। সেই রাতেই সে শহিদ হয়। খবরটা জানে কেবল নেবুর প্রেমাকাঙ্খী কানু। নেবুর শহিদ হবার খবর অজানাই থাকে তার বাবা-মার কাছে। তারা ভাবে সুযোগ পেয়ে উঠতি বয়সের মেয়ে পালিয়েছে। প্রতিবেশীদের কাছে সাফাই দিতে একটি বিশ্বাসযোগ্য কাহিনি গড়ে তুলতে মরিয়া হয়ে ওঠে নেবুর মা।
লেখক বলেন, ‘১৯৪৬ সালের কলকাতার মেয়ে নেবু। আগস্ট আন্দোলন সে দেখেছে। ‘ভারত ছাড়ো’, ‘করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে’ কী তা সে জানে। আজাদ-হিন্দ ফৌজ, নেতাজী জানে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আতঙ্ক, কষ্ট, দুর্ভোগ সে ভোগ করেছে, ব্ল্যাক আউট, লরির তলায় মানুষের অপঘাত, পথের উপর না খেয়ে মানুষের মৃত্যু, সমস্ত কিছুর ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়া তার মনের ধাতুকে দুপিঠে হাতুরির মতো ঘা মেরে মেরে এমন বেদনার্ত করে রেখেছে যে একটু উত্তেজনার ছোঁয়ায়, চরমতম অধীরতায় চঞ্চল করে তোলে; মা বাপের অনুপস্থিতির সুযোগে সে আজ যা করলে, ঠিক তাই ছাড়া আর কিছু করতে পারত না। এ নেশা লাগা অনিবার্য নেবুর পক্ষে।’
কলকাতার দাঙ্গা ও আমিঃ ১৯৪৬ সালের অগাস্ট মাসের কলকাতায় হিন্দু মুসলিমের দাঙ্গাকে ঘিরে ‘বিস্ফোরণ’ শিরোনামে একটি প্রতীকী গল্প লিখেছিলেন তারাশঙ্কর। মহানগরীর ছিনভিন্ন চিত্র তাতে ফুটে উঠেছিল। এছাড়াও তিনি লিখেছেন ‘কলকাতার দাঙ্গা ও আমি’। গল্পটি হিংসামত্ত বিভীষিকাগ্রস্ত কলকাতার ছবির সঙ্গে গ্রামবাংলার চিত্রকে মিলিয়ে দেখার কাহিনি। লেখকের গ্রামের চতুর্দিকে গ্রামগুলিতে মুসলমান সংখ্যায় কম। তারা যে বংশপরম্পরায় এ দেশের মানুষ সেকথা তারা গর্ব করে বলে। প্রভাব প্রতিপত্তি বা বিত্ত সবদিক থেকেই তারা হিন্দুদের চেয়ে পিছিয়ে। সমগ্র অঞ্চলের শাসন ক্ষমতা, বিত্ত এবং শিক্ষায় মূলত হিন্দুদের প্রতাপ। মুসলমানরা সাধারণত চাষি অথবা মজুর।
লেখক ট্রেন থেকে নেমেছেন। আরও সাত মাইল পথ যেতে হবে। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। গোরুর গাড়িতে গেলে ঘন্টা পাঁচেক সময় লাগবে। ততক্ষণে সন্ধ্যে পেরিয়ে রাত্রি নেমে আসবে। সামনের পথ ধূ ধূ মাঠ। জনবসতি নেই। পথে কিছুটা জঙ্গল পড়ে আর পড়ে একটি শতাব্দী প্রাচীন কুখ্যাত বটতলা। একটি গোরুর গাড়ি ঠিক করে যেই চড়ে বসতে যাবেন কুলী সাবধান করে দিল, মুসলমানের গাড়িতে যাওয়া কি ঠিক হবে! চালক যে চিরপরিচিত গোরুর গাড়ির গাড়োয়ান ছাড়া আর কিছু এ কথা লেখকের মাথায় একবারও আসে নি। তাঁর মনে এখনও কোনও দ্বিধা নেই। গাড়ি ছাড়ল। পথে সঙ্গী হল বাউল নিতাই দাস। সময় কাটল গড়িয়ে গড়িয়ে। বটতলার কাছাকাছি এসে শুরু হল ঝড় বৃষ্টি। লেখক বটগাছের নিচে আশ্রয় নিতে চাইলে বাকি দুজন বাধা দিল। খুন, ধর্ষণ আর ডাকাতির জন্যে কুখ্যাত স্থানে তারা তাঁকে যেতে দেবে না। লেখকের যুক্তিবাদী মন বলল, ‘যারা অপরাধ করবে তারা কেবল মাত্র গাছের গোড়াতেই করবে এমন তো নয়। অদূরে অসহায় অবস্থায় তিনজন যাত্রী আটকে আছে জেনেও কি ছেড়ে দেবে!’ নিতাই দাস বাউল সাবধান করে, আসল ভয় তা নয়। ভয় পাপের। ওই গাছের গোড়ায় পাপ জমা হয়ে আছে। যে সেখানে যায় তার মনের ভেতরের পাপ বেরিয়ে আসে। নিরীহ মানুষ হিংস্র হয়। তবে উপায় একটা আছে। অকপটে নিজের করা সবচেয়ে বড় পাপের কথা বলতে পারলে আর কোনও পাপ স্পর্শ করবে না। গাড়োয়ান নির্দ্বিধায় সম্মত হয় তার পাপের কথা খুলে বলতে। লেখক থমকে যান। সবচেয়ে বড় পাপের কথা মুখ ফুটে বলা যায় নাকি? কোনও শহুরে সভ্য মানুষ কি তা পারে? তিনি পারবেন না। মনে পড়ল তাঁর সাহিত্যিক ও সম্পাদক বন্ধুদের কথা, তারাও পারবে না। নিজের করা পাপের কথা খুলে বলা আর মন থেকে পাপপ্রবৃত্তি ঝেড়ে ফেলা, দুটোই সমান কঠিন।
গল্পের শেষ অংশে লেখক যেন তাৎপর্যপূর্ণভাবেই আশার কথা বলতে চেয়েছেন, কোন-না-কোন দিন মানুষ অকপটে নিজের পাপ স্বীকার করবে। নিজের ভেতর থেকে সমস্ত রাগ, হিংসা আর পাপকে সত্যি যদি ঝেড়ে ফেলতে পারে, তাহলেই মানুষ হবে নিষ্কলুষ। সেদিন আর এমন নৃশংস ঘটনা ঘটবে না।
স্বাধীনতাঃ ‘উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরোই আগস্ট। ভারতবর্ষ স্বাধীনতার সিংহদ্বারে প্রবেশ করেছে। নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে মহোৎসব। একটি সমৃদ্ধিসম্পন্ন পল্লীগ্রামে স্বাধীনতা উৎসবের অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সভাপতি বাংলাদেশের একজন বিখ্যাত ব্যাক্তি, কলকাতায় থাকেন, তিনি কলকাতার বহু অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণের সম্মান সসম্মানে ফিরিয়ে দিয়ে, সেখানকার বিপুল সমারোহ, অপরিমেয় প্রাণশক্তির উল্লসিত, উচ্ছ্বসিত বিকাশের অতুলনীয় দৃশ্য দেখার প্রলোভন সংবরণ করেও এখানে এসেছেন –তার কারণ তিনি এই গ্রামের সন্তান।’
এই বিবরণ ‘স্বাধীনতা’ নামে একটি ছোটগল্পে পাওয়া যায়। ফ্ল্যাশব্যাকে আসে পূর্বরাত্রির অভিজ্ঞতা। ঘরে ঘরে বেজেছে শাঁখ। শাঁখের শব্দ গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে ধ্বনিত হয়েছে। আবার চোখের সামনে ভেসে ওঠে সভামণ্ডপ। ড্রাম বাজছে। ধ্বনি উঠছে, ‘বন্দে মাতরম’ ‘জয় হিন্দ’ ‘ইনকিলাব জিন্দাবাদ’, ‘স্বাধীন ভারত কি জয়’, ‘স্বাধীন ভারত জিন্দাবাদ’।
সভায় হিন্দু এসেছে। এসেছে মুসলমান। খদ্দরের টুপি পরা ছেলের দল এসেছে। এসেছে ভদ্রজন। খালি গা খালি পা কিছু মানুষ এসে সভার প্রান্তে দাঁড়িয়েছে। নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে কী হচ্ছে!
‘বাবুরা রাজা হলেন, সাহেবরা চলে গেল?’
হঠাৎ মঞ্চের সামনে হাজির হল উন্মত্ত আকাল হাড়ী। তার বাপ সাহেবের রেশমকুঠিতে কাজ করত। সাহেবকে বাবা বাঁচিয়েছিল সাপের কামড় থেকে। সেই সাহেবের গুলিতেই বাবা মরেছে। মালিক মেরেছিল তাই বিচার হয় নি। আকাল পালিয়ে গিয়েছিল। ১৯১৪ সালে ইংরেজ- জার্মানির যুদ্ধের সময় চেপে বসেছিল জাহাজে। লড়াই করতে হয়েছিল ইংরেজের পক্ষে। এই তার আপসোস। অন্তত একজন ইংরেজকে মেরে বাবার হত্যার প্রতিশোধ সে নিতে পারত কিন্তু সে অধর্ম সে করতে পারে নি।
গান্ধী মতাবলম্বী সভাপতি আকালকে স্বান্ত্বনা দেন, ‘তুমি ঠিকই করেছিলে। আজ আমরা যে পুণ্যের বলে স্বাধীনতা পেলাম – সেই পুণ্যের মধ্যে তোমার সেদিনের পুণ্যও আছে। এদেশে তোমার জন্ম বলেই তুমি তা পেরেছিলে।’
আকাল বলে, ‘স্বাধীনতা কী বলছ গো? সাহেবরা চলে গেল, তাই বল।’
স্বাধীনতার ঊষালগ্নে তারাশঙ্কর যেন একজন ‘খালি গা খালি পা’ শ্রেণির জনগণের প্রতিনিধিকে হাজির করে দিলেন। যার প্রশ্ন স্বাধীনতার দিনটা ঠিক কী? সাহেবদের চলে যাওয়া আর দেশের বাবুদের রাজা হওয়া! কেবল ক্ষমতার হাত বদল হল নাকি সত্যিকারের স্বাধীনতা এল, এই দ্বন্দ্বের মধ্যেই স্বাধীনতা লাভের যাত্রার সমাপ্তি ঘটে।
পরিশিষ্টঃ তারাশঙ্করের বিপুল সাহিত্যকীর্তির মধ্যে উপন্যাস ‘ছায়াপথ’, ‘কালান্তর’, ‘কীর্তিহাটের কড়চা’ অথবা নাটক ‘বিংশ শতাব্দী’কে আলোচনার বাইরে রেখেও বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে তারাশঙ্কর স্বদেশ চেতনার একটি অভিনব ধারা যোগ করেছিলেন। এ ধারা তাঁর পূর্বসূরী বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ অথবা শরৎচন্দ্রের থেকে ভিন্ন। তাঁর সাহিত্যে স্থান পেয়েছিল সাঁওতাল বিদ্রোহ থেকে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতিটি ধাপ। পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরে তার অভিঘাত আলোচিত হয়েছে। ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের দোষগুণ নিয়ে এমন করে আর কেউ কাটাছেঁড়া করেন নি। অভিজাত শ্রেণী থেকে দরিদ্র চাষি অথবা অন্ত্যজ ভিক্ষুকের মহত্ত্ব ও দেশাত্মবোধ একাকার হয়ে গিয়েছে তাঁর লেখায়।
শিবনাথ, ধীরানন্দ, অহীন্দ্র, দেবু পণ্ডিত, বিজয় অথবা স্বাধীনতা উদযাপন অনুষ্ঠানের সভাপতির আদর্শ মিলে গিয়েছে তারাশঙ্করের নিজের আদর্শের সঙ্গে। তিনি নিজে যেমন সশস্ত্র বিপ্লবী এবং অহিংস কংগ্রেসি দুটি ধারাতেই প্রভাবিত হয়েছিলেন, তাঁর রচনাতেও দুটি ধারাই স্থান পেয়েছে। তাঁরই চেতনার প্রতিফলন ঘটেছে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির স্বদেশ চেতনা, মুক্তি চেতনা এবং সমাজ চেতনার মধ্যে।
তথ্যসূত্রঃ
১। তারাশঙ্কর রচনাবলী (মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স); খণ্ড ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৭ ও ৮।
২। তারাশঙ্করের গল্পগুচ্ছ (সাহিত্য সংসদ); খণ্ড ১, ২ ও ৩।
৩। আমার কালের কথাঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৪। আমার সাহিত্য জীবনঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৫। তারাশঙ্করের জীবনীঃ জগদীশ ভট্টাচার্য।
৬। আমার জীবনে কপালকুণ্ডলা; প্রবন্ধঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৭। আমার কৈশোর; প্রবন্ধঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৮। শিল্পীর স্বাধীনতা; প্রবন্ধঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
৯। মন্বন্তর ও সাহিত্য; প্রবন্ধঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
১০। সাহিত্য ও রাজনীতি; প্রবন্ধঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।
১১। গৌরীহর মিত্র সঙ্কলিত বীরভূমের ইতিহাস; সম্পাদনা অরুণ চৌধুরী।
