
মেয়েদের লেখালেখি - বাংলা সাহিত্যের তিন হারিয়ে যাওয়া লেখিকা
- 15 April, 2023
- লেখক: শতাব্দী দাশ
বাংলা সংস্কৃতির উদযাপন যে পয়লা বৈশাখের বাৎসরিক কর্মকাণ্ডে সীমাবদ্ধ হয়েছে, তা নিয়ে আমাদের হুতোশের শেষ এই। হিন্দি-হিন্দু-হিন্দুস্তানের মানচিত্রে এ যেমন প্রান্তিকীকরণ, তেমন প্রান্তিকীকরণের রাজনীতি অবশ্য চিরকালই বহাল ছিল সমাজে, সাহিত্যে ও সংস্কৃতিতে। বস্তুত, বাংলা সংস্কৃতি বলে যা পালন করি, তা ভদ্রবিত্ত উচ্চবর্ণ পিতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতিই বটে। যেমন, পাটভাঙা শাড়ি, ধুতি, মঙ্গল শোভাযাত্রা গ্রামবাংলার নববর্ষের অঙ্গ নয়। সেই পয়লা বৈশাখের সঙ্গে অনেক বেশি সম্পৃক্ত ভোরবেলায় মাঠে নুড়ো জ্বালতে যাওয়া, প্রথম পাতে আবশ্যিক তেতো আর বিকেলে গাজনের মেলায় ভ্রমণ। একই কথা খাটে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে।
নববর্ষের সঙ্গে সাহিত্যের আবার গাঁটছড়া বাঁধা। কবে কীভাবে তা বাঁধা হয়েছিল,তা বর্ষিয়ান লেখক-প্রকাশকেরা বলতে পারবেন। কিন্তু গ্রন্থিটি যে পোক্ত, তা বোঝা যায় কলেজ স্ট্রিট পাড়ায় প্রকাশকদের দপ্তরে বুধমণ্ডলীর নতুন বছরের আড্ডা দেখে। মূলধারার বাংলা কৃষ্টির অন্যতম ভরকেন্দ্র যদি হয় সাহিত্য, তবে পাঠক হিসাবে যে প্রশ্ন অবধারিত ভাবে মনে আসে, তা হল— বাংলার অমর সাহিত্যিক কারা? বা অমর সাহিত্য কী? অমরত্বের যে ক্যানন, তা স্থির হল কীভাবে? যাঁরা স্থির করেন, তাঁদের লিঙ্গ-বর্ণ-শ্রেণি-ধর্মগত পরিচয় কী? অমরত্ব স্থির করার সূচক কী কী ছিল? কথিত 'অমর'-রা যে মহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করেননি তা নয়, কিন্তু যাঁদের তুলনায় শ্রেয় বলে এঁরা অমর হলেন, তাঁদেরকে না পড়ে তুলনামূলক সিদ্ধান্তে আসা যায় কি? এই প্রসঙ্গে এসে পড়ে দলিত সাহিত্যের কথা, এসে পড়ে নারী সাহিত্যের কথা— মূলস্রোতে স্থান জোটেনি যাদের। এসে পড়ে সেই লেখিকাদের কথা, যাঁদের কোনো বুধসমাবেশে হয়ত ডাক পড়েনি কোনোদিনও।
আশাপূর্ণা দেবীর উপন্যাসে যখন সুবর্ণলতার বইপত্র-খাতা সব পুড়ে যাচ্ছে, তখন ছোট বকুল মনে মনে বলেছিল,
''মা, মাগো, তোমার পুড়ে যাওয়া, হারিয়ে যাওয়া লেখা, না-লেখা সব আমি খুঁজে বার করবো, সব কথা আমি নতুন করে লিখব৷ দিনের আলোর পৃথিবীকে জানিয়ে যাব অন্ধকারের বেবাক যন্ত্রণার ইতিহাস।''
তেমন করে হারিয়ে যাওয়া লেখাদের খুঁজে বার করার, আর না-লেখাদের লিখে যাওয়ার দায়িত্ব বর্তায় নারীবাদের উপর আর উত্তরকালের লেখিকাদের উপর। নারীবাদ শুরু থেকে সাহিত্যতত্ত্বের সাথে সম্পৃক্ত ছিল না। তা ছিল সামাজিক ও রাজনৈতিক মতবাদ মাত্র। বিংশ শতকে এসে নারীবাদ সাহিত্যতত্ত্বে জায়গা করে নিতে শুরু করল। প্রথমে তা পুরুষ লেখকদের লেখায় নারীর অবমূল্যায়িত চিত্র অনুসন্ধানে ব্যাপৃত ছিল, যাকে বলে গাইনোক্রিটিসিজম। অতঃপর উত্তরাধুনিক ও মনোবিশ্লেষণাত্মক নারীবাদ সাহিত্যের অর্থনির্মাণ প্রক্রিয়ায় লিঙ্গের ভূমিকা বিষয়ে আলোকপাত করে। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও আইনি কাঠামো অতিক্রম করে নারীবাদকে সাংস্কৃতিক প্রসঙ্গে প্রবেশের আহ্বান জানিয়েছিল অবশ্য সিমন দে বেভোয়ারের ‘দ্য সেকেন্ড সেক্স’। বেভোয়ার প্রথম বলেছিলেন ‘নারীরা নারী হয়ে জন্মায় না, বরং ধীরে ধীরে নারীতে পরিণত হয়’। ১৯৭০ এর দশকে শুরু হয় নারীবাদের এই নবযাত্রা। একই সুরে তাঁর ১৯৯০ সালে প্রকাশিত 'জেন্ডার ট্রাবল' গ্রন্থে জুডিথ বাটলার বলেন, নারী একটি কল্পিত সত্ত্বা (The identity of ‘woman’ is a fiction)। নারী নামক সত্ত্বা বর্তমান, কারণ সমাজ নারী নামক যে সত্ত্বা তৈরি করেছে নারী সেই সত্ত্বার চাওয়া অনুসারে কাজ করছে। সমাজের চাওয়া অনুসারে সম্পাদিত নারীর ঐ কাজগুলোর বাইরে নারী নামক কোনো মৌলিক সত্ত্বা নেই। এই সামাজিক ভূমিকার চাপ নারীর লেখক হয়ে ওঠার ও লেখক পরিচিতির পথে সবচেয়ে বড় বাধা। সুতপা ভট্টাচার্য মনে করিয়ে দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে শক্তি চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত সকলেই মেয়েরা আদৌ কবিতা লিখতে পারে কিনা তা নিয়ে সশংয়দীর্ণ। তিনি নিজেই দিয়েছেন উত্তর :
“সত্যিই তো মেয়েরা কল্পনা করতে পারেই না। কবিতা লিখতে চায় যদি কোনো মেয়ে, তবে হয়তো তার বালিকা বয়সেই সে অনুভব করে নিজের কল্পনাশক্তির সীমা...। কিন্তু এমনটাই তো হবার কথা। কল্পনা যে করে সেই বিষয়ীকে নিজের মধ্যে চিনে নেওয়া মেয়েদের পক্ষে কি সহজ? যে ভাষা দিয়ে সে কল্পনা করবে, যে ছবি দিয়ে সে কল্পনা করবে, সেই ভাষা সেই ছবি পুরুষ–পেষিত সমাজের, তার সাহিত্যের। সে ভাষা সে ছবি মেয়েদের শেখায় পুরুষ নির্দেশিত এক ভুল ঐকাত্ম্য। সাহিত্যের পরম্পরা থেকে মেয়েরা সাধারণত সেই ভুল ঐকাত্ম্য গ্রহণ করে এবং প্রতিফলিত করে। নিজেকে বিষয়ী হিসেবে জানতে গেলে কোনো মেয়েকে ঘুরে দাঁড়াতে হয় সেই পরম্পরার বিপরীত মুখে।''
(সুতপা ভট্টাচার্য, ‘কবিতায় নারী, নারীর কবিতা’, মেয়েলি পাঠ, পৃঃ ৪৪)
বিষয়ের বদলে বিষয়ী হয়ে ওঠা লেখক ওঠার রোখ কবিতা সিংহের লেখায় স্পষ্ট: "না আমি হব না মোম আমাকে জ্বালিয়ে ঘরে তুমি লিখবে না…"
এই যে পুরুষের ভাষার কথা বললেন সুতপা ভট্টাচার্য, এও নারী সাহিত্যিকের পথে সে এক চিরকালীন অন্তরায়। ভার্জিনিয়া উলফ বলেন, লিখতে গিয়ে নারী দেখল যে তাদের লেখার জন্য কোনো ভাষাই তৈরি নেই। পুরুষরা এতকাল লিখে লিখে যে ভাষাটি নির্মাণ করেছে সেটি নারীর লেখার ভাষা হওয়ার নয়। হেলেন সিকশু লেখেন, মেয়েদের মাতৃদুগ্ধের সাদা কালি দিয়ে সব নতুন করে নতুন ভাষায় লিখতে হবে, সে কল্পিত ভাষার নাম তিনি দেন ‘এক্রিতুর ফেমিনিন’ (ecriture feminine)। (দ্য লাফ অফ মেডুসা)
সাহিত্যের অঙ্গনে নারীবাদের তৃতীয় কাজ হল ক্যানন বা মূলধারার বাইরে থেকে যাওয়া নারীসাহিত্য বা 'গাইনোটেক্সট' খুঁজে বের করা। এই লেখায় বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত অ-খ্যাত নারী সাহিত্যিকদের মধ্য থেকে যে তিনজনকে প্রতিনিধিত্বমূলক উদ্দেশ্যে বেছে নিচ্ছি, তাঁরা সকলেই মূলত গদ্যকার। 'ভারতী' ও অন্যান্য পত্রিকা সাক্ষী, গৃহকাজের ফাঁকফোকরে মেয়েদের পক্ষে কবিতা লেখা যদি বা সম্ভব হয়েছে, বৃহদাকার উপন্যাস বা আত্মচরিত লেখা ছিল আরও বেশি কঠিন। অথচ এঁরা তিনজন কিন্তু বিচ্ছিন্ন উদাহরণ নন। এমন নারী আরও ছিলেন। অন্য কোনো অবকাশে তাঁদের আরও কাউকে কাউকে নিয়ে বলা যাবে। অন্তত বলা দরকার।
******
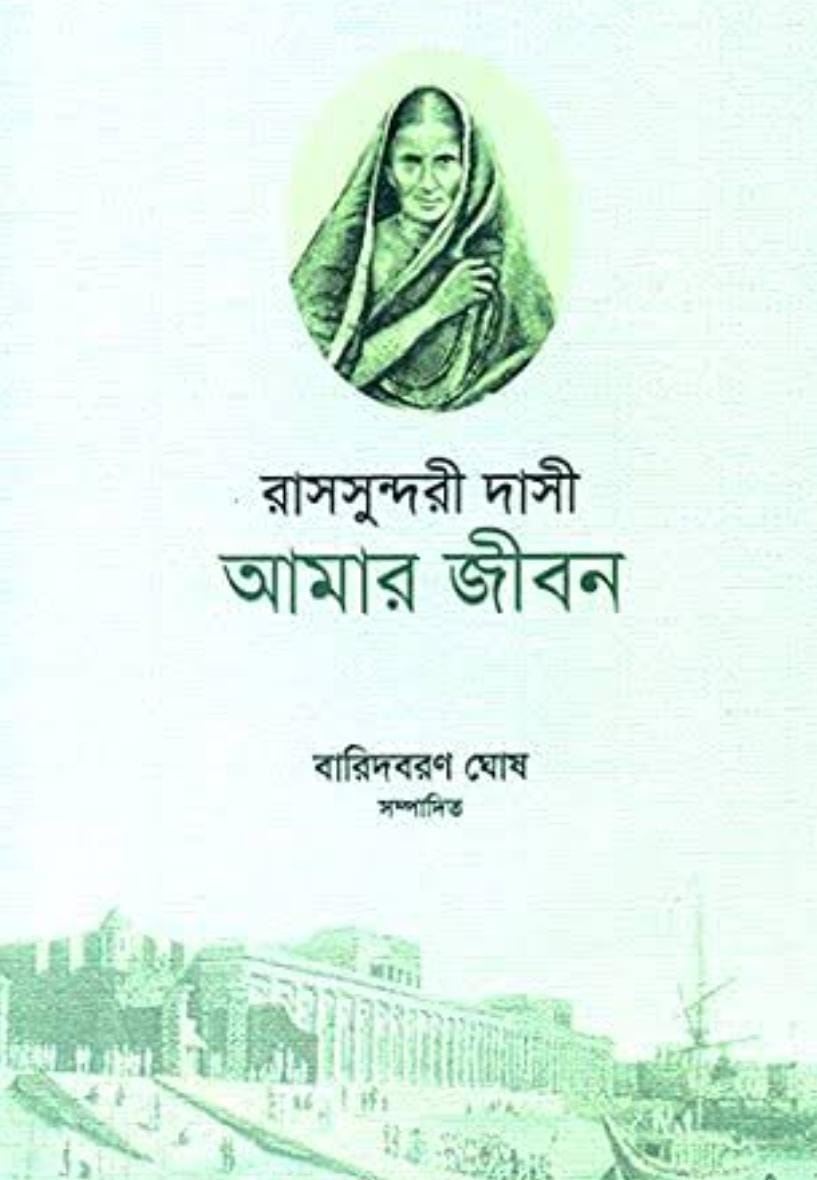
বাংলাভাষা গর্বের অন্যতম কারণ হল, এ এমনই এক ভাষা, যে ভাষার প্রথম আত্মজীবনী এক নারীর লেখা। রাসসুন্দরী দেবীর ‘আমার জীবন’। ১৮১০ খ্রিস্টাব্দে পুববাংলার এক গ্রামে জন্মেছিলেন এই অনামা, সাধারণ, সহজ, সরল, ঈশ্বরবিশ্বাসী মেয়ে। 'ভারতবর্ষ' কথাটিকে তিনি এমন ভাবে ব্যবহার করেছেন নিজের লেখায় যে, মনে হয় তা পৃথিবীর সমার্থক।
বারো বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল তাঁর৷ 'আমার জীবন' প্রথম প্রকাশিত যখন হয়, তখন তাঁর বয়স সাতষট্টি। প্রথম থেকে তৃতীয় সংস্করণ পর্যন্ত বইয়ের কলেবর ক্রমেই বেড়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা যায়, লেখিকার বয়স তখন অষ্টআশি। তৃতীয় সংস্করণটি বেরোয় মরণোত্তর।
বইটির দুটি ভাগ। প্রথম ভাগে ষোলোটি পরিচ্ছেদ। দ্বিতীয়টিতে পনেরটি। প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শুরুতে আছে দেব-দেবীর বন্দনা, যা থেকে বোঝা যায়, লেখিকা কবিতায় হাত দিলেও মন্দ লিখতেন না। মেয়েদের আত্মজীবনী, তা রাসসুন্দরীর 'আমার জীবন', বিনোদিনী দাসীর 'আমার কথা', সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেয়া' বা মানদা দেবীর 'শিক্ষিতা পতিতার আত্মচরিত' যাই হোক না কেন, সেখানে নিজের পরিপার্শ্বকে লিখে রাখেন মেয়েরা। আবার একইসঙ্গে নিজেকেও লেখেন বৈকি! বিনোদিনী যখন সংসারহীনতার কথা বলেন, অথবা সাহানা বলেন 'সংসার করতে ভাল লাগত না', তখন সামাজিক লিঙ্গভূমিকাকে প্রাকৃতিক বলে চালানোর প্রবঞ্চনা ভেঙে পড়ে।
রাসসুন্দরীর বর্ণনাতেও সেকালের রক্ষণশীল সমাজের নিখুঁত ছবি।
"আমার মনে মনে নিতান্ত চেষ্টা হইল লেখাপড়া শিখিয়া পুঁথি পড়িব৷ কিন্তু আমার অদৃষ্টক্রমে তখন মেয়েছেলে লেখাপড়া শিখিত না।… তখনকার লোকে বলিত, 'বুঝি কলিকাল উপস্থিত হইয়াছে দেখিতে পাই। এখন বুঝি মেয়েছেলেতেও পুরুষের কাজ করিবে।… দিনে দিনে আর কত দেখিব৷ এখন যেমত হইয়াছে, ইহাতে আর ভদ্রলোকের জাতি থাকিবে না। এখন বুঝি সকল মাগীরা একত্র হইয়া লেখাপড়া শিখিবে।'... লোকনিন্দার ভয়ে লেখাপড়া শেখা হইল না।"
একথা সুবিদিত যে স্ত্রীশিক্ষার বিরােধিতায় সর্বশক্তি প্রয়ােগ করেছিলেন সনাতপন্থীরা। মেয়েরা শিক্ষা লাভ করলে সমাজ-সংসার রসাতলে যাবে, তাই এই অপপ্রয়াস বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা। ভূধর চট্টোপাধ্যায়ের ‘বেদব্যাস’ পত্রিকা লিখেছিল,
“প্রকৃত বিদ্যাশিক্ষাও নারীর পক্ষে অমঙ্গলের কারণ। কেননা ইহার দ্বারা নারীর পুত্র প্রসবােপযােগিনী শক্তিগুলির হ্রাস হয়। বিদূষী নারীগণের বক্ষদেশ সমতল হইয়া যায়, এবং তাঁহাদের স্তনে প্রায়ই স্তন্যের সঞ্চার হয় না, এতদ্ভিন্ন তাহাদের জরায়ু প্রভৃতি বিকৃত হইয়া যায়।..বিদ্যা নানারূপে আমাদের মঙ্গলের কারণ হইলেও নারীগণের পরম শত্রু।”
কবি ঈশ্বর গুপ্ত লিখলেন—
“যত ছড়ীগুলাে তুড়ি মেরে,
কেতাব হাতে নিচ্ছে যবে।
তখন এবি শিখে বিবি সেজে,
বিলাতী বােল কবেই কবে।''
সেই সময়েরই ফার্স্ট-পার্সন বর্ণনা রাসসুন্দরীর আত্মজীবনীতে।
উনবিংশ শতকের এক বধূ যখন নিজের আত্মজীবনীতে নিজের গার্হস্থ্য ভূমিকার সঙ্গে তুলনা করেন কলুর বলদের, তখনও নারীর কল্যাণী মূর্তিনির্মাণের পিছনে পিতৃতান্ত্রিক স্বার্থ স্পষ্ট হয়।
''বুক পর্যন্ত ঘোমটা দিয়া সকলকাজ করিতাম। সে কাপড়ের মধ্য হইতে বাহিরে দৃষ্টি হইত না। যেন কলুর বলদের মতো দুইটি চক্ষু ঢাকা থাকিত। আপনার পায়ের পাতা ভিন্ন অন্য কোনো দিকে দৃষ্টি চলিত না৷"
রাসসুন্দরী বর্ণনা দেন তাঁর গৃহকাজেরও। দুবেলা দশ বারো শের চালের ভাত রান্না। সঙ্গে ব্যাঞ্জনাদি। তার মধ্যেও,
''কেবল দিবারাত্র পরমেশ্বরকে ডাকিয়া বলিতাম, পরমেশ্বর! তুমি আমাকে লেখাপড়া শিখাও, আমি নিতান্ত শিখিব।''
পুত্রদের লেখা তালপাতা থেকে তাঁর অক্ষরজ্ঞানের সূত্রপাত। তা থেকে রান্নাঘরে লুকিয়ে 'চৈতন্যভাগবত'-এর একটি ছেঁড়া পাতা পড়ে ফেলা। এভাবে যাঁর পড়তে শেখা ধীরে ধীরে, তাঁর লেখায় সিদ্ধি লাভ আরও কঠিন ছিল। এ কাজে উৎসাহ দিয়েছিলেন সপ্তম পুত্র, কলকাতায় পাঠরত কিশোরীলাল৷ কিশোরীলাল তাঁকে কাগজ-কলম-কালির দোয়াত কিনে দিয়েছিলেন, যাতে মায়ের থেকে নিজের প্রেরিত পত্রের উত্তর পান।
সব কাজ শেষ করে, দিনশেষে, বা মধ্যাহ্নের নীরব নির্জন ক্ষণে খাতা খুলে সামান্য অক্ষরজ্ঞানের সমস্তটা উজাড় করে দিয়ে লিখে রাখা মনের কথা, একান্তে সখীদের বলার কথাগুলি, দিনান্তে নিজের আয়নার সামনে বসে নিজেকে বলার কথাগুলি শব্দে আর অক্ষরে প্রকাশ করে রাখা — এই হল মেয়েদের আত্মকথার নির্যাস। যখন তাঁরা লিখছেন, তখন লেখার মাধ্যমেই তাঁরা যেন বুঝতে পারছেন যে শুধু নারীসুলভ ভূমিকা পালনেই তাঁদের অস্তিত্ব শেষ হয়ে যায় না। বলতে পারছেন যেন, কৃষ্ণভাবিনী দেবীর ভাষায়, ''রমনী নিজের নিমিত্তও বাঁচিয়া থাকে।''
প্রশ্ন ওঠে, এহেন লেখায় বিষয়বৈচিত্র্য কোথায়? সার্বিক ভাবে নারীসাহিত্য নিয়েও এ প্রশ্ন ওঠে। আশাপূর্ণা দেবীর মতো জনপ্রিয় লেখকও 'হেঁশেলের-অন্দরের লেখক' হয়ে যান। অথচ কবি সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায় যে বলেছিলেন, “কবিতা মানে আমার কাছে এই। নিজেকে রক্তাক্ত হতে দেখা ও একইসঙ্গে সেই রক্ত পান করা।" রাসসুন্দরী থেকে শুরু করে বাংলার কত যে নারীর সাহিত্যে সে নিজ রুধীর পানের বেদনা!
তাঁদের শ্রোতা থাকে না, পাঠক থাকে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কেউ জানতেও পারে না তাঁদের লেখার কথা। ভয়ে, সংশয়ে, কুন্ঠায় তাঁরা নিজেদের লেখা অন্য কাউকে দেখান না। অন্য মানে শিক্ষিত পুরুষ, স্বামী-শ্বশুর-ভাশুর— যাঁরা সমাজে লেখালেখির জন্য নির্বাচিত, ক্ষমতায়িত। রাসসুন্দরীর বইটি শেষ হয় যে কুণ্ঠা নিয়ে, তা প্রান্তিকীকরণের রাজনীতিকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখায়।
''এই বইখানি আমি নিজ হাতে লিখিয়াছি৷ আমি লেখাপড়া কিছুই জানি নে। অধিকারী মহাশয়েরা, তোমরা যেন অবহেলা না করো৷ দেখিয়া ঘৃণা করিও না৷ অধিক লেখা বাহুল্য।''
কারা এই অধিকারী মহাশয়? তাঁরা কিসের অধিকারী? আর সে অধিকার তাঁরা হস্তান্তর করেন কাদের?
প্রশ্নগুলো সহজ, উত্তরও তো জানা।
*****
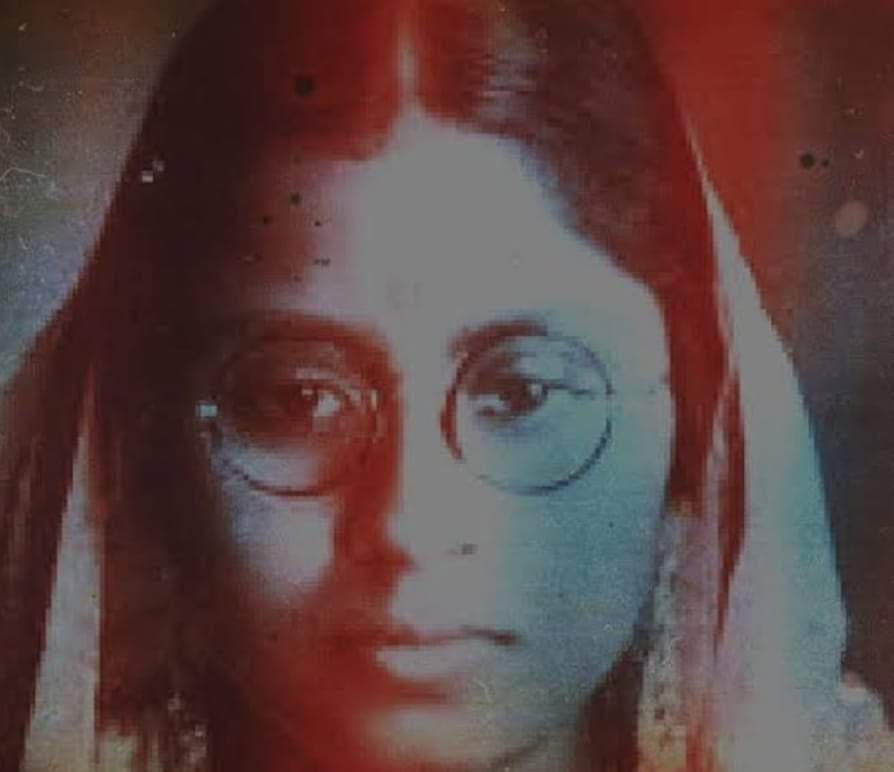
এই যে কুণ্ঠায় লুকিয়ে লুকিয়ে লেখা, লেখা প্রকাশ না করা, তা বাংলা উপন্যাসের জগতে নারীর প্রবেশের সঠিক সময়কালকে ধোঁয়াশায় আবৃত রেখেছে। এ প্রসঙ্গ উত্থাপনের কারণ হল, অন্য যে দুজন নারীকে প্রতিনিধিত্বমূলক উদ্দেশ্যে নির্বাচন করা হয়েছে এ লেখার জন্য, তাঁরা দুজনেই ঔপন্যাসিক। তাই নারীর উপন্যাসের ইতিহাস কিছু জানা প্রয়োজন। হেমাঙ্গিনী দেবীর দুটি উপন্যাসের সন্ধান পাওয়া যায়: ‘মনোরমা’ ও ‘প্রণয়প্রতিমা’। ‘মনোরমা’র রচনাকাল ১২৭২ বঙ্গাব্দ (১৮৬৫ খ্রিস্টাব্দ)। বাংলা ভাষায় প্রথম স্বীকৃত উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' সে বছরেই প্রকাশিত৷ কিন্তু 'মনোরমা'-র প্রকাশকাল ১২৮১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দ। বইটির ‘উৎসর্গপত্র’ জানায়, ১২৭২ সালে ‘মনোরমা লিখিত হলেও ‘ইহা মুদ্রাঙ্কনের নিতান্ত অযোগ্য জানিয়া এ পর্যন্ত কাহাকেও না দেখাইয়া ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম।’ সুকুমার সেন স্বয়ং সে কথা আমাদের জানান।
আরেক উপন্যাস আবিষ্কার করেছিলেন অদ্রীশ বিশ্বাস। সেটি লেখা ছদ্মনামে, ‘হিন্দুকুল-কামিনী প্রণীত’। সাল ১৮৬৮। কে এই হিন্দুকুল-কামিনী তা সঠিক ভাবে জানা যায়নি। বইটিতে কোনও প্রকাশকের নাম নেই, মুদ্রকের নাম আছে। পরে অবশ্য অদ্রীশবাবু আরও খুঁজে পেলেন, ‘নবপ্রবন্ধ’ নামক মাসিক পত্রিকায় ১৮৬৭ সালে প্রায় এক বছর ধরে ‘মনোত্তমা’ ধারাবাহিক হিসেবে বের হয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষায় যখন বঙ্কিমচন্দ্র তথাকথিত 'প্রথম উপন্যাস' লিখছিলেন, সেই সমসময়েই অনেক মেয়ে উপন্যাস লিখতে শুরু করেছেন, কিন্তু গোপনে।
বিংশ শতকের শুরুতে অনুরূপা দেবী ও নিরুপমা দেবীর উপন্যাসগুলি যদি বিষয়ে ও চরিত্রায়নে নারীর সনাতনী রূপটিকেই প্রতিষ্ঠা করে, তবে সেই রূপের অন্তরালে থাকা নির্যাতন নিয়ে মুখর হলেন শৈলবালা ঘোষজায়া। শৈলবালা ঘোষজায়ার জন্ম উনিশ শতকের শেষ দিকে, ১৮৯৪ সালের ২ মার্চ, কক্সবাজারে৷ তেরো বছর বয়সে বিয়ে। বৈবাহিক সঙ্গীর উৎসাহে, তাঁর হাত দিয়েই 'প্রবাসী'র দপ্তরে পাঠিয়েছেন 'সেখ আন্দু' নামের উপন্যাসটি। কিন্তু এ সুখ বেশিদিন সয়নি৷ স্বামী উন্মাদ হলেন। তিনি আরও দশ বছর বেঁচে ছিলেন এর পরও। পরবর্তীকালে অত্যাচার করতেন, গঞ্জনা দিতেন শোনা যায়। অথচ ১৩৩৪ সনে স্বামীর মৃত্যু, আত্মীয়দের প্রবঞ্চনা, নিরাপত্তাহীনতা, আর্থিক অনটনের মধ্যে অক্লান্ত লিখে চলেছিলেন শৈলবালা। মেমারির শ্বশুরবাড়ি থেকে উৎখাত হয়ে জীবনের শেষ কুড়ি বছর কাটিয়েছেন পুরুলিয়ার রামচন্দ্রপুরের এক ধর্মীয় আশ্রমে৷ শৈলবালা 'ঘোষ' না লিখে 'ঘোষজায়া' লিখতেন সম্ভবত শ্বশুরবাড়ির লোকেদের চোখে ধুলো দেওয়ার জন্য। 'শৈলবালা ঘোষ' নামেই যারা তাঁকে জানে, তারা 'ঘোষজায়া' দেখলে ভাবত, অন্য কেউ।
এখন বিজেপি যাকে বলে 'লাভ জিহাদ', অর্থাৎ হিন্দু মেয়ে ও মুসলমান পুরুষের প্রেম বা বিবাহ, যা নিয়ে বিরোধী আইন করেছে কয়েকটি রাজ্য, সেই বিধর্মী প্রেমকে খুব সহজেই উপন্যাসে ঠাঁই দিয়েছেন এই নারী ঔপন্যাসিক। তাও, আজ থেকে প্রায় একশ বছর আগে। উপন্যাসের নায়ক সেখ আন্দু জমিদারের ড্রাইভার। শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র। তার প্রেমে পড়ে জমিদারের মেয়ে লতিকা৷ বালিকাসুলভ সে একতরফা আকুতিতে প্রতাপশালী জমিদারের দিক থেকে বিপদ ঘনিয়ে আসছে দেখে, সেখ আন্দু গ্রাম ছেড়ে পালায়। কিন্তু পরবর্তীতে সে নিজেও এক হিন্দু বিধবার প্রেমে পড়ে— সে লতিকার বান্ধবী জ্যোৎস্না। সে প্রেম উভয় দিকেই প্রস্ফুটিত হয়, কিন্তু তা পরিপূর্ণতা পায় না৷ উপন্যাসের শেষে বিধবা জ্যোৎস্নার গন্তব্য হয় দ্বারকা, আন্দুর মক্কা।
মুসলমান সমাজের সঙ্গে লেখিকার ঘনিষ্ঠতার কোনো তথ্য তাঁর জীবনপঞ্জিতে মেলে না। কিন্তু 'নমিতা', 'মিষ্টি সরবত', 'অভিশপ্ত সাধনা', 'ইমানদার' বা 'অবাক'— এসব উপন্যাসে মুসলমান মানুষেরা প্রায়শই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। নমিতা নিজে নার্স, কিন্তু তার সঙ্গে সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে ওঠে এক প্রৌঢ়া মুসলিম গামছাওয়ালির। 'ইমানদার'-এ ফৈজু হিন্দু জমিদার মনিবের ইমানদার লেঠেল, কিন্তু আপন ঘরে সে স্ত্রী টিয়া-র বাধ্য স্বামী। চারবার নিকাহ্ দূরস্থান, সে বিবির অসুস্থতায় উতলা হয়ে নিজের সামর্থ্য অতিক্রম শহর থেকে ডাক্তার আনে। ফৈজু বৈষ্ণব মঠের মোহান্তকে বাধা দেয় শিশুনির্যাতনে। ক্রুদ্ধ মোহান্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় ইন্ধন দেয়। 'অভিশপ্ত সাধনা'-য় মুসলমান মেয়ে রাবেয়া নিজের সমাজের সব সংস্কার তুচ্ছ করে স্বাবলম্বী হবেই হবে। 'অবাক'-এ একই পণ নিয়েছে এক মুসলিম ব্যারিস্টার তনয়া। অদ্ভুত ব্যাপার হল, শৈলবালার উপন্যাসে হিন্দু নারীরা কিন্তু প্রায়শই নির্যাতিতা, ভূলুণ্ঠিতা। এত তেজ তাদের নেই, যা আছে মুসলমান মেয়েদের। আর হিন্দু পুরুষ প্রায়শই নির্যাতক। নিজের সমাজে মুক্তি খুঁজে পাননি বলেই কি তিনি অন্যতর সমাজে রূপকথা খুঁজেছেন?
শুধু মুসলমান নয়, অন্ত্যজ শ্রেণির মধ্যেও শৈলবালা আদর্শ নায়কদের খুঁজে পান। 'রঙিন ফানুস' উপন্যাসে খন্তর কুর্মি এক মিস্ত্রী। সংযম ও সততা তার চরিত্র বৈশিষ্ট্য। 'গঙ্গাপুত্র' উপন্যাসে ব্রাহ্মণবধূ ও লালু ডোমের মিলন ঘটান লেখিকা, কী জানি কোন সাহসে! মৃত্যুপথযাত্রী বধূটি ঝড়জলের রাতে পরিত্যক্ত হয়েছিল। সৎকার হয়নি। প্রাণ বেঁচেছিল তার ডোমের সেবায়, যদিও পূর্বজন্মের স্মৃতি লোপ পায়৷ সে নতুন নাম পায়— লক্ষ্মী৷ অসবর্ণ প্রতিলোম বিবাহ হয় তার সঙ্গে লালুর। লেখিকা এক অধ্যাপকের মুখ দিয়ে বলান, লালু ''অনেক কদাচারী তথাকথিত ব্রাহ্মণের চেয়ে বড় ব্রাহ্মণ্য গৌরবের অধিকারী।''
শৈলবালা যখন হিন্দু পরিবারের কথা লেখেন, তখন সেখানে অবধারিত ভাবে এসে পড়ে গৃহহিংসার বর্ণনা। বস্তুত গৃহহিংসার কথা এত অকপটে এই প্রথম বাংলা সাহিত্যে বলা হল। শৈলবালা-র উপন্যাসের পর উপন্যাসে এক মেয়ের কলমে আমরা পেলাম গোপন গৃহহিংসার বর্ণনা। 'জন্ম-অপরাধী' উপন্যাসে পদাঘাতে অন্ত:স্বত্ত্বার মৃত্যু হয়। 'জন্ম-অভিশপ্তা' উপন্যাস স্পষ্ট উচ্চারণ করে, খুঁটে বাঁধা গরুর মতো পরাধীন দশা নির্যাতিতার, আর সেই হল নির্যাতিতর মূলধন —
''জানে পাপ যাবে কোথা? যতবারই যত তাচ্ছিল্য যত যন্ত্রণা দিয়ে দগ্ধে মারি না কেন, ফিরে আমদেরই হাতে পড়তে হবে তো? অতএব এই প্রভুত্বের প্রতাপ ছুটিয়ে সার্থক করে নিই, সেই তো পরম পৌরুষ।"
'অরু' উপন্যাসে অরু শিক্ষিতা। স্বামী মদ্যপ নির্যাতক। যে অরুকে 'পতিভক্তিহীনা' বেশ্যা বলে বাড়ি থেকে বার করে দেওয়া হয়, সেই অরু অনেকাংশে যেন শৈলবালা। স্বামীর মৃত্যুর পর অরুও শৈলবালার মতোই নিজের মনোমতো জীবন বেছে নেন। বৈধব্যে আত্মসমর্পণ না করে অরু বেছে নেয় শিক্ষয়িত্রীর জীবন। বয়স্কাদের শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের ব্যবস্থা করার কাজেও ব্রতী হয় সে। 'তেজস্বতী' উপন্যাসে দেখি, মেয়েদের লেখাপড়া ও চাকরি করা নিয়ে এক লম্পট পুরুষ দেবেন সেই রাসসুন্দরী দেবীর সময়ের মতোই রক্ষণশীল থেকে গেছে পরের শতকেও। সে বলে,
"মেয়েমানুষকে লেখাপড়া শেখালে- সে উচ্ছন্ন যায়, লোকে বলে ঠিক।"
গৃহহিংসার নির্যাতিতারা তাঁর উপন্যাসে অধিকাংশ সময়েই বাচিক ভাবে প্রতিবাদী। কিন্তু তারা সম্পর্ক ছেড়ে বেরিয়ে আসছে না— বলা ভাল, বেরোতে পারছে না। বিবাহ বিচ্ছেদ ও নারীর স্বাধীন জীবনযাপন সেইসময় অলীক কল্পলোক বলেই সে পথ পরিহার করেছেন লেখিকা। এ তাঁর রক্ষণশীলতা নয়, বাস্তবানুরাগ মাত্র। কিন্তু হিন্দু দাম্পত্যের মুখ থেকে রোম্যান্টিসিজমের মুখোশ যেভাবে টেনে ছিঁড়েছেন, তাতে ভাবতে অবাক লাগে, এমন পূর্বজা থাকতে মেয়েরা আজও গৃহহিংসা নিয়ে মুখে কুলুপ আঁটে কেন?
*****

শেষত যাঁর কথা বলব, তিনি চল্লিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বিস্তার করেছেন তাঁর লেখক-ডানা। সে উড়ান বহাল থেকেছে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ জুড়ে। সাবিত্রী রায়। এভাবে পঞ্চাশ-ষাট দশকের রাজনীতির বামপন্থী গতিধারার ফিকশনাল খতিয়ান কেউ রেখে যাননি নারীপুরুষনির্বিশেষে।
প্রাক-স্বাধীনতা ও স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ঘূর্ণাবর্ত, বিশেষত কমিউনিস্ট পার্টির কর্মকাণ্ড, অতি বাম মতাদর্শ ও তার বিপদ বা বিচ্যুতি, নানবিধ রাজনৈতিক বিতর্ক তাঁর উপন্যাসগুলিকে ওতপ্রোত জড়িয়ে আছে৷ আশ্চর্য ডায়লেক্টিকাল তাঁর বৃহদাকার উপন্যাসগুলি, যেখানে এক অশেষ প্রশ্নকারিণী অবাধ্য ধীময়ীকে খুঁজে পাই। ব্যক্তি থেকে সমষ্টি, সমষ্টি থেকে ব্যক্তিতে অবাধ বিচরণ করে তাঁর উপন্যাসগুলো। লেখক হিসেবে তিনি স্রেফ ভদ্রবিত্ত সমাজে আটকে না থেকে এক বিরাট ক্যানভাস সৃষ্টি করতে ভালবাসতেন৷ অথচ
তৎকালীন বামধারার সাদা-কালো মোটা দাগের সাহিত্য এ নয়। তাঁর লেখা দ্বিধাকীর্ণ ও প্রশ্নমুখর৷
ঢাকার উয়াড়িপল্লিতে তাঁর জন্ম ১৯১৮ সালে। বেথুন কলেজে পড়তে কলকাতায় আসা। শিক্ষকতা করেছেন একাধিক স্কুলে৷ বিয়ে হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতা শান্তিময় রায়ের সঙ্গে৷ ১৯৪৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন৷
প্রথম উপন্যাস 'সৃজন।' এসময়েই সহিংস বিপ্লবীরা কারারুদ্ধ অবস্থায় ধীরে ধীরে মার্ক্সবাদের দিকে ঝুঁকছেন। তাঁদেরই প্রতিনিধি দুখু ওরফে বিশ্বজিত।
সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে সাবিত্রী যখন নেত্রকোণা যান, তখন সেখানে হাজং এলাকার প্রতিনিধি মেয়েরাও এসেছিলেন৷ তাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই 'পাকা ধানের গান' লেখার কথা মাথায় আসে৷ এই উপন্যাস দেয় গ্রামজীবনের বর্ণনা আর কৃষক বিদ্রোহের খতিয়ান। ‘পাকা ধানের গান’-এর মূল চরিত্র পার্থ যখন হাজং আন্দোলনের কালে মিলিটারির গুলিতে প্রাণ দেয়, সাবিত্রীর কলম সে বর্ণনায় দৃঢ়। তাঁর দুই ম্যাগনাম ওপাস— তিন খণ্ডে ‘পাকা ধানের গান’, দু’খণ্ডে ‘মেঘনা পদ্মা’ (তার তৃতীয় খণ্ড আবার ‘সমুদ্রের ঢেউ’ নামে আলাদা উপন্যাস হিসেবে) অবশ্য লেখা হয়েছিল তাঁর সবচেয়ে জটিল উপন্যাস 'স্বরলিপি'-র পর।
‘স্বরলিপি’ প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। সে তাঁর তৃতীয় উপন্যাস। এর উৎসর্গে ছিল ১৯৪৯ এর খাদ্য আন্দোলনের শহিদ-লতিকা, অমিয়া, গীতা, প্রতিভা আর বাদলের নাম। বৃহৎ ও বিস্তৃত এই উপন্যাসে গল্পে ঢুকতেও অনেকটা সময় লাগে, কারণ নানা ডিসকোর্সের দার্শনিক সংঘাতও এ উপন্যাসের উপজীব্য, শুধু কাহিনীবস্তু নয়।
চল্লিশের দশকের জটিল ও রক্তাক্ত রাজনীতি— বিয়াল্লিশের অগস্ট আন্দোলন, তেভাগা আন্দোলন, হাজং বিদ্রোহ, দেশভাগ, দাঙ্গা, উদ্বাস্তু সমস্যা, কলোনি গড়ে ওঠা, হিন্দু উদবাস্তুদের মধ্যে ধিকি ধিকি মুসলমান বিদ্বেষ ও তার সুযোগে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার বিকাশ— সবই ধরেছেন তিনি। ঘটনা ঘটে চলেছে মূলত পশ্চিমবঙ্গ ও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জুড়ে। উপন্যাসের প্রেক্ষাপট, বোঝাই যাচ্ছে, ১৯৪৮ সাল থেকে পঞ্চাশ সাল, যখন স্বাধীনতা-উত্তর স্বপ্নভঙ্গের পর কমিউনিস্ট পার্টি ঘোষণা করেছে 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়।' ঘোষণা করেছে যে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শক্তির ভারসাম্য সমাজতন্ত্রী শিবিরের দিকে নাকি ঝুঁকে পড়েছে। তেলেঙ্গানা আন্দোলনকে বিপ্লবের সূচনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই সমস্তই তিনি দেখছেন, লিখছেন— কমিউনিস্ট মতাদর্শের প্রতি অটল কিন্তু নির্মোহ থেকে।
নায়ক পৃথ্বীকে কেন্দ্র করে এই সময়ে এই মহাকাব্যিক আখ্যান আবর্তিত হয়। অথচ সেখানে এও দেখানো হয় যে প্রশ্ন করলেই পার্টি বহিষ্কার করে বা বুর্জোয়ক দেগে দেয়। ছাত্র সভায় রেল ধর্মঘটের উপযোগিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলায় দ্রুপদকে ভর্ৎসনা শুনতে হয়। পৃথ্বীকে বহিষ্কার করা হয়। সঙ্গে অধ্যাপক রথীন্দ্রকেও। ফল্গুকে নির্দেশ দেওয়া হয় কৃষক এলাকায় যাওয়ার, কিন্তু ছোট জোতদারের গোলা লুঠ নিয়ে বিতর্ক দেখা দিলে ফের ফেরত আনা হয়৷
অর্থাৎ অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির ভেতরকার দ্বন্দ্ব বা নেতাদের দ্বিচারিতা সোজাসাপটা লিখেছিলেন তিনি। পৃথ্বী, রথী, ফল্গু, শীতাংশু সাগরীর মতো নিবেদিতপ্রাণ পার্টিকর্মীর গায়ে গায়েই সেখানে ঘোরাফেরা করে নন্দলাল, ব্যোমকেশ, মধু মুখার্জির মতো স্বার্থান্বেষী নেতারা। শীতাংশু নামের তরুণ কর্মীটি স্তম্ভিত হয়ে দেখে, সারাদিন না-খাওয়া কৃষক কর্মীদের একটু অর্থ সাহায্যের আবেদন নস্যাৎ করে ব্যোমকেশ তাকে নিয়ে ‘একটু চা খাওয়া যাক’ বলে রেস্তরাঁয় ঢোকে, ডবল কাপ চা আর পুরু অমলেট অর্ডার দেয়। ব্যোমকেশের বাড়িতে শৌখিন আসবাব, নরম গালিচা, বিলিতি কাপে সুগন্ধি চায়ের সঙ্গে সাম্যবাদী নেতার বিপ্লবের বুলিকে মেলাতে পারে না সে। নেতা নন্দলাল কৌশলে বহিস্কৃত রথীন্দ্রর স্ত্রী সাগরীকে টেনে আনে নিজের কমিউনে, সাগরীকে চাপ দেয় রথীকে ডিভোর্স দিতে। তার কামুক নজর পড়েছে বিপ্লবের স্বপ্ন-দেখা মেয়ের উপরে। নন্দলালের স্যাঙাত এক দিন সাগরীকে জানিয়েই দেয়, ‘নন্দলাল is waiting for you...’ দল আর মতাদর্শের মধ্যে ঘাপটি মেরে থাকে যে পিতৃতন্ত্র, রাজনীতি-সচেতন নারীও তার কবল থেকে বাঁচে না। পার্টির মধ্যে 'দাদা কালচার'-এর অনুপ্রবেশ, বিপ্লব করতে আসা মেয়েদেরও যৌনবস্তু ভাবার এই প্রবণতা দাদাদের, তা স্পষ্ট করেন সাবিত্রী
শকুন্তলা, সীতা, ভদ্রা, জয়া— বস্তুত এমন নানা নারীচরিত্র সৃষ্টি করে সাবিত্রী প্রশ্ন রেখে যান, প্রগতিশীল পুরুষও কেন লিঙ্গপ্রশ্নে সাম্যবাদী নয়?
সাগরীর মৃত্যু হয় পুলিসের গুলিতে। দিদিকে সে লিখে যায়, তারা ভুল পথে চালিত হয়েছে৷ উপন্যাস শেষ হয় নতুন আশা, নতুন উদ্দীপনা, নতুন শপথ দিয়ে। কিন্তু যুক্তিহীন আনুগত্য যে আত্মপ্রবঞ্চনা, তা স্পষ্ট বলে যান সাবিত্রী।
এ বই নিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই হইচই পড়েছিল। নিঃশর্ত ক্ষমাপ্রার্থনার ‘আদেশ’ দেওয়া হয়েছিল সাবিত্রীকে। 'স্বরলিপি' প্রকাশের অব্যবহিত পরেই উপন্যাস প্রত্যাহারের নির্দেশ আসে পার্টি থেকে। তিনি সম্মত হননি। অতঃপর পার্টি সভ্য ও সমর্থকদের মধ্যে 'স্বরলিপি' পাঠ নিষিদ্ধ করা হয়। সভ্যপদ ত্যাগ করেন সাবিত্রী। পার্টির বিচ্যুতি চিহ্নিত করায় তাঁকে চলে যেতে হয় অন্তরালে।
'অরণি' পত্রিকায় গল্পও লিখতেন তিনি। তবে বোঝা যায়, উপন্যাসে হাত খুলে খুলতেই তিনি বেশি স্বচ্ছন্দ। তবু ছোটগল্পেও স্বাক্ষর রেখে গেছেন। যেমন, 'ওরা সব পারে' গল্পে যখন দুলজোড়া হারানোর পর তথাকথিত প্রগতিশীল পরিবার নিশ্চিত হয়, কর্মসহায়িকা পারুলই নিয়েছে- "আর কে নেবে। ওরা সব পারে.." তখন প্রগতিশীলতার ভণ্ডামি টুটে যায়। শেষত যে গল্পটাটির কথা বলব, সেটি 'অন্তঃসলিলা'। কি আশ্চর্য, সেখানে মূল চরিত্র শকুন্তলা লিখতে ভালবাসে। নিজের লেখার ঘর দূরস্থান, তার লেখার পাতাও নেই, দোমড়ানো মোচড়ানো হিসাবের পাতায় সে লেখে। বামপন্থী বর তার, যিনি কফি হাউসে তুফান ছোটান চায়ের কাপে। তাঁর কাছে তাচ্ছিল্য পায় স্ত্রীর সেসব লেখাপত্তর। রাসসুন্দরী দেবীর 'অধিকারী মহাশয়গণ' তাহলে এত বছরের ব্যবধানে সাবিত্রীর যুগেও বর্তমান! যে কোনো রাজনৈতিক ও সামাজিক মতাদর্শ নির্বিশেষেই তাঁরা আছেন।
******
ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র পড়ে জানা যায়, নিজের অগ্রজা স্বর্ণকুমারী দেবীর লেখাপত্র, যা এমনকি ইংরেজিতেও অনূদিত হয়েছিল, তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যই করতেন। কি জানি কেন, তবু 'খাতা'-র মতো একটি গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ লিখে যেতে পেরেছিলেন! সে গল্পের উমার মতোই ,অনেক মেয়ের লেখা গোপন খাতাতে থেকে যায় বন্ধু-দাদা-বাবা-জ্যাঠা-স্বামী-পার্টনার বা অন্য পুরুষ সদস্যদের কাছে হাস্যাস্পদ হবার ভয়ে। ভয় আসলে কার? হাস্যাস্পদ করার বা প্রান্তিক করে রাখার কারণ আসলে কী? উমার স্বামীর ভাবনার খেই যখন ধরিয়ে দেন রবীন্দ্রনাথ, তখন বোঝা যায়, ভয়টা পিতৃতন্ত্রের। বহুস্বরের ভয়।
"প্যারীমোহন এই সংবাদ অবগত হইয়া বিশেষ চিন্তিত হইল। পড়াশুনা আরম্ভ হইলেই নভেল-নাটকের আমদানি হইবে এবং গৃহধর্ম রক্ষা করা দায় হইয়া উঠিবে।
তা ছাড়া বিশেষ চিন্তা দ্বারা এ বিষয়ে সে একটি অতি সুক্ষ্ণতত্ত্ব নির্ণয় করিয়াছিল। সে বলিত, স্ত্রীশক্তি এবং পুংশক্তি উভয় শক্তির সম্মিলনে পবিত্র দাম্পত্যশক্তির উদ্ভব হয়; কিন্তু লেখাপড়া শিক্ষার দ্বারা যদি স্ত্রীশক্তি পরাভূত হইয়া একান্ত পুংশক্তির প্রাদুর্ভাব হয়, তবে পুংশক্তির সহিত পুংশক্তির প্রতিঘাতে এমন একটি প্রলয়শক্তির উৎপত্তি হয় যদ্দ্বারা দাম্পত্যশক্তি বিনাশশক্তির মধ্যে বিলীনসত্তা লাভ করে, সুতরাং রমণী বিধবা হয়। এ পর্যন্ত এ তত্ত্বের কেহ প্রতিবাদ করিতে পারে নাই।"
অতঃপর,
"প্যারীমোহন সন্ধ্যাকালে ঘরে আসিয়া উমাকে যথেষ্ট ভর্ৎসনা করিল এবং কিঞ্চিৎ উপহাসও করিল-বলিল, 'শামলা ফরমাশ দিতে হইবে, গিন্নী কানে কলম গুঁজিয়া আপিসে যাইবেন।' "
ভয় হতে ভর্ৎসনা, ভর্ৎসনা হতে ভিন্নকরণ। সেই ট্রাডিশন বুঝি আজও চলছে!
