
হারুকি মুরাকামি ও তাঁর প্রথম উপন্যাস - শোনো বাতাসের সুর
- 05 August, 2022
- লেখক: সৌভিক ঘোষাল
জাপানী কথাকার হারুকি মুরাকামি বর্তমান বিশ্বের বিশিষ্ট ও জনপ্রিয়তম ঔপন্যাসিকদের অন্যতম। তাঁর লেখা উপন্যাসগুলির মধ্যে রয়েছে হিয়ার দ্য উইন্ড সিং, পিনবল ১৯৭৩, আ ওয়াইল্ড শিপ চেজ, হার্ড বয়েলড ওয়ান্ডারল্যান্ড অ্যান্ড দ্য এন্ড অব দ্য ওয়ার্ল্ড, নরওয়েজিয়ান উড, ড্যান্স ড্যান্স ড্যান্স, সীমান্তের দক্ষিণে সূর্যের পশ্চিমে, দ্য উইন্ড আপ বার্ড ক্রনিকল, স্পুটনিক স্যুইটহার্ট, কাফকা অন দ্য শোর, আফটার ডার্ক ইত্যাদি।
এছাড়া হাতি গায়েব, আফটার দ্য কোয়েক, ব্লাইন্ড উইলো স্লিপিং উওমেন, নারী বিবর্জিত পুরুষেরা ইত্যাদি নামের বেশ কিছু জনপ্রিয় গল্পগ্রন্থও তিনি লিখেছেন।
কলকাতার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় সহ এপার বাংলা ওপার বাংলা মিশিয়ে বিভিন্ন প্রকাশনসংস্থা থেকে মুরাকামির বেশ কিছু উপন্যাস ও গল্পগ্রন্থের অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা মুরাকামির ওপর বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছে। তাঁকে নিয়ে দুই বাংলাতেই চর্চা ক্রমবর্ধমান।
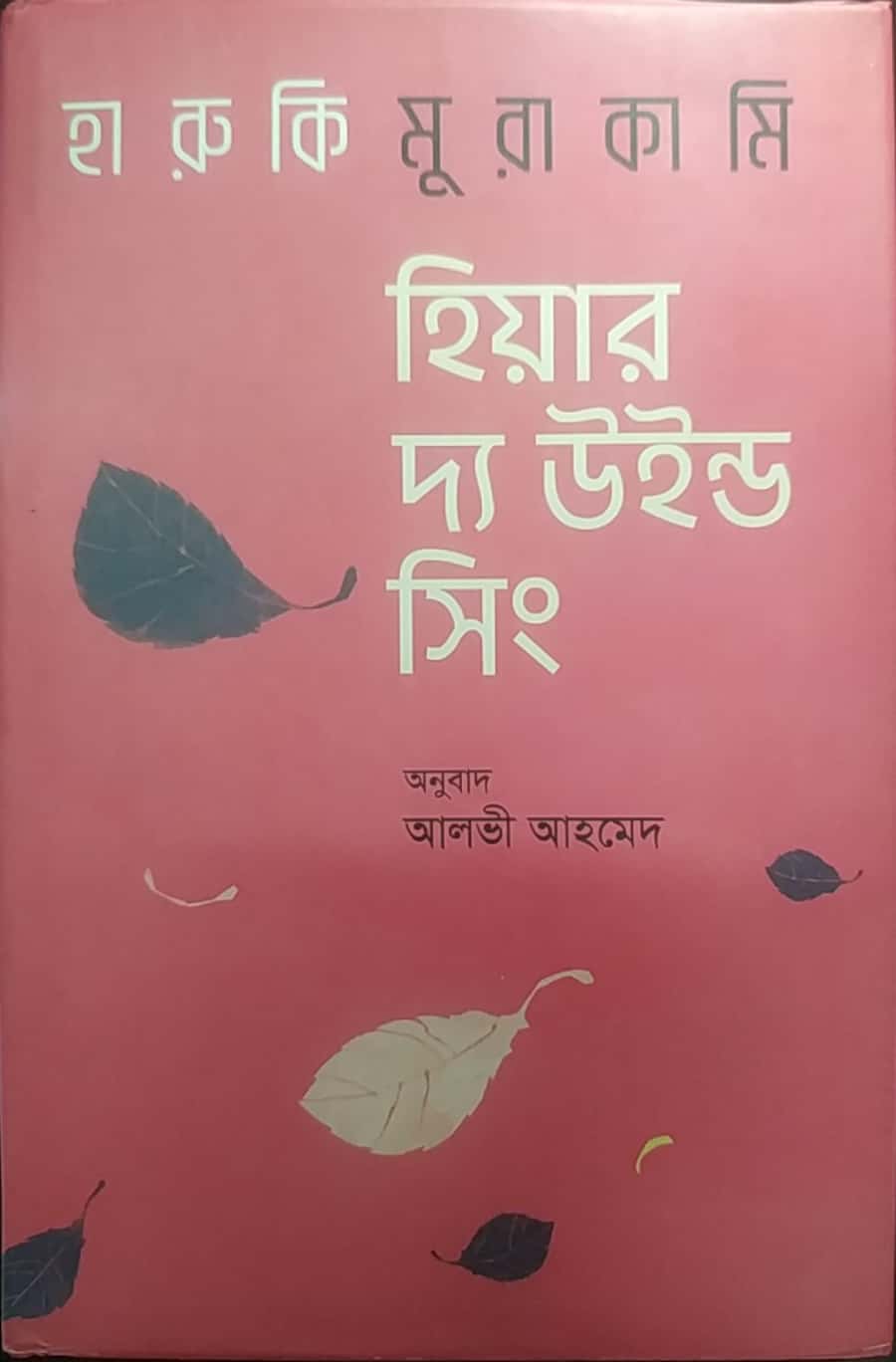
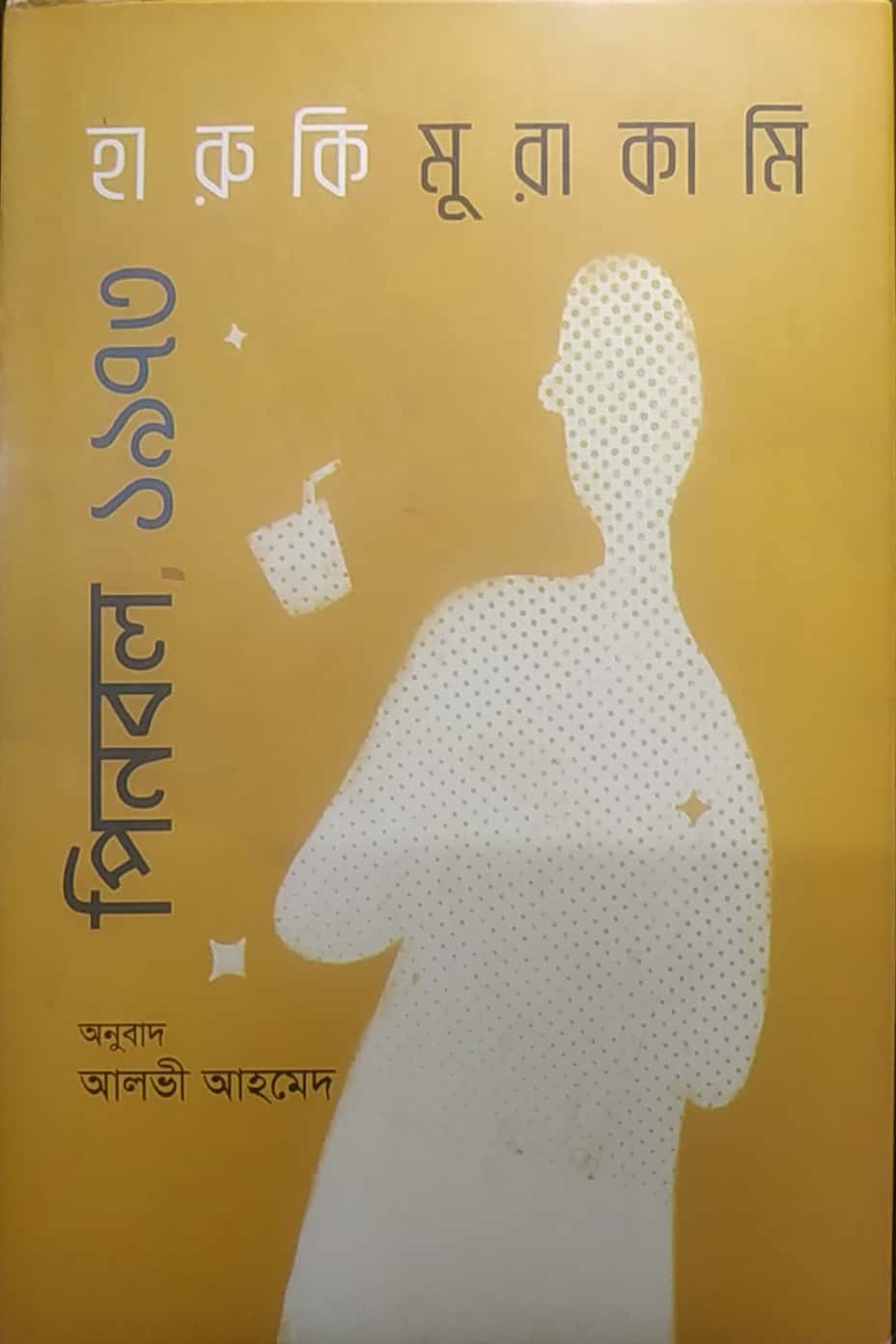
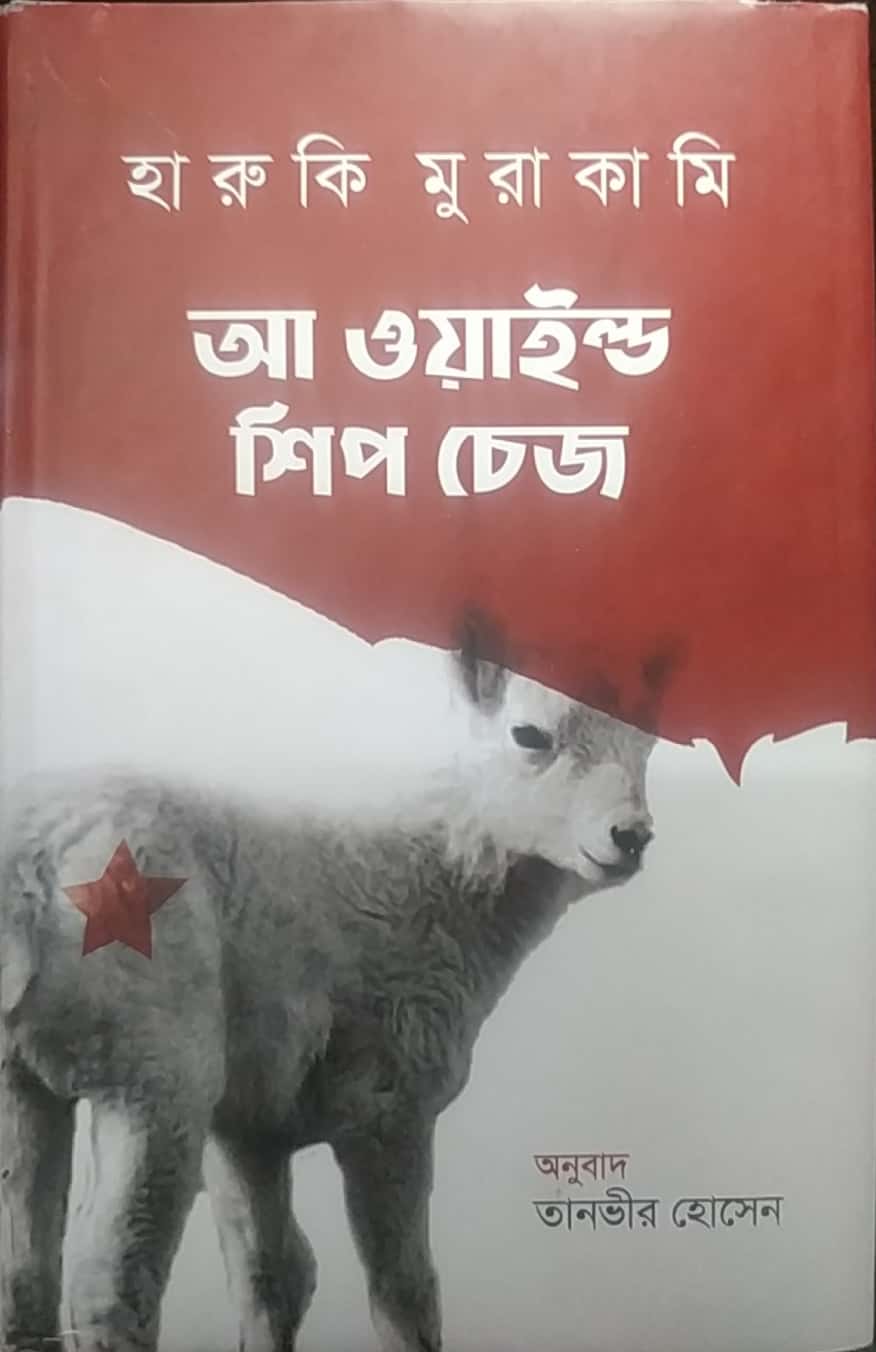
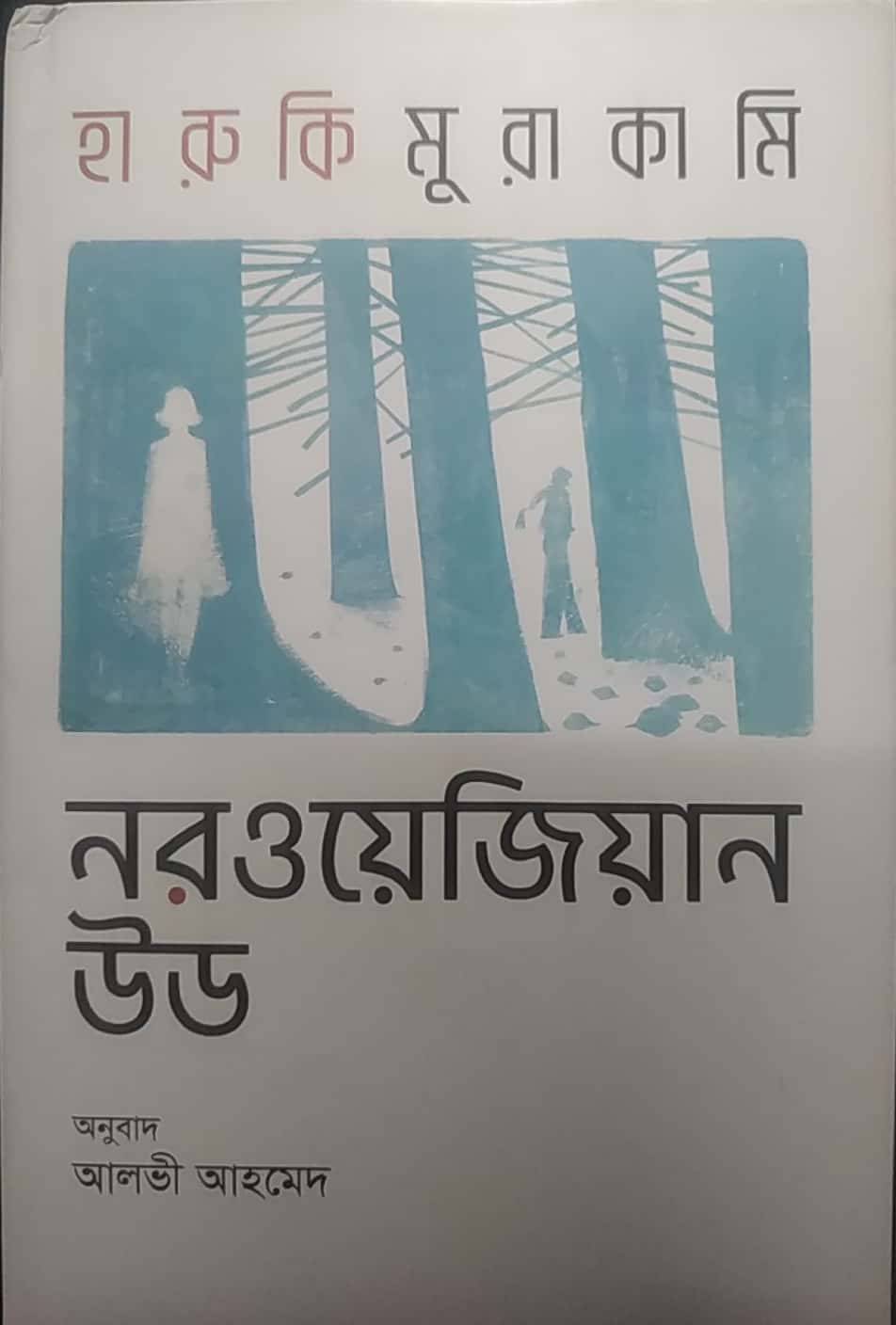
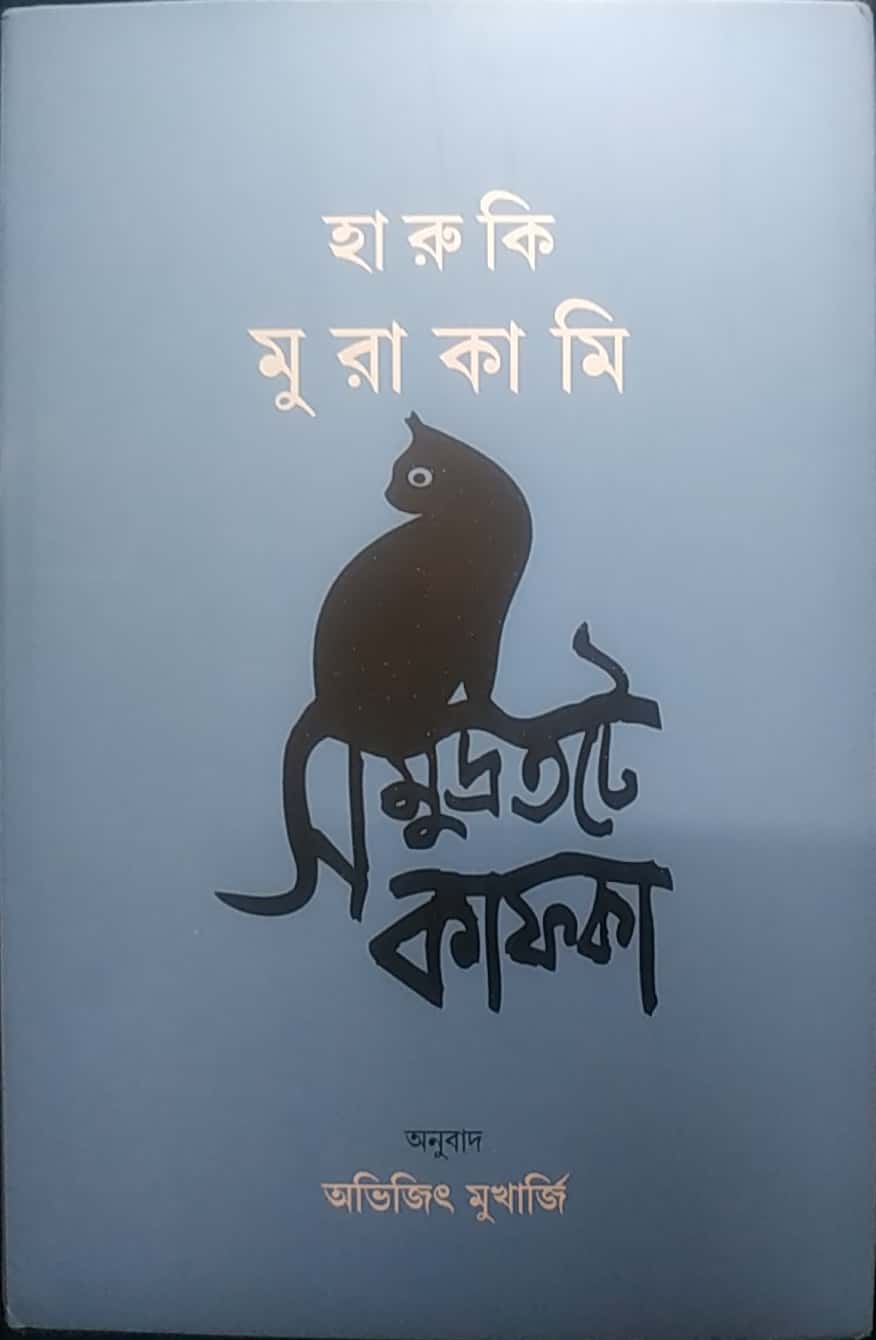
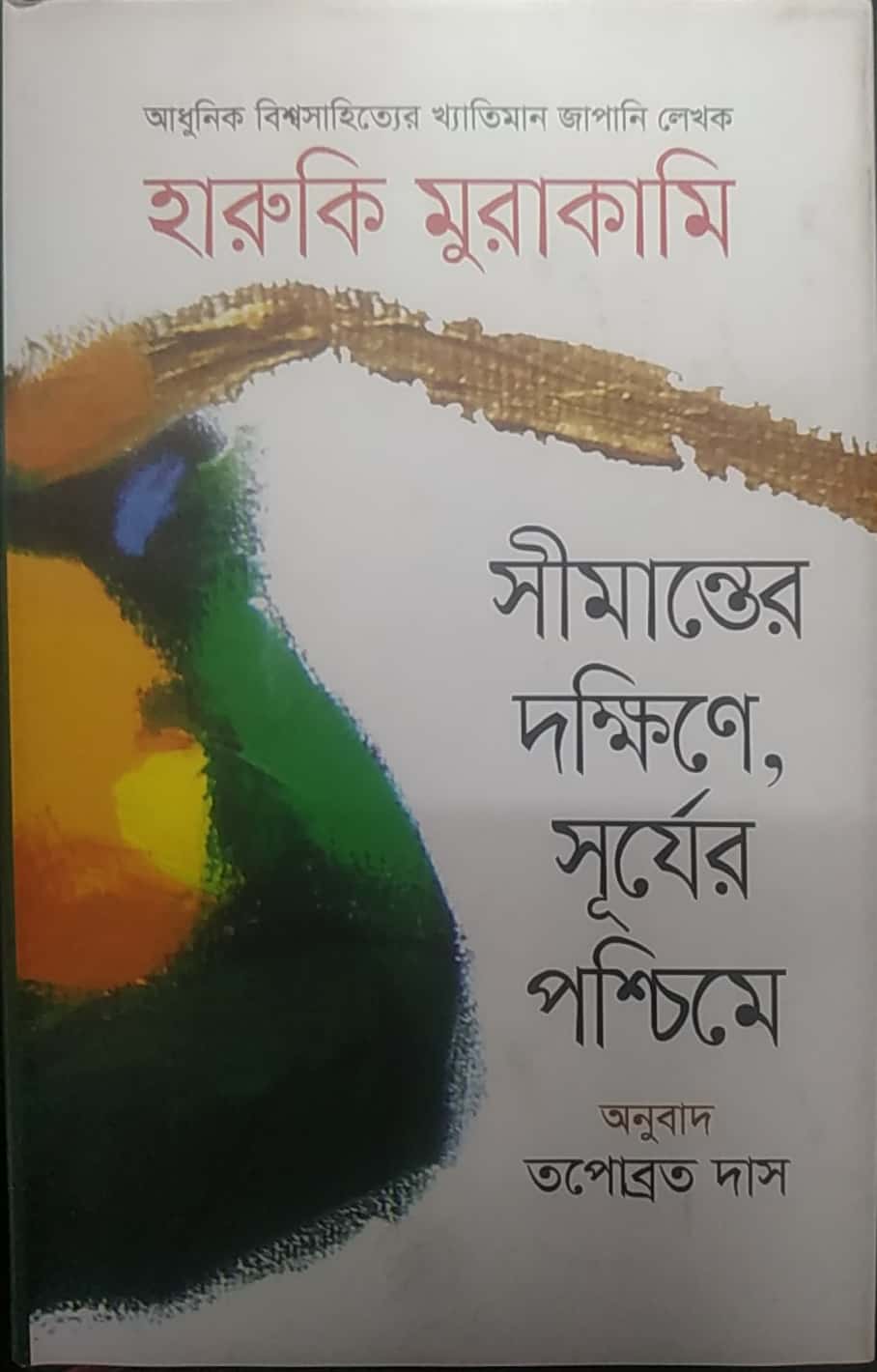
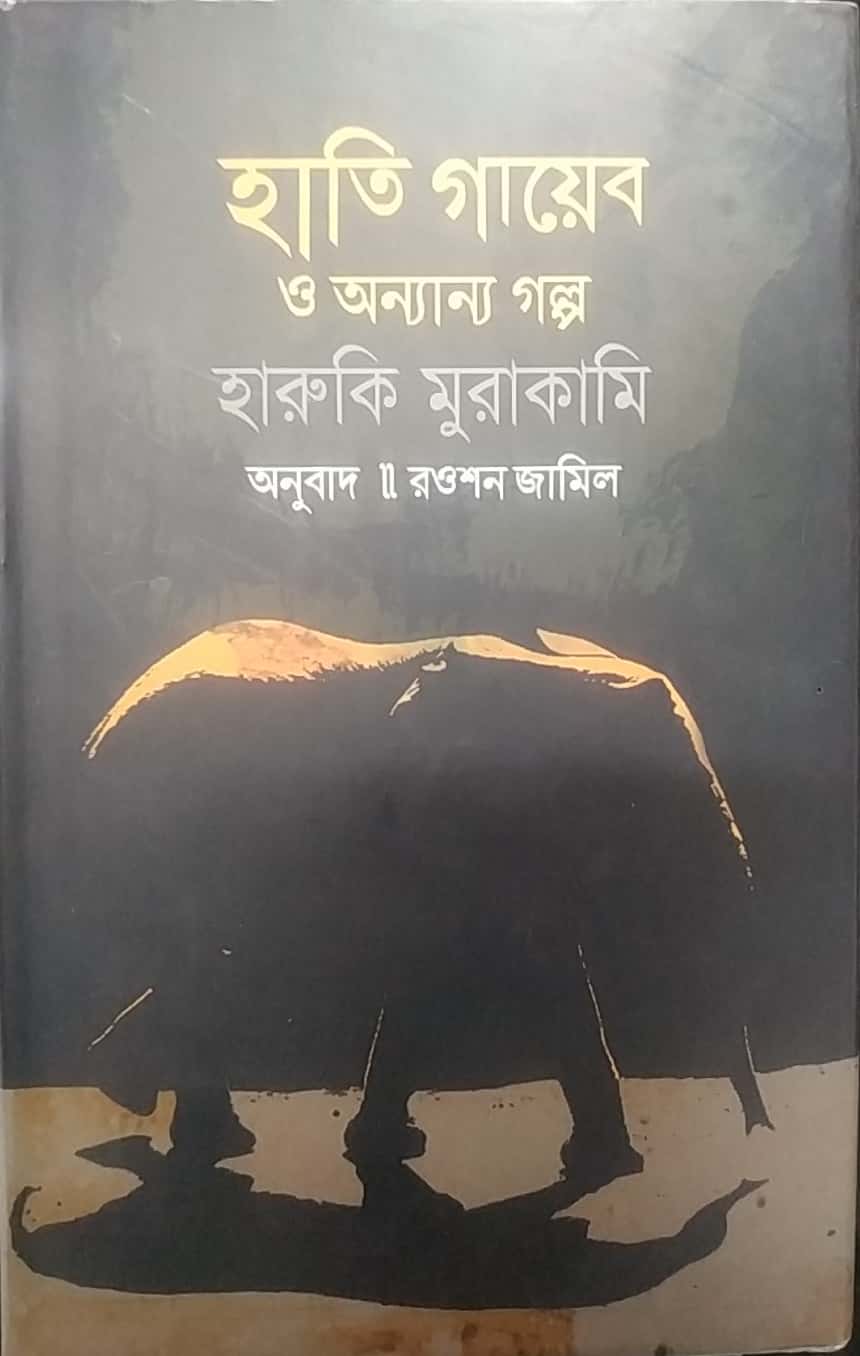
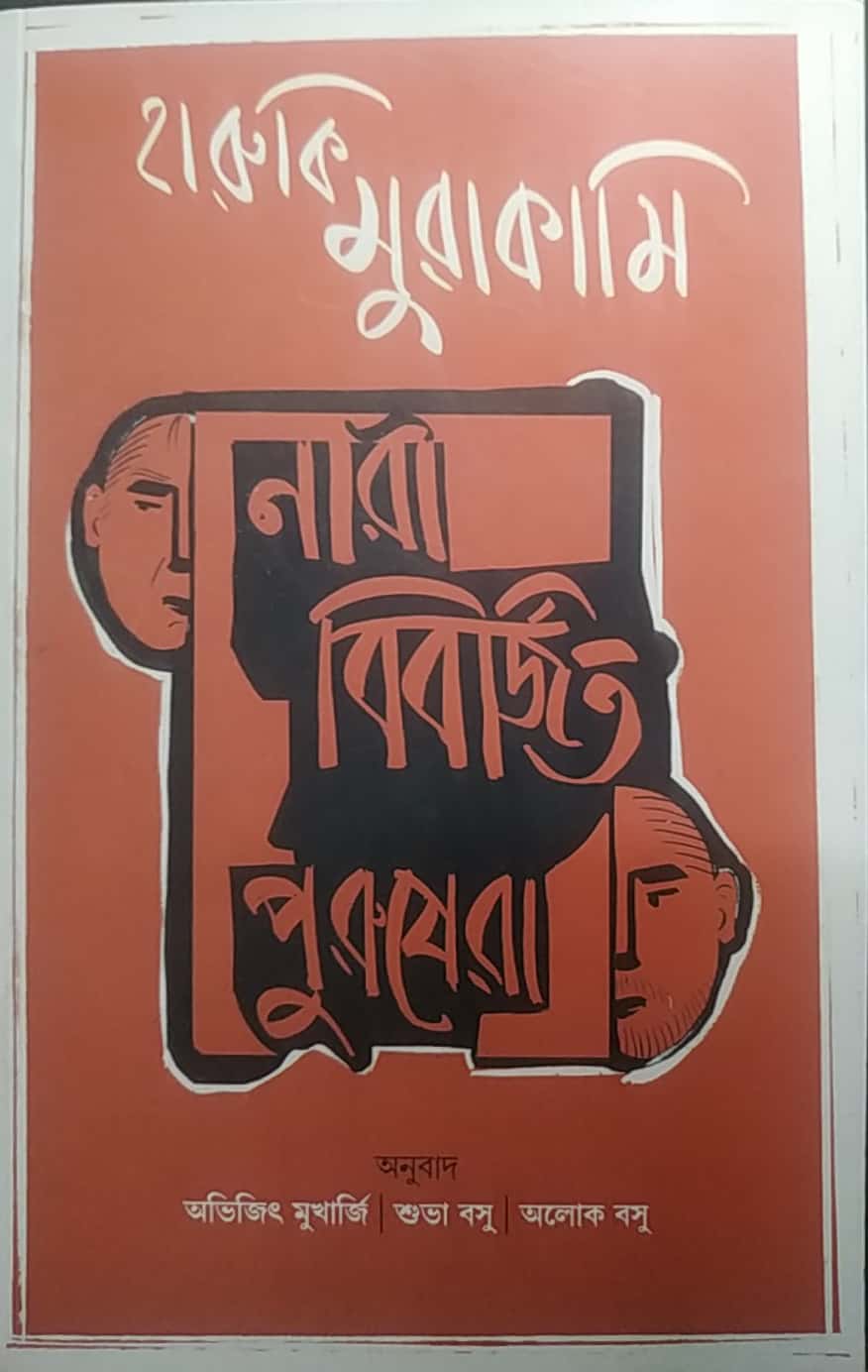
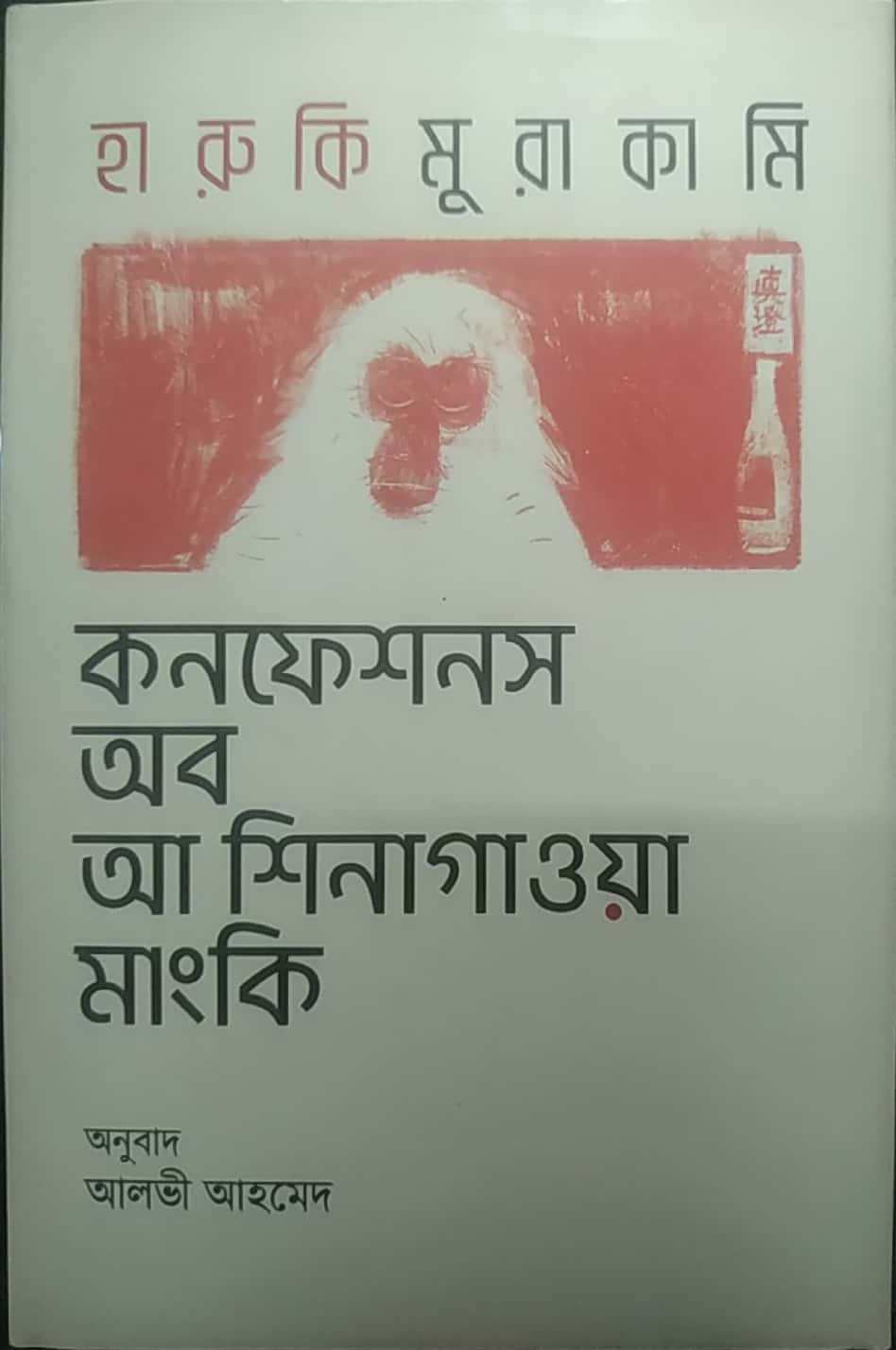
আমাদের বর্তমান লেখার বিষয়বস্তু মুরাকামির প্রথম উপন্যাস – “হিয়ার দ্য উইন্ড সিং”। এই উপন্যাসটির একাধিক বাংলা অনুবাদ হয়েছে। আলভী আহমেদ একটি অনুবাদ করেছেন। বাংলাদেশের বাতিঘর প্রকাশনী থেকে সেটি প্রকাশিত হয়েছে। আলভী এই অনুবাদ করেছেন টেড গুসন এই বইয়ের যে ইংরাজী তরজমা করেছিলেন, সেটিকে ভিত্তি করে। গুসনের ইংরাজী অনুবাদটির প্রকাশক ছিল পেঙ্গুইন। আলভীর অনুবাদটি ছাড়াও "হিয়ার দ্য উইন্ড সিং" এর আরো একটি বাংলা অনুবাদ হয়েছে। সেটি করেছেন জিয়া হাসান। জিয়ার অনুবাদটির প্রকাশক বাংলাদেশের ঐতিহ্য প্রকাশন সংস্থা।
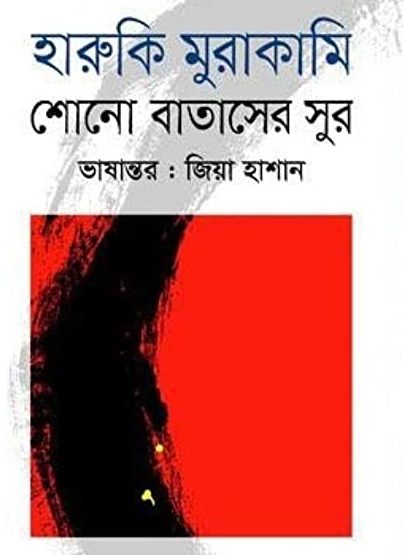
উপন্যাসটি নিয়ে কথা বলার আগে আমরা মুরাকামির জীবনের কিছু গল্পের কথায় আসি প্রথমে। "দ্য বার্থ অব মাই কিচেন টেবিল ফিকশন" নামের লেখাটিতে নিজের জীবনের গল্প শোনাতে গিয়ে মুরাকামি লিখছেন -
“জাপানের বেশিরভাগ লোকের জীবনধারনের একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন আছে। তারা প্রথমে গ্রাজুয়েশন শেষ করে। তারপর কোনও একটা কাজ খুঁজে নেয়। চাকরিবাকরি করে। এভাবে বেশ কিছুদিন কাটানোর পর বিয়ে করে সংসার শুরু করে। থিতু হয়। আমিও এই প্যাটার্ন অনুসরণ করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু বাস্তবে ব্যাপারটা একটু বদলে গেল।
আমি একদিন দুম করে বিয়ে করে ফেললাম। তারপর চাকরি নিলাম। এবং তারপর গ্রাজুয়েশন শেষ করলাম। অর্থাৎ নিচ থেকে ওপরে না উঠে সিঁড়ির তিনধাপ ওপর থেকে নিচে নামলাম।
চাকরিবাকরি আমার কোনওদিনই তেমন পছন্দের ছিল না। তাই অচিরেই চাকরিটা ছেড়ে দেবার ইচ্ছে জাগল মনে। কিন্তু ছেড়ে দিলে রোজগারপাতির কি দাঁড়াবে ? চলবে কি করে ? ভাবলাম স্বাধীনভাবে একটা ব্যবসা করব।
কী ধরনের ব্যবসা করা যেতে পারে সেটা ভাবতে থাকলাম। আমার ইচ্ছে ছিল একটা কফিশপ চালু করার। এমন একটা কফিশপ যেখানে মানুষজন জ্যাজ মিউজিক শুনতে আসবে। মিউজিক শুনবে, সেইসঙ্গে কফি, স্ন্যাক্স, নানারকম ড্রিংকস খাবে। কফিশপ কাম বার টাইপের একটা ব্যাপার। ... ভেবেছিলাম আর কিছু না হোক এরকম একটা ব্যবসা হলে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পছন্দের মিউজিক অন্তত শুনতে পারব আমি।
সমস্যা হল ব্যবসা করতে মূলধন লাগে। সেটা তো নেই। না আমার কাছে, না আমার স্ত্রীর কাছে কোনও জমানো টাকা পয়সা ছিল।
মূলধন জোগাড়ের জন্য তিন তিনটে বছর আমরা গাধার মতোই প্রচণ্ড পরিশ্রম করলাম। একসঙ্গে একাধিক চাকরিও করলাম। এতে কিছুটা টাকা জমল। এরপর যাকে সামনে পেলাম তার থেকেই টাকা ধার করতে শুরু করলাম। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কেউই বাকি রইলো না। ব্যাংক থেকেও একটা ছোটখাটো লোন পেয়ে গেলাম। সব টাকা এক করে আমরা টোকিওর পশ্চিমদিকের শহরতলি কোকুবুনজিতে একটা ছোটো কফিশপ কম বার খুললাম।”
জাপানে তরুণদের মধ্যে তখন এই ধরনের স্বাধীন ব্যবসার দিকে বেশ ঝোঁক এসেছিল। মুরাকামি ঐ লেখাটিতেই এই প্রসঙ্গে বলছেন, "জায়গাটাকে আমরা একটা স্টুডেন্ট হ্যাঙ আউটের আদল দিতে চেয়েছিলাম। সেটা ১৯৭৪ সালের ঘটনা।
এখন যেমন একটা ব্যবসা করতে অনেক টাকাপয়সার প্রয়োজন হয়, সে আমলে ততটা প্রয়োজন পড়ত না। আমাদের মতো তরুণ যারা চাকরি করবে না বলে ঠিক করেছে, তারা শহরের অলিতে গলিতে এই ধরনের ছোটখাটো ব্যবসা শুরু করেছিল। ক্যাফে, রেস্টুরেন্ট থেকে বইয়ের দোকান, স্টেশনারি শপ - সব ধরনের ব্যবসার উদ্যোগই ছিল।"
মুরাকামির দ্বিতীয় উপন্যাস "পিনবল ১৯৭৩" যাঁরা পড়েছেন তাঁরা জানেন সেখানে জাপানের সে সময়ের ছাত্র আন্দোলন সম্পর্কে অনেক কথা আছে। 'বার্থ অব মাই কিচেন টেবিল ফিকশন' লেখাটিতে মুরাকামি সেই প্রসঙ্গে লিখছেন, "কোকুবুনজির আকাশে বাতাসে তখন একধরনের প্রতিবাদী প্রতিবাদী সাংস্কৃতিক আবহ ছিল। কফিশপের আশেপাশে বেশকিছু কলেজ আর ইউনিভার্সিটি। ছেলেমেয়েরা দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। কফি খেতে আসে, আড্ডা দেয়। আমরা যারা ঐ এলাকায় এ রকম স্বাধীন ব্যবসা শুরু করেছিলাম, তাদের অনেকেই ছিলাম কয়েক বছর ধরে চলতে থাকা ছাত্র আন্দোলনের সক্রিয় নেতা কর্মী।"
মুরাকামি তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কফিশপ কাম বার চালিয়ে বেশ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছিলেন।
"বড় আনন্দ নিয়ে বেঁচে ছিলাম। বয়েসটা আমাদের পক্ষে ছিল। সবচেয়ে বড় কথা সারাদিন আমরা আমাদের পছন্দের গান শুনতে পারতাম। নিজের রাজ্যে আমি নিজেই ছিলাম রাজা। সকালে ঘুম থেকে উঠে ট্রেনের জন্য দৌড়ই না। দিনে তিন চারটে বিরক্তিকর মিটিং অ্যাটেন্ড করতে হয় না। বসের সামনে মাথা নিচু করে দাঁড়াতে হয় না। ভিড়ের বাসে মানুষের ঘামের গন্ধ শুঁকে রোজ যাতায়াত করতে হয় না। নিজের রেস্টুরেন্টে কাজ করি, মিউজিক শুনি আর মানুষ দেখি।"
তখনো লেখালিখি করার কোনও ভাবনাই তাঁর মাথায় আসে নি। সেটা এলো একদিন অকস্মাৎই। ১৯৭৮ সালের ১ এপ্রিল একটি বেসবল খেলা দেখতে দেখতে “শোনো বাতাসের সুর” উপন্যাসটির ভাবনা হঠাৎ করেই তাঁর মাথায় আসে।
"দিনটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাসের এক বিকেল। রৌদ্রজ্জ্বল একটা দিন। জিঙ্গু স্টেডিয়ামে বেসবল খেলা দেখতে গিয়েছিলাম। আমার জ্যাজ ক্লাব থেকে দশ মিনিটের হাঁটাপথ মাঠটা। সেন্ট্রাল লিগের খেলা ছিল সেদিন। মরসুমের প্রথম ম্যাচ। খেলবে ইয়াকুল্ট সোয়ালো আর হিরোসিমা কার্প নামে দুটো দল।
আমি তখন ইয়াকুল্ট সোয়েলোর প্রবল সমর্থক। যে সময়টার কথা বলছি তখন হিরোসিমা কার্প বড় দল হলেও সোয়ালো খুবই দুর্বল একটা দল ছিল দলের টাকাপয়সা তেমন ছিল না। তাই খুব নামী খেলোয়াড় নিতে পারত না৷ এ কারণে ততটা জনপ্রিয় ছিল না৷ তাদের খেলাগুলোতে মাঠ মোটামুটি ফাঁকাই থাকত। সে সময় বিকেলে হাঁটাহাঁটির বদলে আমি প্রায়ই মাঠে খেলা দেখতে চলে যেতাম।
তখন মাঠটায় দর্শকদের খেলা দেখার কোনও সিট ছিল না। একটা ঘাসে ঢাকা ঢাল ছিল। সেখানে বসেই আরাম করে লোকজন খেলা দেখত। বিয়ার খেতে খেতে খেলা দেখার সে ছিল এক চমৎকার ব্যবস্থা।
আকাশে সেদিন এক ফোঁটা মেঘ ছিল না। মৃদু হাওয়া বইছিল। হাতে ধরা বিয়ারটা ছিল বেশ ঠান্ডা।
সোয়ালোর হয়ে ওপেনিং ব্যাটার ছিল ডেভ হিলটন নামে এক আমেরিকান খেলোয়াড়। সে বছরই সে দলে যোগ দিয়েছিল। হিলটন ঠিক মাঝ ব্যটে একটা ভালো হিট করে। ব্যাটের ঠিক মাঝখানে বল লাগলে যেমন শব্দ হয়, সে রকম একটা শব্দ পুরো স্টেডিয়ামে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে।
এবং সেই মুহূর্তে আমার মনে হয়, আমি একটা উপন্যাস লিখতে পারব। সেই উড়ে আসা ভাবনাটাকে ক্যাচের মতো শক্ত হাতে আমি মুঠোবন্দী করি। মুহূর্তটাকে স্বর্গীয় কিছু বলে মনে হয় আমার। আমার জীবনটা মুহূর্তে বদলে যায়।
খেলা শেষে আমি ট্রেনে করে শিঞ্জকু স্টেশনে যাই এবং সেখান থেকে কিছু লেখালিখির কাগজ আর একটা সেইলর ফাউন্টেন পেন কিনে ফেলি। সে যুগে এখনকার মতো ওয়ার্ড প্রসেসর বা কম্পিউটার ছিল না। যা কিছু লেখার সেগুলো কাগজ কলমে লিখতে হত।
সে রাতেই লেখা শুরু করি। অনেক বছর পর সেই রাতে আমি ফাউন্টেন পেন হাতে নিই।"
কফিশপের ব্যবসা সেরে বাড়ি ফিরে তিনি রোজ একঘন্টা করে লিখতে থাকেন এবং ছ মাস ধরে একটানা লিখে এই উপন্যাসটি শেষ করেন।
'হিয়ার দ্য উইন্ড সিং' উপন্যাসটি আকারে তেমন বড় নয়। চল্লিশটা ছোট ছোট অনুচ্ছেদ মিলিয়ে ১৩০ পাতার একটা পকেট বই। ১৯৭৯ সালের জুন মাসে জাপানের বিখ্যাত সাহিত্য পত্রিকা গুনজোতে এটি প্রথম প্রকাশিত হয়। পরের মাসেই এটি বই হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বইটি যথেষ্ট সাড়া ফেলেছিল। বইটি নিয়ে একটি চলচ্চিত্রও তৈরি হয়। ১৯৮১ সালে সেটি তৈরি করেন জাপানি পরিচালক কিজুরি ওমোরি।
মজার ব্যাপার হল মুরাকামির নানা লেখা যখন ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে এবং সারা বিশ্বেই তাঁর বইয়ের চাহিদা তুঙ্গে, তখনো তিনি দীর্ঘদিন তাঁর লেখা প্রথম উপন্যাস দুটি - 'হিয়ার দ্য উইন্ড সিং' ও 'পিনবল ১৯৭৩' কে ইংরাজীতে অনুবাদ করার অনুমতি দেন নি। অবশেষে ১৯৮৭ সালে এই অনুমতি দিলেন মুরাকামি। 'হিয়ার দ্য উইন্ড সিং' কে জাপানী থেকে ইংরাজীতে প্রথম ভাষান্তরিত করলেন আলফ্রেড ব্রিনব্যুম। পরে টেড গুসন উপন্যাসটির আরেকটি স্বতন্ত্র তরজমা করেন।
এই প্রসঙ্গে একটা কম জানা, খানিক মজার ও আশ্চর্যের কথা বলা দরকার। 'হিয়ার দ্য উইন্ড সিং' উপন্যাসটি মুরাকামি প্রথমে জাপানিতে লিখতে শুরু করেন। কিন্তু লেখার পর তাঁর মনে হতে থাকে উপন্যাসের আঙ্গিক এবং কাঠামো ঠিক থাকলেও সেটা পড়তে বেশ বিরক্তিকর লাগছে। এই উপলব্ধি তাঁর ভেতরটাকে একেবারে ঠান্ডা করে দিল। তিনি ভাবলেন একজন লেখকের নিজেরই যদি নিজের লেখা পড়ে মজা না আসে, পাঠকের কী দায় আছে সেটা পড়ার।
এতদিন ধরে যে পান্ডুলিপিটা মুরাকামি লিখেছিলেন সেইটে তিনি ছুঁড়ে ফেলে দেন। ফাউন্টেন পেন তুলে রেখে লিখতে শুরু করেন তাঁর পুরনো অলিভেটি টাইপরাইটারটা দিয়ে।
আর আশ্চর্য করার মতো ব্যাপার হলো এই যে জাপানির বদলে তিনি লিখতে শুরু করলেন ইংরাজীতে।
মুরাকামি নিজেই বলেছেন যে তিনি খুব ভালো ইংরাজী জানতেন না। তাঁর ইংরাজী শব্দসম্ভার ছিল বেশ সীমিত। সমস্যা ছিল বাক্যরীতি নিয়েও। এই অসুবিধেগুলোই এই উপন্যাসের পরিকল্পনার জন্য যেন মহাসুবিধেজনক হয়ে উঠল। এই গল্পটার জন্য দরকার ছিল সহজ করে গল্পটা বলা। সীমিত শব্দভাণ্ডার ও বাকরীতির সীমাবদ্ধতা নিয়ে ইংরাজীতে লেখার কারণে সেটা সম্ভবপর হল। জটিল জাপানী বাক্যরীতির বদলে এইবার তিনি বাধ্য হয়েই ছোট ছোট ইংরাজী বাক্যে লেখাটা লিখতে থাকলেন। এমন কোনও শব্দ লিখলেন না যার মানে দেখতে অভিধান ঘাঁততে হয়। বেশ সরল এক গদ্যভাষা তৈরি করে নিতে পারলেন মুরাকামি। এইবার তাঁর মনে হল নিজস্ব গদ্যভাষাটিকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন।
ইংরাজীতে টাইপরাইটারে উপন্যাসটি লিখে ফেলার পর তিনি টাইপরাইটারটা আবার বাক্সবন্দী করে রেখে দেন। আবার হাতে তুলে নেন ফাউন্টেন পেন। এইবার নিজের ইংরাজী লেখাটাই তিনি জাপানী ভাষায় অনুবাদ করতে শুরু করেন। তিনি এই কাজটাকে ট্রানস্লেশন এর বদলে বলেছেন ট্রান্সপ্লান্টেশন।
লেখার পাণ্ডুলিপিটা জাপানের বিখ্যাত পত্রিকা গুঞ্জোর একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্য তিনি পাঠিয়ে দেন। তারপর এটার কথা প্রায় ভুলেই যান। অনেকদিন পর গুঞ্জোর সম্পাদকের কাছ থেকে মুরাকামি একটি ফোন পান। তাঁকে জানানো নয় এই উপন্যাসটি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে এবং এটি ছাপা হচ্ছে। মুরাকামি বলেছেন এই পাণ্ডুলিপির কোনও প্রতিলিপিও তিনি নিজের কাছে রাখেন নি। যদি উপন্যাসটা পুরস্কার না পেত, পাণ্ডুলিপিটি হয়ত হারিয়েই যেত চিরতরে আর কোনও উপন্যাস লেখার কথাও হয়ত মুরাকামি কখনো ভাবতেন না।

১৯৭০ সালের অগস্ট মাসের কয়েকটা দিনের কাহিনী রয়েছে এই উপন্যাসটিতে। কাহিনীর শুরু ১৯৭০ সালের ৮ অগস্ট, যখন অনামা কথক গ্রীষ্মাবকাশে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাড়ি ফিরেছে।
এই গল্পের শুরু ১৯৭০ সালের ৮ অগস্ট। তখন আমি টোকিওতে একটা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি। ওখানকার ডর্মিটরিতে থাকি। গরমের ছুটিতে আমার জন্মশহরে ফিরে এসেছিলাম। সেই বন্দর শহরের কাহিনী এটি। মোটামুটি আঠারো দিনের একটা ঘটনা বলে ধরা যেতে পারে। সেই হিসেবে অগস্টের ২৬ তারিখে গিয়ে গল্পটা শেষ হয়ে যাবে।
২৬ অগস্টে গিয়ে কাহিনী শেষ হয়, যখন অনামা কথক গ্রীষ্মাবকাশ শেষে আবার ফিরে যাচ্ছে তার বিশ্ববিদ্যালয়ে। কাহিনী বলতে অবশ্য একটানা কোনও আখ্যান এখানে নেই। ছেঁড়া ছেঁড়া কিছু স্মৃতিকথা, কিছু অনুভূতি, কিছু পর্যবেক্ষণ। উপন্যাসের কথকের কোনও নাম নেই এখানে। তার সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানাও যায় না। গরমের ছুটির অবকাশে সে কয়েকদিনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরেছে তার বাড়িতে। সেখানে ফিরে এক স্থানীয় পাবে যায় সে, মদ খেয়েই কাটিয়ে দেয় বেশিরভাগ সময়টা। অনামা কথকের বয়স মুরাকামির নিজের বয়সের সমান। ১৯৪৮ এর ২৪ ডিসেম্বর এই অনামা কথকের জন্ম আর মুরাকামির নিজের জন্মদিন ১২ জানুয়ারী ১৯৪৯ এ।
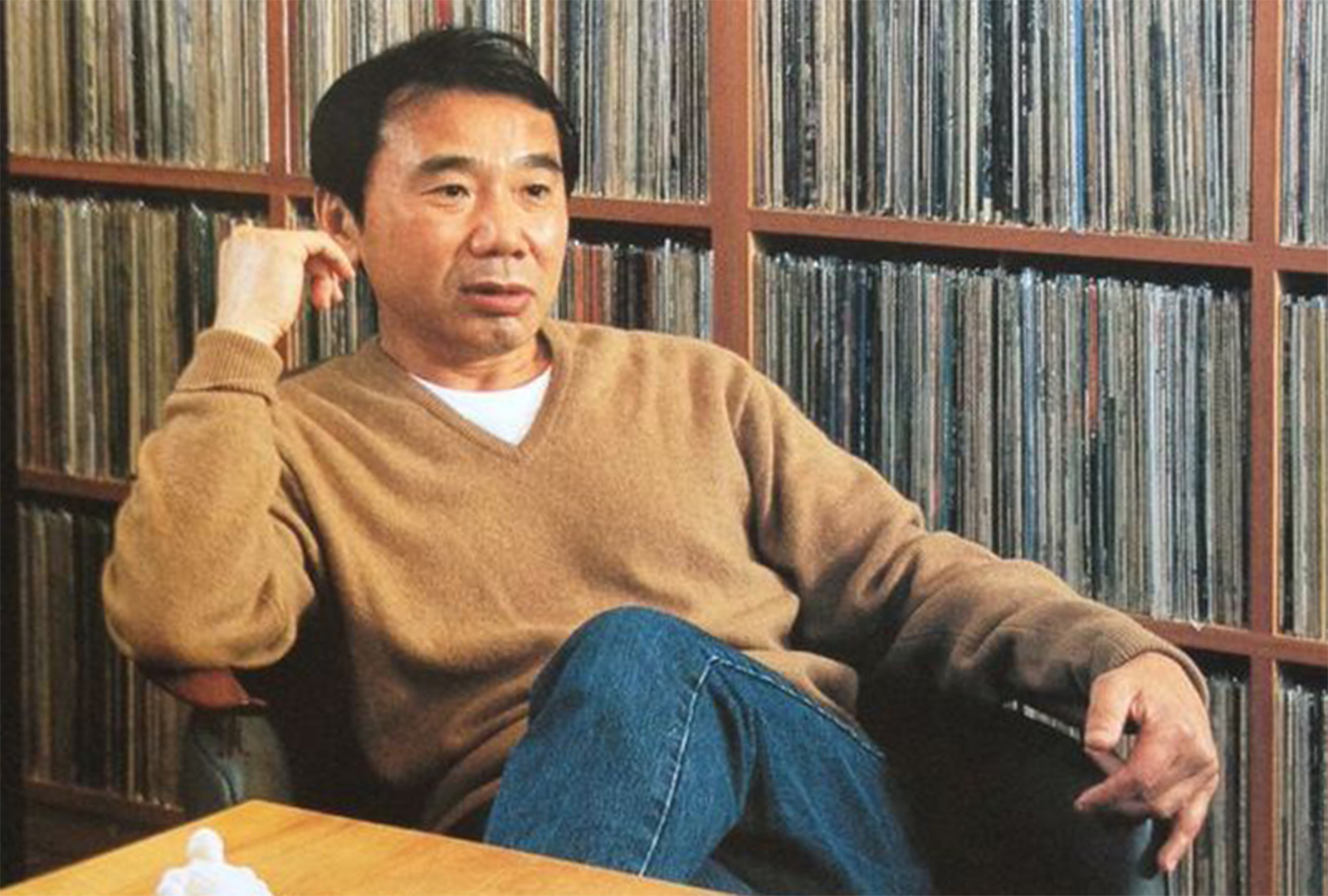
এই উপন্যাসের কথকের কোনও নামকরণ মুরাকামি করেন নি। সেই অনামা কথকের মদ্যপানের সঙ্গী র্যাট বলে একজন। সে তিনতলা এক বাড়িতে থাকে, বেশ বড়লোক বাবার ছেলে। তা সত্ত্বেও সে বড়লোকদের কোনও এক কারণে তীব্র অপছন্দ করে, তাদের নিয়মিত গালাগালি করে থাকে। – “বড়লোকদের প্রতি র্যাটের মুখ খারাপ করা এটাই প্রথম নয়। আগেও বহুবার করেছে। তাতেই বোঝা যায়, আসলেই সে বড়লোকদের ঘৃণা করে। অথচ তার নিজের পরিবার মোটামুটি বড়লোকই। আমি তাকে তা স্মরণ করিয়ে দিলে জবাবও তার, ‘এ জন্য তো আমি দায়ী নই।”
কেন র্যাট বড়লোকদের ঘৃণা করে সেই প্রসঙ্গে অনামা কথককে র্যাটের বলা কথাগুলো উদ্ধৃত করা যাক।
শোনো আমি কেন বড়লোকেদের ঘৃণা করি। ওদের মধ্যে কল্পনাশক্তি নেই। নিজে নিজে কারো সাহায্য ছাড়া কোনওকিছু করবে, সে রকম বোধবুদ্ধি ওদের নেই।... তাদের যেটুকু মেধা বরাদ্দ ছিল তা তারা বড়লোক হতে গিয়ে খরচ করে ফেলেছে। বড়লোক হওয়ার জন্য সামান্য কিছু মেধা দরকার হয় বই কি, তবে সেই সম্পত্তি ধরে রাখার জন্য কোনও মেধার দরকার হয় না। একটা স্যাটেলাইট মহাকাশে পাঠাতে জ্বালানির দরকার হয়। কিন্তু একবার পাঠিয়ে দেবার পর সেটা কোনও প্রকার জ্বালানি ছাড়াই কক্ষপথে ঘুরপাক খেতে থাকে। এটাও সেরকম একটা ব্যাপার।
র্যাটের সঙ্গে অনামা কথকের আলাপ ও প্রথমদিনের অভিজ্ঞতা ছিল অতি চমকপ্রদ। -
'বছর তিনেক আগে এক বসন্তকালে র্যাটের সাথে আমার পরিচয় হয়। সে বছরেই আমরা প্রথম কলেজে ঢুকেছিলাম। পরিচয়ের প্রথম দিনেই আমরা বেশ বড় রকমের একটা দুর্ঘটনার শিকার হই। মৃত্যুকে চোখের খুব কাছ থেকে দেখে তার রূপ, রস, স্বাদ, গন্ধ নিয়ে জীবনে ফেরৎ আসি।
আমি কোনোভাবেই মনে করতে পারি না, আমাদের কী করে প্রথমবার দেখা হয়েছিল। আবার এটাও মনে নেই কী করে আমি তার কালো চকচকে ফিয়াট গাড়িটাতে উঠেছিলাম। সম্ভবত আমাদের দুজনের কোনও মিউচুয়াল ফ্রেন্ড ছিল। যার মাধ্যমে আমাদের পরিচয়।
সে যাই হোক পরিচয়ের রাতে ভোর চারটের দিকে গলা পর্যন্ত মদ টেনে আমি র্যাটের সাথে তার ফিয়াট গাড়িতে চড়ে বসলাম। র্যাট গাড়িটা ঘন্টায় আশি কিলোমিটার বেগে চালাতে শুরু করল। একসময় আমরা নিজেদের মিউসিপ্যালিটির সাজানো গোছানো একটা পার্কের মধ্যে আবিষ্কার করলাম। সিনেমায় যে রকম হয়, সে রকম হয়েছিল ব্যাপারটা। বড় রাস্তা থেকে গাড়িটা প্রায় উড়ে গিয়ে পার্কের দেওয়াল ভেঙে সোজা ভেতরে ঢুকে যায়। ... ধাক্কা খাওয়ার পর আমার মোটামুটি হুঁশ ফিরে এল। অবাক হয়ে দেখলাম আমাদের গায়ে একটুও আঘাত লাগে নি।
গাড়ির ভাঙা দরজাটা লাথি মেরে সরিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলাম।
র্যাট তখনো গাড়ির ভেতরে। আমি হামাগুড়ি দিয়ে ওর কাছে গেলাম। গাড়ির ভেতরটা একটু দেখার চেষ্টা করলাম। র্যাটের হাত তখনো স্টিয়ারিং হুইলে। ...
তুমি ঠিক আছ ? জিজ্ঞেস করলাম তাকে। ... তুমি কি বের হয়ে আসতে পারবে ?
দেখি হাতটা বাড়াও তো। আমাকে একটু টেনে তোল।
র্যাট গাড়ির ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল। তারপর ড্যাশবোর্ড থেকে সিগারেটের প্যাকেটটা নিয়ে আমার হাত ধরে গাড়ির ছাদে উঠল।
আমরা গাড়ির ছাদে পাশাপাশি বসলাম এবং একটার পর একটা সিগারেট ধ্বংস করলাম।
কয়েক মিনিট যাওয়ার পর র্যাট বলল - আমরা আসলে খুবই ভাগ্যবান। বড় বাঁচা বেঁচে গেছি। মরেও যেতে পারতাম।'
মুরাকামির 'হিয়ার দ্য উইন্ড সিং' বা 'শোনো বাতাসের সুর' উপন্যাসটির একটি বড় অবলম্বন লেখালিখি সম্পর্কে কথাবার্তা।
অনামা কথক লেখালিখি নিয়ে ভাবে। কিন্তু যে বন্ধুর সঙ্গে বারে বসে সে অনেক সময় কাটায়, বিয়ার খায় সেই র্যাটকে সে কখনো বই পড়তে দেখে নি৷
বইয়ের জগতে তার ঘোরাফেরাটা অনেকটা ভার্চুয়াল প্রেমিকের মতো। প্রেমিকার সাথে দেখা হয় না বটে, কিন্তু একধরনের ভালোবাসা তাদের মধ্যে আছে। পত্রিকার খেলার পাতা বা বাতিল কিছু জাঙ্ক মেইল ছাড়া তেমন কিছুই পড়ে না র্যাট। তারপরও আমায় যখন বই পড়তে দেখে তখন একধরনের কৌতূহল নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থাকে। মাছি যেমন আগ্রহ নিয়ে মাছি মারার ফাঁদের দিকে তাকায়, তার কৌতুহলী দৃষ্টি অনেকটা সেরকম।
তবুও অনামা কথক র্যাটের সঙ্গে বইপত্র নিয়ে কথা বলতে আগ্রহী। সে র্যাটের কাছে জানতে চায় তার পড়া বই সম্পর্কে। র্যাট তার পড়া শেষ বইটির কথা অনামা কথককে জানায়। যে বইটা সে পড়েছিল গত বছর।
র্যাট বলে -
বইটার নাম আমার মনে নেই। লেখক কে সেটাও মনে নেই। কী কারণে বইটা পড়েছিলাম সেটাও এখন আর মনে করতে পারছি না। তবে এটুকু মনে আছে বইটা লিখেছিলেন একজন মহিলা। বইয়ের প্রধান চরিত্রও ছিল এক নারী। সে মহিলা ভাবতে ভালোবাসত যে তার ক্যান্সার বা এরকম কোনও দুরারোগ্য ব্যধি আছে। সে যে কোনও মুহূর্তে মরে যেতে পারে।
সেই মহিলা খুবই অদ্ভুত ধরনের৷ উপন্যাসজুড়ে তার মূল কাজ মাস্টারবেট করা। সে এক সমুদ্র তীরবর্তী রিসোর্টে বেড়াতে যায়। সে রিসোর্টের বাথরুমে, নিজের বিছানায়, বনে জঙ্গলে, পাহাড় পর্বতে, সমুদ্রে সব জায়গায় মাস্টারবেট করে।
এই ধরনের উপন্যাস লেখার কি কোনও দরকার আছে? পৃথিবীতে লেখার বিষয়ের কি এতই অভাব পড়ে গেছে?
র্যাট জানায় সে যদি কখনো উপন্যাস লেখে একেবারে অন্যভাবে লিখবে। কেমন হবে সেই উপন্যাস ?
আমার উপন্যাসের কেন্দ্রে প্রশান্ত মহাসাগর। সেই প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যে একটা জাহাজ ডুবে গেছে। আমি সেই জাহাজের যাত্রী। কোনও রকমে লাইফ জ্যাকেটের মতো একটা কিছু জোগাড় করে জলের ওপর ভাসছি। লাইফ জ্যাকেটের বদলে একটা কাঠের টুকরো ধরেও ভাসতে পারি। মোট কথা বেঁচে আছি এবং বাঁচার চেষ্টা করে যাচ্ছি। আমার দৃষ্টি আকাশের দিকে। তখন গভীর রাত। হুট করে আমি দেখি যে একটা মেয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে আমার দিকে আসছে। তার পরনেও একতা লাইফ জ্যাকেট। ...
মেয়েটা সাঁতার কাটতে কাটতে আমার কাছে এল। আর তখন তার সাথে আমি গল্প জুড়ে দিলাম। ... আমি মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা করলাম এখন তুমি কী করবে ? সে বলল - আমার ধারণা ওই দূরে কোনও একতা দ্বীপ আছে। আমি সেদিকে সাঁতরে চলে যাব।
আমি বললাম দূরে সম্ভবত কোনও দ্বীপ নেই। তার চেয়ে এসো আমরা এখানে কোনওমতে ভেসে থাকি আর বিয়ার খাই। কোনও উদ্ধারকারী এরোপ্লেন নিশ্চয় আসবে আর আমাদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। ততক্ষণ পর্যন্ত ভেসে থাকতে পারলেই হল। কিন্তু মেয়েটা আমার কথা শুনল না। সে একা একা সাঁতার কাটতে কাটতে অনেক দূরে চলে গেল।
র্যাট পরে সত্যিই একজন ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠে। উপন্যাস লেখা শুরু করার আগে তার মন মেজাজ বেশ খারাপ ছিল। অনামা কথক ছাড়াও বারের মালিক জে-র বিষয়টা নজরে এসেছিল। কথকের সঙ্গে এই নিয়ে সে কথাও বলে। প্রিয় বন্ধু হিসেবে কথককেই অনুরোধ করে র্যাটের মনের গভীরের দুঃখগুলোকে বের করে আনার জন্য তার সঙ্গে কথা বলতে। কথকের মনে হয়েছিল, একটি মেয়ে যার সঙ্গে র্যাট তার আলাপ করিয়ে দেবে বলেছিল, কিন্তু মেয়েটি আর না আসায় সেই আলাপ হয় নি - র্যাটের বিষণ্ণতার মূল কারণ। জে-র আবার অনুমান র্যাটের কর্মহীন জীবন ই তাকে নিঃসঙ্গ করছে ও হতাশার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কারণ "মেয়েদের ঝামেলায় আটকে থাকার মতো ছেলে র্যাট না। ঝামেলা যদি কিছু হয়েও থাকে, সে খুব দ্রুত মেয়েটাকে ভুলে যেতে পারবে।"
জে মনে করে র্যাট একধরনের হীনমন্যতায় ভুগছে। তার চারপাশের সবাই ধাই ধাই করে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। কেউ ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে, কেউ জব করছে, সবাই যে যার মতো করে ভালো আছে, শান্তিতে আছে। ... শুধু র্যাটের কোনও কাজ নেই। সে কলেজ ড্রপ করেছে। পড়তে ভালো লাগে না তার। এই মরার শহরে বসে নিজের বিয়ারের গ্লাস পাহারা দিচ্ছে এবং পিনবল খেলছে। আর এটা সে নিজে বুঝতে পারছে। তাই মনটা দিনদিন দুর্বল হয়ে পড়ছে।
র্যাট এরপরে হঠাৎই অনেক পড়াশুনো শুরু করে। অনেক পড়তে থাকে। লিখতে থাকে। একজন ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠে। সেই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি সে অনামা কথককে পাঠাত।
লেখালেখি সম্পর্কে এই অনামা কথক উপন্যাসের এখানে সেখানে তার বেশ কিছু ভাবনা চিন্তার কথা জানিয়েছে।
গল্প লেখা স্বচিকিৎসার কোনো ব্যাপার না। বরং বলা ভালো, তা স্বচিকিৎসার হীন চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, সততার সঙ্গে কোনো কাহিনী বলা খুবই কষ্টকর। কেননা আমি যেসব শব্দ খুঁজে বেড়াই, তা মনে হয় গহীন গভীরে গিয়ে লুকায়। এটা একেবারেই সত্যনিষ্ঠ স্বীকারোক্তি, কোনো কৈফিয়ত নয়। তবে শেষ পর্যন্ত আমি যা লিখেছি, তা-ই সেরা, এর চেয়ে ভালো লেখা আমার পক্ষে আর সম্ভব নয়। এ ছাড়া এ ব্যাপারে আমার আর কিছু বলার নেই। এখনো আমি ভাবছি, যেভাবে তুমি এখন দক্ষ, বছরের পর বছর, কিংবা দশকের পর দশক আগে তুমি তা ছিলে। এভাবে চিন্তা করলেই তুমি তোমাকে বাঁচাতে পারো বলে আমার ধারণা। তবে তার পরও যখন তোমার কাজ হয়ে যাবে, তখন হাতি সমতলে ফিরে এসে তোমার চেয়ে আরো সুন্দর শব্দে তার নিজের কাহিনী বয়ান করতে সক্ষম হবে। ... লেখালেখি নিয়ে আরো কিছু লিখছি। তবে এটাই হবে আমার শেষ কথা। আমার কাছে লেখালেখি খুবই কষ্টকর একটা ব্যাপার। কখনো কখনো মাস কেটে যায়, একটা লাইনও লিখতে পারি না। আবার কখনো কখনো একটানা তিন দিন তিন রাত ধরে লেখার পর একসময় বুঝতে পারি, যা কিছু লিখছি তা কিছু হয়নি। এই সব কিছু সত্ত্বেও লেখালেখির মধ্যে আনন্দ আছে। জীবনযাপনের সমস্যাদির সঙ্গে তুলনা করলে দেখা যায়, লেখালেখির মধ্যে অর্থবহ কিছু খুঁজে পাওয়া খুবই সহজ। এটা যখন আমি বুঝতে পারি, তখন আমার বয়স খুব কম। তাই বিস্ময়ে সপ্তাহখানেক ধরে হতভম্ব হয়ে থাকি।
র্যাট ছাড়াও বারটেন্ডার জে’র সাথে অনামা কথকের মাঝেমাঝে কিছু কথাবার্তা হয় ও ক্রেতা খরিদ্দার সম্পর্কের বাইরে একটা হালকা বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। সে নিজে চিনা, কিন্তু তাদের থেকেও ভালো জাপানিজ বলে।
এই বারেই একদিন বাথরুমের কাছে একটি মেয়েকে অচেতন হয়ে পড়ে থাকতে দেখে কথক। বারের সবাইকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। ব্যাগ থেকে পাওয়া ঠিকানার ভিত্তিতে তাকে তার ঘরে পৌঁছে দেয় কথক ও সেখানেই রাতটা থেকে যায়, যতক্ষণ না মেয়েটি সুস্থ হয়ে ওঠে।

ভোর ছটার দিকে কথকের ঘুম ভাঙে যখন, মেয়েটি তার পাশে ঘুমোচ্ছে। জানলার দিকে মুখ করে শুয়ে ছিল সে৷ টেরি কাপড়ের একটা কম্বলের নিচে। কম্বলটা অবশ্য হাঁটু পর্যন্তই গোটানো ছিল। তার শরীরে একটা সুতোও ছিল না৷ নির্দিষ্ট সময় পর পর যখন সে শ্বাস নিচ্ছিল, তার সুগঠিত স্তন ওঠানামা করছিল। মেয়েটার শরীর দেখে মনে হচ্ছিল সেটা সূর্যের আলোয় ট্যান করা হয়েছে। শরীরের মাঝে মাঝে ছিল সাদা দাগ। সম্ভবত স্যুইমিং স্যুট পড়ার চিহ্ন এগুলো। মেয়েটার শরীর ছিল ছোটখাটো। পাঁচ ফুট তিন ইঞ্চির মতো। বয়স সম্ভবত বিশের কম।
এই মেয়েটিরও কোনও নাম নেই আখ্যানে, তাকে আমরা চিনি বাঁ হাতের কড়ে আঙুলটি নেই যার, এমন এক পরিচয়ে।
মেয়েটি সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর নিজেকে নগ্ন অবস্থায় আবিষ্কার করে ও কথককে জিজ্ঞাসা করে তাদের মধ্যে যৌন সম্পর্ক হয়েছিল কিনা। কথক নেতিবাচক উত্তর দিলেও তার সন্দেহ যায় না। প্রবল মদ খেয়ে সে এতটাই নেশাতুর ছিল, যে গত রাতের কোনও স্মৃতিই তার নেই। সেই কারণেই তার সংশয় কাটতে চায় না সকালে নিজেকে নগ্ন অবস্থায় দেখে। কথক জানিয়ে দেন মেয়েটি নিজেই তার জামা কাপড় খুলে ফেলেছিল।
এই মেয়েটির সাথে পরে কথকের আবার দেখা হয় তার কাজের জায়গায়, একটি রেকর্ডের দোকানে।
তারপর একদিন মেয়েটি জে'র বার এ আসে, কথকের সঙ্গে দেখা করার জন্য। সেখানে সে তার জীবনের কথা বলে। জানায় তার এক জমজ বোন ছিল, যে মারা গেছে। তার বাবাও দুবছর ক্যান্সারে ভুগে অনেক কষ্ট পেয়ে মারা গেছেন। বাবার চিকিৎসার জন্য সব টাকা শেষ হয়ে গেছে তাদের। বাবা মারা যাবার পর মাও তাদের ছেড়ে চলে যান, সম্ভবত অন্য কোনও পুরুষের সঙ্গে।
অল্পবয়সে নিজের কড়ে আঙুলটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনারে কীভাবে কাটা গিয়েছিল তাও সে জানায়। তাদের কথাবার্তার মধ্যেই আসে ভারত, চিতাবাঘ আর জিম করবেটের কথা। মেয়েটি জানতে পারে কথক বায়োলজি নিয়ে ইউনিভার্সিটিতে পড়ছে। পশুপাখি তার খুব পছন্দ। মেয়েটি প্রত্যুত্তরে জানায় তারও পশুপাখি পছন্দের। এরপর কথক বলে -
ভারত বলে একটা দেশ আছে সেটা তো জানো ?
জানি।
সেখানে ভাগলপুর নামে একটা জায়গা আছে। এক ভয়ঙ্কর চিতাবাঘ থাকত সেখানে। মাত্র তিন বছরে সে প্রায় তিনশ পঞ্চাশজন ভারতীয়কে খেয়ে ফেলে। সত্যি এটা ? [যদিও বাঘটি আসলে ভাগলপুরের ছিল না। ছিল রুদ্রপ্রয়াগের।]
সত্যি। ...
চিতাবাঘতার শেষপর্যন্ত কী হয়েছিল ?
একজন ইংরেজ শিকারী ছিল। বিখ্যাত শিকারী। জিম করবেট তার নাম। তিনি মাত্র আট বছরে চিতাটাসহ মোট একশ পঁচিশটা বাঘ শিকার করেন।
এরপর আবার যখন মেয়েটি তার ঘরে আসে তখন সে জানায় সে এখন যৌন সংগমে অক্ষম, কারণ সদ্য তাকে গর্ভপাত করাতে হয়েছে।
এই মেয়েটির সঙ্গে অনামা কথকের কোনও যৌন সম্পর্ক হয়েছিল কীনা, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু দুজনেই দুজনকে ভালোবেসেছিল অল্পদিনের মধ্যেই আর নিজেদের গোপন গহন কথাগুলি পরস্পরকে বলতেও শুরু করেছিল। কিন্তু এই মেয়েটি একদিন হঠাৎ করেই চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়। সে রেকর্ডের দোকানের চাকরি ছেড়ে দেয়, ভাড়াবাড়িটা ছেড়ে চলে যায়। কথক অনেক খুঁজেও আর তার কোনও সন্ধান পান নি।
উপন্যাসটিতে একটি বারে বসে এই অনামা কথক তার বন্ধু র্যাটের সঙ্গে অঢেল মদ্যপান করে। তার অঢেল মদ্যপানের অভ্যাস যে অনেকদিনের, সে কথা এই উপন্যাসে বলা আছে। কথক যদিও জানিয়েছে গরমের হাত থেকে বাঁচার জন্যই তাদের এই মাত্রাতিরিক্ত বিয়ার পান –
“গ্রীষ্মের এই গরমে আমরা যেন পাল্লা দিয়ে বিয়ার টানি। আমাদের খাওয়া বিয়ার দিয়ে ২৫ মিটারের সুইমিংপুল অনায়াসে ভরে ফেলা যায়। আর বাদামের খোসায় জে-এর বারের মেঝে দুই ইঞ্চি পর্যন্ত ঢেকে দেওয়া যাবে। কিন্তু এটা যদি না করি, তাহলে গরমের অসহ্য যাতনা থেকে রেহাই পাওয়ার আর কোনো উপায় থাকে না"।
তবে এ নিজের রক্তাক্ত হৃদয়কে নিরাসক্তি দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টাও হতে পারে।
এটা জানা যায় কদিন আগেই তার তৃতীয় প্রেমিকা হঠাৎ ই গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।
আমরা জানতে পারি কথকের শুধু এই তৃতীয় প্রেমটিই নয়, আগের দুটি প্রেমও হঠাৎ করেই শেষ হয়ে গিয়েছিল। প্রথম প্রেম ছিল হাইস্কুলের এক সহপাঠিনীর সাথে। স্কুল শেষ হবার কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। মেয়েটি কোথায় হারিয়ে যায়, তার আর সন্ধান পাওয়া যায় নি। দ্বিতীয় প্রেম স্টেশনে হঠাৎ আলাপ হওয়া একটি মেয়ের সাথে। ছাত্র আন্দোলনে ফেরার পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় সে কথকের ঘরে চলে আসে ও সেখানেই হপ্তাখানেক থেকে যায়। তারপর সেখান থেকে সে চলে যায় ও তাদের সম্পর্কের সেখানেই ইতি। তারপর এই তৃতীয় প্রেম, যার শুরুটা হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে তাদের পরিচয়ের মধ্যে দিয়ে। মেয়েটি ফরাসী ভাষা নিয়ে তখন পড়াশুনো করছে। পরের বসন্তেই হঠাৎ এই শোচনীয় পরিণতি, যে আত্মহত্যার কারণ কথক শুধু জানে না তাই নয়, অনুমানও করতে পারে না।
মাত্র একুশ বছরের জীবনে তিন তিনটে প্রেম ও যৌন অভিজ্ঞতার জন্য অনামা কথক বেশ খুশি।
আমার বয়স মাত্র একুশ। বেঁচে থাকার জন্য এই বয়েসটা বাড়াবাড়ি রকমের ভালো না হলেও খারাপ নয়। এর মধ্যেই তিনটে মেয়ের সঙ্গে আমি বিছানা পর্যন্ত গিয়েছি। লাইফ ইজ বিউটিফুল।
এরপর সে বিস্তারে তার প্রেম ও যৌন অভিজ্ঞতাগুলোর বর্ণনা দেয়।
প্রথম যে মেয়েটার সঙ্গে আমি বিছানায় যাই, সে ছিল আমার ক্লাসমেট। আমাদের দুজনের বয়েসই তখন সতেরো। সম্ভবত আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসতাম। এক সন্ধ্যায় প্রচুর মদ খাওয়ার পর আমরা নিজেদের একটা ঝোপের মধ্যে আবিষ্কার করি। আমার গার্লফ্রেন্ড তখন নিজ দায়িত্বে তার এবং আমার দুজনেরই জামা, জুতো, অন্তর্বাস সব খুলে ফেলে। একটুক্ষণ ভেবে কী মনে করে যেন হাতের ঘড়িটাও সে ঝোপের মধ্যে খুলে ফেলে দেয়।
বাড়ি থেকে ট্রেনে বসে পড়ার জন্য আমি আসাহি পত্রিকার রবিবারের সংখ্যাটা হাতে করে এনেছিলাম। ঝোপের মধ্যে সেটা বিছিয়ে দিয়ে তার ওপর আমরা একজন আরেকজনকে জড়িয়ে ধরি। সেটা ছিল আমার জীবনের প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা।
কী কারণে যেন সম্পর্কটা শেষ পর্যন্ত টেকেনি। আমাদের দুজনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। কারণটা ঠিক বুঝতে পারি নি। তবে এটা সত্যি যে আমাদের মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়। এরপরও বেশ কিছুদিন সারাক্ষণ তার কথা ভাবতাম। একধরনের কষ্ট হতো বুকের ভেতর। রাতে মাঝেমধ্যে ঘুম হতো না। তবে সে কাহিনী এখানেই শেষ।
দ্বিতীয় মেয়েটির সঙ্গে আমার দেখা হয় টোকিওর শিঞ্জুকু স্টেশনে। ততদিনে আমি মফস্বলের পাট চুকিয়ে টোকিওর একটা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। মেয়েটাকে যখন প্রথম দেখি, তখন তার বয়েস মাত্র ষোল। একদম চালচুলোহীন একটা মেয়ে। রাতে মাথা গোঁজার মতো সামান্য একতা জায়গাও তার ছিল না। শরীরের যেখানে স্তন থাকার কথা, সে জায়গাটা একেবারে সমান। ম্যানচেস্টেড, স্তন বলে কিছু নেই। দেওয়ালেরও উঁচু নিচু থাকতে পারে, কিন্তু তার বুক ছিল একেবারে মসৃণ। তবে সুন্দর দুটো চোখ ছিল তার। বুদ্ধির ঝিলিক ছিল সেখানে।
এক রাতে শিঞ্জুক স্টেশনে যুদ্ধবিরোধী বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। প্রচণ্ড ভাঙচুর হচ্ছিল। বাস, ট্রেন, দোকানপাঠ সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। আমি ট্রেন থেকে নেমে আমার আপ্যার্টমেন্টে ফিরছিলাম। হঠাৎ দেখি টিকিট গার্ডের বন্ধ ঘরের কোণায় মেয়েটা জড়োসড়ো হয়ে বসে আছে।
... পরের কয়েক সপ্তাহ মেয়েটা আমার অ্যাপার্টমেন্টেই ছিল। ... একদিন সুপারমার্কেটে গিয়েছি বাজার করতে। সেখান থেকে এক ব্যাগ জিনিসপত্র নিয়ে বাসায় ফিরে দেখি মেয়েটা নেই। নেই মানে নেই। পুরোপুরি হাওয়া। নিজের সব জিনিসপত্রের সঙ্গে আমার কিছু জিনিসও নিয়ে গেছে সে। টেবিলের ওপর কিছু খুচরো টাকাপয়সা ছিল আমার। সেগুলো হাওয়া।
এরপর তৃতীয় মেয়েটির গল্প শোনায় কথক।
তার সঙ্গে দেখা হয় ইউনিভার্সিটির লাইব্রেরীতে। ফরাসী সাহিত্যে মেজর করছিল সে। যদি বেঁচে থাকত আমার সঙ্গে একটা দীর্ঘমেয়াদী সম্পর্ক হতে পারত। তবে মরে যাওয়ায় সেটা আর হয়ে ওঠে নি।
মেয়েটি আত্মহত্যা করেছিল। কেন করেছিল তা কেউ জানে না।
কথক বাইরে থেকে নিজেকে নিরাসক্ত দেখানোর চেষ্টা করে, না সে সত্যিই নিরাসক্ত সে ধাঁধার উন্মোচন মুরাকামি এখানে করেন নি।
কথকের বাবা মার কথা এখানে তেমন কিছু নেই। তবে এটা বলা আছে যে ছোটবেলায় তিনি খুব চুপয়াপ ছিলেন বলে তার বাবা মা তাকে নিয়ে বেশ দুশ্চিন্তায় পড়ে যান ও তাদের এক সাইক্রিয়াটিস্ট বন্ধুর কাছে নিয়ে যান। সেই সাইক্রিয়াটিস্ট ও তার চিকিৎসাপদ্ধতির কথা অবশ্য অনেকটা জায়গা জুড়ে বলা হয়েছে। উপন্যাসে কথকের তিন কাকার কথাও আছে। একজন জাপান জুড়ে বিভিন্ন উষ্ণ প্রস্রবনে ঘুরে ঘুরে বেড়ান। একজন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার ঠিক দুদিন পরে নিজের পাতা মাইন বিস্ফোরণেই মারা যান। আর এক কাকা মারা যান ক্ষুদ্রান্তের ক্যান্সারে।
এই কাকাই তাকে ডেরেক হার্টফিল্ড এর উপন্যাসের সাথে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। এই কাল্পনিক ঔপন্যাসিককে একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে এই আখ্যানে নিয়ে আসেন মুরাকামি। এই কল্পিত লেখক চরিত্রটি অনেক জনপ্রিয় উপন্যাসের রচয়িতা। দৈত্য, দানো, ভিনগ্রহের প্রাণীদের নিয়ে কাহিনী ফাঁদতে তিনি ছিলেন ওস্তাদ। কথক জানিয়েছেন তিনি এনার থেকেই লেখার অনেক কলাকৌশল শিখেছিলেন। - “লেখালেখির ব্যাপারে ডেরেক হার্টফিল্ডের কাছ থেকে আমি অনেক কিছু শিখেছি। অবশ্য বলা উচিত, পুরোটাই তাঁর কাছ থেকে শেখা। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে হার্টফিল্ড নিজে একজন সাধারণ মানের লেখক ছিলেন। আপনি যদি তাঁর বই পড়ে থাকেন, তাহলে সহজেই বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাচ্ছি। তাঁর লেখা পড়া খুব কষ্টসাধ্য। আর লেখার প্লট এলোমেলো, থিম একেবারেই শিশুসুলভ। এসব সত্ত্বেও যে কজন অসাধারণ লেখক তাঁদের লেখাকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করতে সক্ষম হয়েছেন, তাদের মধ্যে তিনি অনন্য। হেমিংওয়ে, ফিৎজারেন্ডের মতো তাঁর সময়কার অন্যান্য লেখকের সঙ্গে তুলনা করে দেখেছি যে তাঁর লেখালেখি তেমন সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়নি বলে আমার মনে হয়েছে”। ... “ভালো লেখালেখির ব্যাপারে হার্টফিল্ড যা বলেছেন, তা জড়ো করলে দাঁড়ায় এ রকম—‘তিনি লেখক, যিনি সাহিত্য লেখেন। তাই বলা যায়, লেখকের লেখাই হবে মূলকথা। তিনি সব সময় দূরত্ব বজায় রাখবেন। আর তিনি কী বুঝলেন সেটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং তিনি কী মাপকাঠি ব্যবহার করেছেন, সেটাই বিবেচনার বিষয়”।
হার্টফিল্ডের চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তোলার জন্য তার একটি নাটকীয় মৃত্যুদৃশ্যও রচনা করেন মুরাকামি।
হার্টফিল্ডের একটা বড় সমস্যা ছিল জীবনের শেষ প্রান্তে এসেও তিনি বুঝতে পারেন নি কিসের বিরুদ্ধে লড়ছেন। এক অজানা শত্রুর মোকাবিলা করে গেছেন তিনি। শেষ পর্যন্ত হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিশ্চিত পরাজয় জেনেও তিনি মাথা উঁচু করে লড়ে গেছেন। আট বছর দুই মাস লেখার চেষ্টা করেছেন। তারপর নিজেই একদিন মৃত্যুকে বেছে নেন। ১৯৩৮ সালের রোববারের এক রৌদ্রকরোজ্জ্বল সকালে আত্মহত্যা করেন তিনি। ডান হাতে হিটলারের পোট্রেট চেপে ধরে বাঁ হাতে ছাতা খুলে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে ঝাঁপ দেন।
মুরাকামির উপন্যাসটি প্রকাশিত ও জনপ্রিয় হলে অনেক পাঠকই ডেরেক হার্টফিল্ডকে একজন বাস্তব লেখক হিসেবে ধরে নিয়ে বিভিন্ন গ্রন্থাগারে তাঁর বই এর খোঁজ করতে থাকেন ও গ্রন্থাগারিকেরা এই নিয়ে বেশ বিড়ম্বনায় পড়েন।
